শিবলিঙ্গ কি?!

শিবলিঙ্গ বিষয়ে বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। এ বিষয়ে তত্ত্বত কোনো জ্ঞান না থাকায় কতিপয় ব্যক্তি এর নিন্দা করে থাকে। কিন্তু কেউ তাঁর সম্পর্কে যথার্থ অবগত হলে তখন নিন্দার পরিবর্তে তাঁর স্তুতি করবে মূল সংস্কৃত लिङ्गं (লিঙ্গ) শব্দের অর্থ হলো “প্রতীক” বা চিহ্ন। বাংলা ব্যাকরণ অনুসারেও লিঙ্গ চার প্রকার, যথা- ১) পুংলিঙ্গ ২) স্ত্রীলিঙ্গ ৩) ক্লীবলিঙ্গ ৪) উভয়লিঙ্গ অতএব, খুব সহজেই বুঝা যায় ব্যাকরণের যে ব্যাখ্যার দ্বারা কোন মানুষকে তথা প্রাণীকে, পুরুষ বা স্ত্রী প্রজাতি হিসেবে, কিংবা কোন জড়বস্তুকে আলাদা আলাদাভাবে সনাক্ত করা হয় তাই লিঙ্গ। যারা লিঙ্গ বলতে কেবল জননেন্দ্রিয়কে বুঝেন তাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি সংস্কৃতে জননেন্দ্রিয়ের প্রতিশব্দ হল- শিশ্নম্। যদি শিবলিঙ্গম্ শব্দে জননেন্দ্রিয়কে বোঝানো হতো তাহলে লিঙ্গ শব্দের ব্যবহার না করে শিশ্নম্ শব্দটি ব্যবহার করা হতো। প্রকৃতপক্ষে “শিবলিঙ্গ” বলতে কোন জননেন্দ্রিয়কে বোঝায় না। “শিব” শব্দের অর্থ মঙ্গলময় এবং “লিঙ্গ” শব্দের অর্থ প্রতীক। এই কারণে শিবলিঙ্গ শব্দটির অর্থ “মঙ্গলময় প্রতীক”, যাঁর দ্বারা জগতের সৃষ্টি কার্য সাধিত হয়েছে। এই প্রতীকরূপেই শিব মনুষ্যগণ, ব্রহ্মাদি দেবগণ, মহর্ষিগণের দ্বারা বহু প্রাচীনকাল থেকেই পূজিত, বন্দিত। কিন্তু অধুনা মানুষের চেতনা কলুষিত হওয়ার ফলে মানুষ এই প্রতীকরূপে শিবের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা জড়জগত সৃষ্টি করেন। কিন্তু মায়ার সাথে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ নেই। তাই শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতাররূপে কারণোদকশায়ী বিষ্ণু মায়াদেবীর প্রতি ইক্ষণ বা দৃষ্টিপাত করেন। ভগবানের ইক্ষণের ফলে সৃষ্ট দিব্য জ্যোতির্ময় প্রকাশ প্রকৃতিরূপা মায়ার গর্ভে সমস্ত জীব ও ব্রহ্মাণ্ডসমূহের উপাদান সঞ্চার করেন এ জ্যোতির্ময় স্বরূপই শিবলিঙ্গরূপে পরিচিত। আবার, যদি লিঙ্গ শব্দে জননেন্দ্রিয়কে বোঝায়, তবুও তা নিন্দার্হ কি না তা একটি উদাহরণের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা যাক- আমাদের জন্মের কথা ধরা যাক। পিতামাতার আনন্দঘন মূহুর্তের ফলেই আমাদের উৎপত্তি। কিন্তু যে কারণে আমাদের জন্ম হয়েছে, সে বিষয়ে আমরা চর্চা করি না বা তাকে ঘৃণাও করি না। বরং, সেই কারণেই আমরা পিতাকে জন্মদাতা বলে সবচেয়ে মর্যাদা দান করে থাকি। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার নিন্দা করবে না। ঠিক তেমনি ভগবান শিবরূপী তাঁর লিঙ্গম্ বা জ্যোতির দ্বারা প্রকৃতিস্বরূপা মায়াদেবীর গর্ভে এ ব্রহ্মাণ্ডের গর্ভাধান করেন, যার মাধ্যমে এ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হলো। তাই, আমাদের সৃষ্টির কারণস্বরূপা যে লিঙ্গ, তাঁকে কি আমাদের প্রাকৃত বা জড় দৃষ্টিতে দেখা উচিত, নাকি অপ্রাকৃত দৃষ্টিতে দর্শনপূর্বক এর অর্চন করা উচিত? তাই লিঙ্গ শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করেই দেখা গেল যে, শিবলিঙ্গ প্রাকৃত কোনো বিষয় নয়; বরং জগৎ সৃষ্টির কারণ। তাই তা পরম শ্রদ্ধাসহকারে গ্রহণ করার বিষয়। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি প্রাকৃত বিধায় আমরা সবকিছুকে প্রাকৃত দৃষ্টিতে বিচার করি। অজ্ঞতাবশতও আমাদের এ ধরনের অপরাধ যেন না হয়, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক এবং যেসকল মূঢ় শিবলিঙ্গের যথার্থ মর্ম না জেনে তাঁর নিন্দা করে, তাদের এ তত্ত্ব অবগত করানো উচিত। “যেসকল মূর্খ শিবলিঙ্গ বলতে জননেন্দ্রিয় মনে করে, তাদের জ্ঞান-বুদ্ধিও সেই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।” শিবলিঙ্গকে পুরুষাঙ্গ ভাবার শাস্তি!!! রাম চন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা ইক্ষ্বাকু জীবনের শেষভাগে শিবের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু পূর্বে তিনি শিবলিঙ্গকে পুরুষের শিশ্ন (পুরুষাঙ্গ) বলে নিন্দা করেছিলেন। ফলে মৃত্যুর পরে পূর্বকৃত পাপের কারণে তার জননাঙ্গের রোগ হয় এবং তিনি জিহ্বা ও নাক হীন হন। “মহেশ্বর ইক্ষ্বাকুর প্রতি কহিলেন, ” তুমি দিন দিন ক্ষীণ হইয়া অষ্টদিন মাত্র আমার পূজা করিয়াছ, কিন্তু পূর্বে শিবলিঙ্গকে ‘শিশ্নের অগ্রভাগ’ এই বলিয়া আমার নিন্দা করিয়াছ, সেই পাপযোগ দ্বারা তোমার শিশ্নের অগ্রভাগ চক্র ও বিবর হইবে এবং তোমার জিহ্বা ও নাসিকাদি থাকিবে না।” – (পদ্মপুরাণ: পাতালখন্ড/ ৬৬/১৬৮-১৮৬) তাই যারা শিবলিঙ্গকে পুরুষাঙ্গ ভাবেন, তারা সাবধান! সংস্কৃতে লিঙ্গ শব্দ দ্বারা পুরুষাঙ্গকে বুঝায় না। ব্যাকরণে পুলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ যে পড়ানো হয়, সেখানে কি জননাঙ্গকে বুঝানো হয়? সংস্কৃতে শিব শব্দের অর্থ ‘মঙ্গল’ এবং লিঙ্গ শব্দের অর্থ ‘প্রতীক’। ভগবান বিষ্ণুর যে মঙ্গলময় রূপ, তা-ই শিবলিঙ্গ। – প্রবীর চৈতন্যচন্দ্র দাস
পুরাণসমূহের সংখ্যা এবং শ্রেণীবিভাগ?!
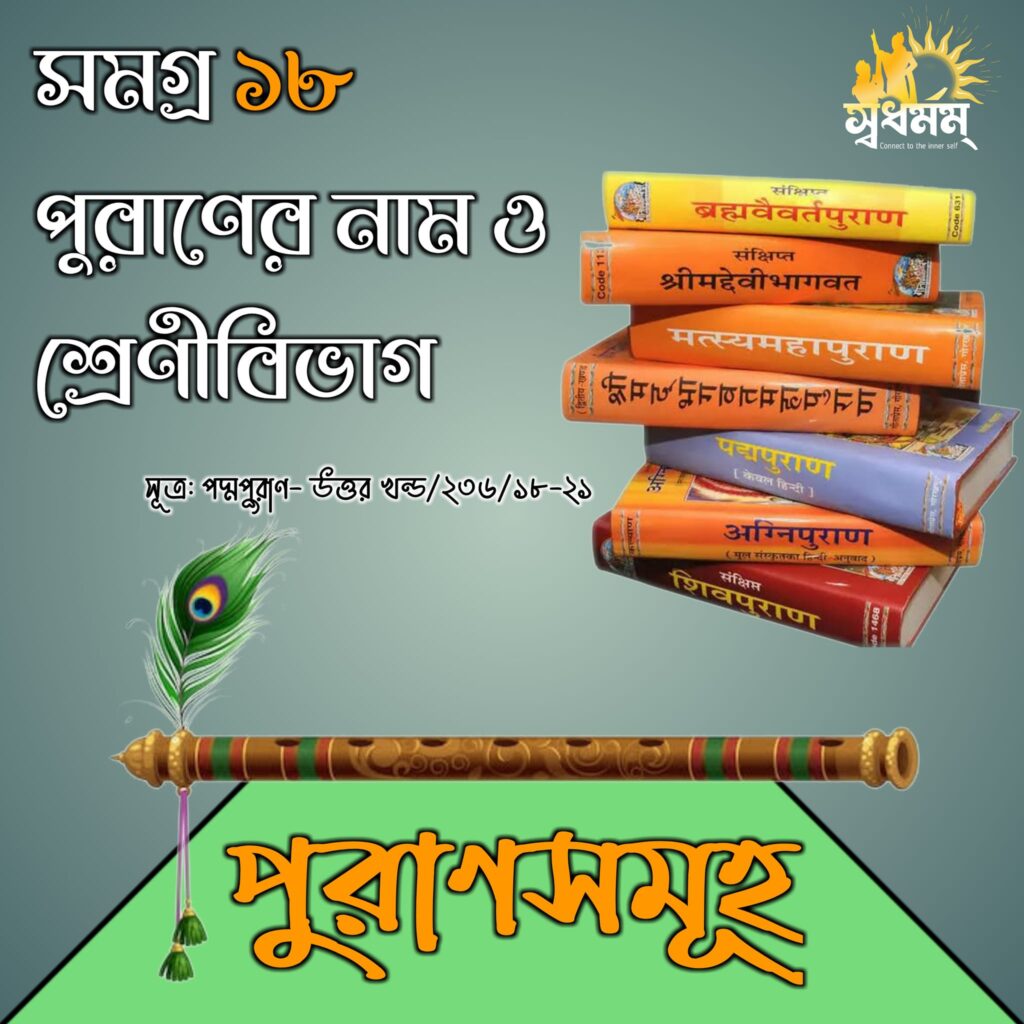
পদ্মপুরাণ উত্তর খন্ড/২৩৬/১৮-২১ নং শ্লোকে ভগবান শিব দেবী পার্বতীর নিকট পুরাণ সমূহের বর্ণনা দিচ্ছেন- “হে সুন্দরী (পার্বতী), জেনে রেখো বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ পুরাণ সাত্ত্বিক; ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, বামন ও ব্রহ্ম পুরাণ রাজসিক; এবং মৎস্য, কূর্ম, লিঙ্গ, শিব, স্কন্দ এবং অগ্নি পুরাণগুলি তামসিক।” সাত্বিক পুরাণ: ১। বিষ্ণুপুরাণ – ২৩,০০০ শ্লোক সমন্বিত২। নারদপুরাণ – ২৫,০০০ শ্লোক সমন্বিত৩। ভাগবতপুরাণ – ১৮,০০০ শ্লোক সমন্বিত৪। গরুড়পুরাণ – ১৯,০০০ শ্লোক সমন্বিত৫। পদ্মপুরাণ – ৫৫,০০০ শ্লোক সমন্বিত৬। বরাহপুরাণ – ২৪,০০০ শ্লোক সমন্বিতরাজসিক পুরাণ:১। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ – ১২,০০০ শ্লোক সমন্বিত২। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ – ১৮,০০০ শ্লোক সমন্বিত৩। মার্কেন্ডেয় পুরাণ – ৯,০০০ শ্লোক সমন্বিত৪। ভবিষ্যপুরাণ – ১৪,৫০০ শ্লোক সমন্বিত৫। বামন পুরাণ – ১০,০০০ শ্লোক সমন্বিত৬। ব্রহ্মপুরাণ – ১০,০০০ শ্লোক সমন্বিততামসিক পুরাণ:১। মৎস্যপুরাণ – ১৪,০০০ শ্লোক সমন্বিত২। কূর্মপুরাণ – ১৭,০০০ শ্লোক সমন্বিত৩। লিঙ্গপুরাণ – ১১,০০০ শ্লোক সমন্বিত৪। শিবপুরাণ – ২৪,০০০ শ্লোক সমন্বিত৫। স্কন্ধপুরাণ – ৮১,১০০ শ্লোক সমন্বিত৬। অগ্নিপুরাণ – ১৫,৪০০ শ্লোক সমন্বিত বিঃদ্রঃ – অষ্টাদশ মহাপুরাণের শ্লোক সংখ্যা ভাগবতপুরাণের ১২/১৩/৪-৯ নং শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে। – প্রবীর চৈতন্যচন্দ্র দাস
পুরাণ সমূহ কি মনোধর্ম প্রসূত কাল্পনিক?!
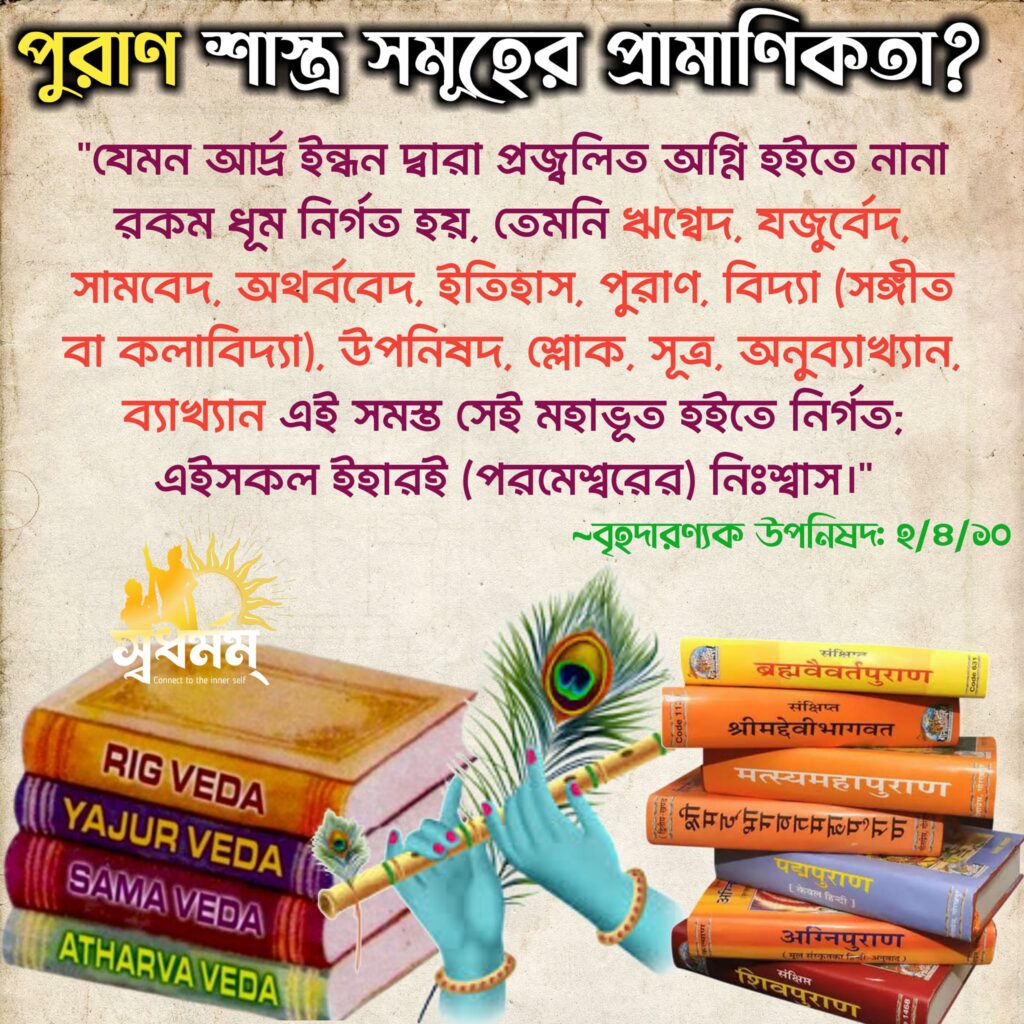
বেদ অপৌরুষেয়। স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান হতে প্রকাশিত হয়েছেন। বেদ বৈদিক সংস্কৃত ভাষায় রচিত, বেদই সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন এবং হিন্দু তথা সনাতন ধর্মের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। “বেদ” এর অপর নাম “শ্রুতি” এর কারণ হিসেবে বলা যায় “বেদ” লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্বে বেদের বাণী সমূহ গুরুশিষ্য পরম্পরায় শ্রবণের মাধ্যমে সংরক্ষিত হতো। যারা সেই বাণী শ্রবণের দ্বারা হৃদয়ে ধারণ করতেন তাঁদের বলা হতো শ্রুতিধর। পরবর্তীতে দ্বাপরযুগের শেষে আসন্ন কলিযুগের প্রয়োজন বিবেচনায় এই সমস্ত বেদকে লিপিবদ্ধ করেন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, যিঁনি ব্যাসদেব নামে সমাদৃত। কিন্তু, আজকালের তথাকথিত মহর্ষি ও নামধারী আর্যরা দাবী করেন বেদ’ সমূহের কিছু বিভাগ কোনো বেদ’ই নয়, কি আশ্চর্যজনক কথা! যেমন- কৃষ্ণ-যজুর্বেদ এবং অষ্টাদশ পুরাণ সমূহকে তারা স্বীকারই করেন না। এগুলা নাকি মনুষ্যসৃষ্ট এবং অষ্টাদশ পুরাণ সমূহ নাকি অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ ঘটনায় ভর্তি! যদিও এমন নগণ্য কিছু ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা রয়েছে এবং এর থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার যথেষ্ট উপযোগিতাও রয়েছে, কিন্তু সেই সকল অনার্যদের যেহেতু তা উপলব্ধির জন্য বিশুদ্ধ চেতনা নেই তাই তারা আসলে এগুলোকে বাদ দিয়ে স্ব-মতাদর্শের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও প্রায়োগিক এমন কিছু বিভাগকেই কেবল মান্য করেন। আজকে আমরা দেখবো তাদের নির্দিষ্ট মান্য শাস্ত্র সমূহেই’বা পুরাণ শাস্ত্র সম্পর্কে কি নির্দেশ রয়েছে। স্মৃতিশাস্ত্র (ধর্মশাস্ত্র) তথা অষ্টাদশ পুরাণ সমূহকে নিয়ে যাদের দ্বিধা রয়েছে তাদের নিমিত্তে স্মৃতিশাস্ত্রের প্রাধাণ্যতা ও প্রামাণিকতা সম্পর্কিত কিছু তথ্য বর্ণিত হলো: “চারটি বেদ ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত, ঠিক তেমনই পুরাণ, ইতিহাস, গাথা, তার থেকে সৃষ্ট।” – (অথর্ববেদ ১৫/৬/১১-১২) “যেমন আর্দ্র ইন্ধন দ্বারা প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে নানা রকম ধূম নির্গত হয়, তেমনি ঋগ্বেদ যজুর্বেদ সামবেদ অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (সঙ্গীত বা কলাবিদ্যা), উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান এই সমস্ত সেই মহাভূত হইতে নির্গত ; এইসকল ইহারই নিঃশ্বাস।” – (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২/৪/১০) “ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা (সঙ্গীত বা কলাবিদ্যা), উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যান, ব্যাখ্যান ইষ্ট, হোম, অশন, পানীয়, ইহলোকে, পরলোক, সর্বভূত – এই সমস্ত বাক্ দ্বারাই জানা যায়। বাক্ই পরমব্রহ্ম। যিনি ইহা জানিয়া বাকে্র উপাসনা করেন, বাক্ তাকে পরিত্যাগ করে না। – (বৃহদারণ্যক উপনিষদ ৪/১/২) “তাহার পর আদিত্যের উত্তরদিকের যে রশ্মিগুসমূহ, তাহারাই ইহার উত্তর মধুনাড়ী; অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহ মধুকর; ইতিহাস পুরাণই পুষ্প। সেই যজ্ঞীয় জলই পুষ্পের অমৃত।” – (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩/৪/১) “সেই অথর্বাঙ্গিরস মন্ত্রসমূহ ইতিহাস ও পুরাণকে উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। অভিতপ্ত সেই ইতিহাস ও পুরাণ হইতে যশ, তেজ, ইন্দ্রিয়সামর্থ্য, বীর্য ও অন্নরূপ রস উৎপন্ন হইয়াছিলো।” – (ছান্দোগ্য উপনিষদ ৩/৪/২) “ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ” – (ছান্দোগ্য উপনিষদ: ৭/১/২; ৭/১/৪; ৭/২/১; ৭/৭/১) “ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা বেদকে বন্ধিত করিবে; না হইলে ‘এ আমাকে প্রহার করিবে’ ইহা ভাবিয়া বেদ অল্পজ্ঞ লোক হইতে ভয় পাইয়া থাকেন।” – (মহাভারত: আদি/০১/২২৯) “বেদকে শ্রুতি ও ধর্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলা হয়, ঐ শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা মীমাংসা করিবে না। যেহেতু, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।। – (মনুসংহিতা: ২/১০) যে ব্যক্তি প্রতিকূল তর্ক দ্বারা মূলস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রকে অবমাননা করে, সাধু লোকেরা সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে দ্বিজের কর্তব্য কর্ম্ম অধ্যয়নাদি সকল অনুষ্ঠান হইতে বহিস্কৃত করিবেন। – (মনুসংহিতায়: ২/১১) শতপথ ব্রাহ্মণেও (১১/৫/৬/৮) পুরাণের কথা উল্লেখ রয়েছে। পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা,ধর্মশাস্ত্র, বেদাঙ্গ (শিক্ষা,কল্প,ব্যাকরণ, নিরুক্ত,জ্যোতিষ, ছন্দ-৬প্রকার), এবং চারি বেদ (সাম,ঋক, যজু,অথর্ব)। – এই ১৪টি(শাস্ত্র) পুরুষার্থ- সাধন জ্ঞান এবং ধর্ম প্রবৃত্তির কারণ। – (যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ১/৩) “ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব – এই চতুর্বেদ এবং ইতিহাস তথা রামায়ণ ও মহাভারত এবং পঞ্চরাত্র—এই সকল ‘শাস্ত্র’ বলিয়া কথিত হইয়াছে ৷ ইহাদের অনুকূল যে সকল গ্রন্থ (পুরাণ, তন্ত্র আদি), তাহা ‘শাস্ত্র’-মধ্যে পরিগণিত৷ এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র তো নহে-ই বরং তাহাকে ‘কুবর্ত্ম’ বলা যায়৷” – (মধ্বভাষ্যধৃত স্কন্দবচন) অতএব, দেখাই যাচ্ছে যে সর্বজনীন শাস্ত্রসমূহতেও পুরাণের প্রামাণিকতা বর্ণিত রয়েছে। বৈদিকশাস্ত্রে ইতিহাস ও পুরাণকে বেদ তথা পঞ্চম বেদ হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও কিছু কিছু নব্য পণ্ডিতরা পুরাণের বিরোধিতা করে মনগড়া ব্যাখ্যা দাড় করিয়ে ঘোষণা দেয় পুরান (অষ্টাদশ পুরাণ) আর ইতিহাস (রামায়ণ+মহাভারত) বলতে এটা বোঝানো হয়নি, ঐটা বোঝানো হয়েছে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। অথচ, তাদের এই সমস্ত মনগড়া তথ্যের কোনো ভিত্তি নেই। তাহলে কোন সিদ্ধান্ত মানা উচিৎ শাস্ত্র সিদ্ধান্ত নাকি তথাকথিত ব্যক্তিবর্গের মনগড়া ব্যাখ্যা?!?
আর্য কে?!
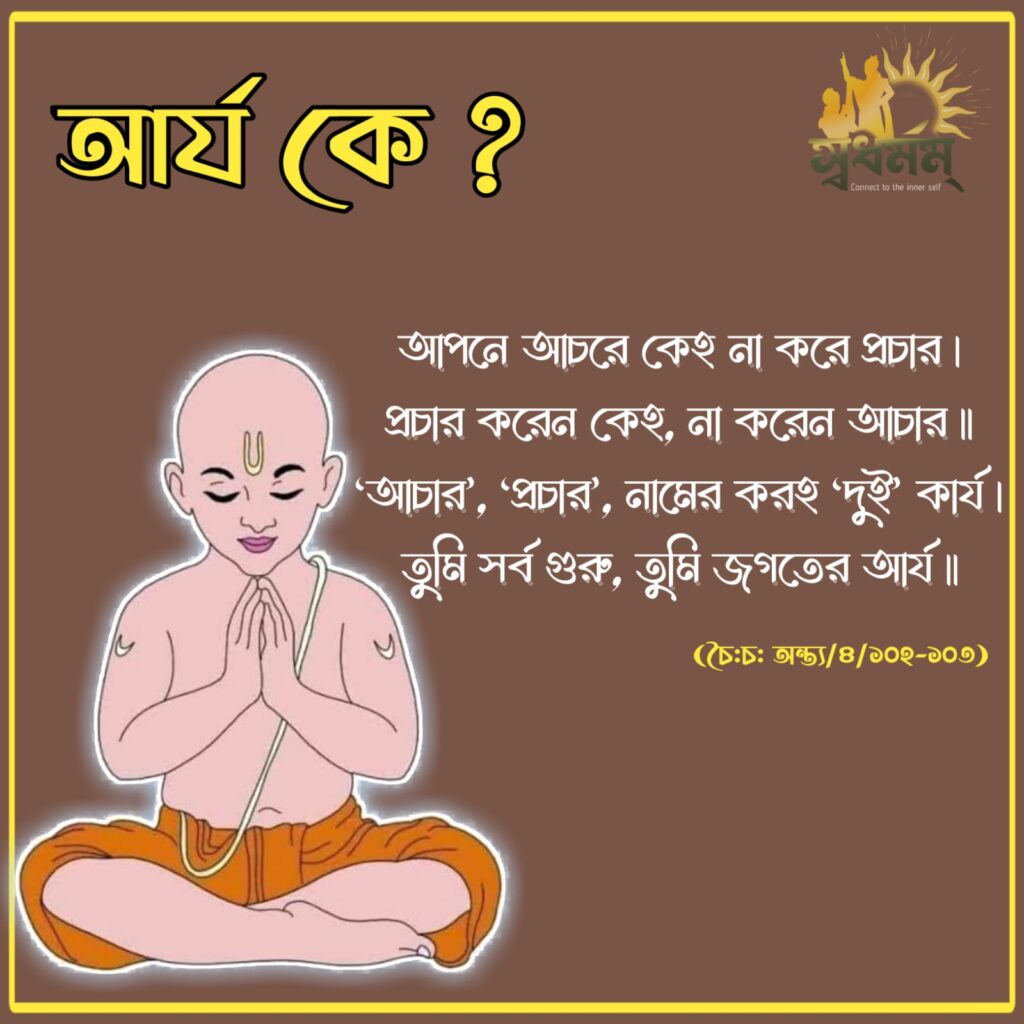
আর্য সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে প্রথমে জেনে রাখা আবশ্যক, মহর্ষি মার্কন্ডেয় কলিযুগের লক্ষণ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন: “এই জগৎটাই বিপরীত হইয়া যাইবে, নীচ উচ্চ হইবে এবং উচ্চ নীচ হইবে ৷” – (মহাভারত: বনপর্ব ১৬১/৬৪) তাই আজকাল দেখা যায় একদল ব্যক্তি আচরণে অনার্য কিন্তু, নিজেকে আর্য প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগে যায়। কেউ কেউ আবার নিজেকে আর্য প্রমাণ করতে নামের পাশে আর্য শব্দটি জুড়ে দেন, অথচ তাদের আচরণ সম্পূর্ণই ভিন্ন, ঠিক যেন অনার্যদের মতন। কিন্তু কি জানি! কি মনে করে সেই সমস্ত ব্যক্তিরা নিজেকে আর্য (শ্রেষ্ঠ) দাবী করেন, আমার বোধগম্য নয়। এই “আর্য কে” এ নিয়ে বহু আলোচনা হতে পারে কিন্তু যদি আমরা সারবস্তুর দিকে আলোকপাত করি, তবে তা স্পষ্ট জ্বলজ্বল করে উঠবে। তাই মূল বিষয়ে আসা যাক। মহাভারতে খুব সুন্দরভাবে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়েছে আসলে কে আর্য। ন বৈরমুদ্দীপয়তি প্রশান্তং ন দর্পমারোহন্তি নাস্তমেতি। ন দূর্গতোস্মীতি করোত্যকার্যং তমার্যশীলং পরমাহুরার্যাঃ।। – (মহাভারত:উদ্যোগ পর্ব,৩৩/১১২) “যে শান্ত, বৈরিতাকে উদ্দীপ্ত করেনা, গর্ব করেনা, হীনতা দেখায় না তথা ‘আমি বিপত্তিতে পড়েছি ‘ এমন ভেবে অনুচিত কর্ম করেনা, সেই উত্তম আচরণকারী ব্যাক্তিকে আর্য বলে।” তাই যদিও দেখতে পাওয়া যায় কিছু লোক অতি আবেগে নামের পাশে আর্য শব্দ জুড়ে দেন। নামের পাশে আর্য লাগালেই কেউ আর্য হয়ে যায় না, তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। অনেককেই দেখা যায় বেদ-জ্ঞান নিয়ে বাকচাতুর্যতা প্রদর্শন করে অন্যদিকে সেই শিক্ষা আচরণ করে না, করতে পারে না, ভন্ডামি করে বেড়ায় তা অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। কারণ এটা বেদ নিন্দার সমতুল্য, অর্থাৎ নাস্তিকতা। যোগ্যতা হলে যেকেউ আর্য হিসেবে এমনিতেই পরিগনিত হবে। সেই সমস্ত তথাকথিত আর্যরা এও জানেন না যে- অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতন্মন্যমানাঃ। দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিযন্তি মূঢ়া অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ।। – (কঠোপনিষদ: ১/২/৫) “যারা অবিদ্যা-পরিবেষ্টিত হয়ে নিজেদের প্রজ্ঞাবান ও শাস্ত্রবিশারদ মনে করে অভিমান করে, এই সব কুটিল স্বভাব অবিবেকী ব্যক্তিরা বিভিন্ন লোকে পরিভ্রমণ করতে থাকে, যেমন অন্ধের দ্বারা পরিচালিত অন্ধ ব্যক্তিরা ঘুরতে থাকে।” (নচিকেতার প্রতি যমরাজ) বাংলা সাহিত্যের একজন বিখ্যাত কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রও স্ব-প্রণোদিতভাবে নিজেকে যারা শ্রেষ্ঠ ঘোষণা করেন কিংবা ভেবে থাকেন তাদের সম্বন্ধে বলেছেন- “আপনারে বড় বলে, বড় সে নয় লোকে যারে বড় বলে, বড় সে হয়। গুনেতে হইলে বড়, বড় বলে সবে বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে।” তো এই বাক্যগুলোই এই কলিযুগের পতিত পাবন অবতারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব এর ভাবাদর্শের মূলনীতি- “তৃণাদপি সুনীচেন তরুরোপি সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।। – (শিক্ষাষ্টকম্-৩) যিনি নিজেকে সকলের পদদলিত তৃণের থেকেও ক্ষুদ্র বলে মনে করেন, যিনি বৃক্ষের মতো সহিষ্ণু, যিনি মান শূন্য হয়েও অন্য সকলকে সম্মান প্রদর্শন করেন, তিনি সর্বক্ষণ ভগবানের দিব্যনাম কীর্তনের অধিকারী। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে (অন্ত্য: ৪/১০২-১০৩) হরিদাস সম্বন্ধে বলা হয়েছে- “আপনে আচরে কেহ না করে প্রচার। প্রচার করেন কেহ, না করেন আচার ॥ ‘আচার’, ‘প্রচার’, নামের করহ ‘দুই’ কার্য। তুমি সর্ব গুরু, তুমি জগতের আর্য ॥” বৈদিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি আচার প্রচারকারীই হলেন আর্য। প্রকৃতপক্ষে এটাই আর্য হিসেবে গড়ে উঠার বেদ নিহিত মূলমন্ত্র। অতএব, আজকাল যাদের দেখা যায় কোনোরূপ প্রামাণিক পরম্পরা ব্যতীতই মনগড়াভাবে বৈদিক শিক্ষানুশীলন করে অন্যকে শুধু জ্ঞানই দিয়ে যান, কিন্তু নিজে তা আচরণ পর্যন্ত করতে পারেন না, তারা আর্য নন। অপরপক্ষে, কেউ যদি বৈদিক শিক্ষা মহাপ্রভু নির্দেশিত পন্থা, “বল কৃষ্ণ; ভজ কৃষ্ণ; কর কৃষ্ণ শিক্ষা” আচরণ করেন এবং অন্যকে সেই শিক্ষা গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করেন প্রকৃতপক্ষে তিনিই হলেন আর্য। – প্রবীর চৈতন্যচন্দ্র দাস
উপনিষদের সংখ্যা ও বিন্যাস।
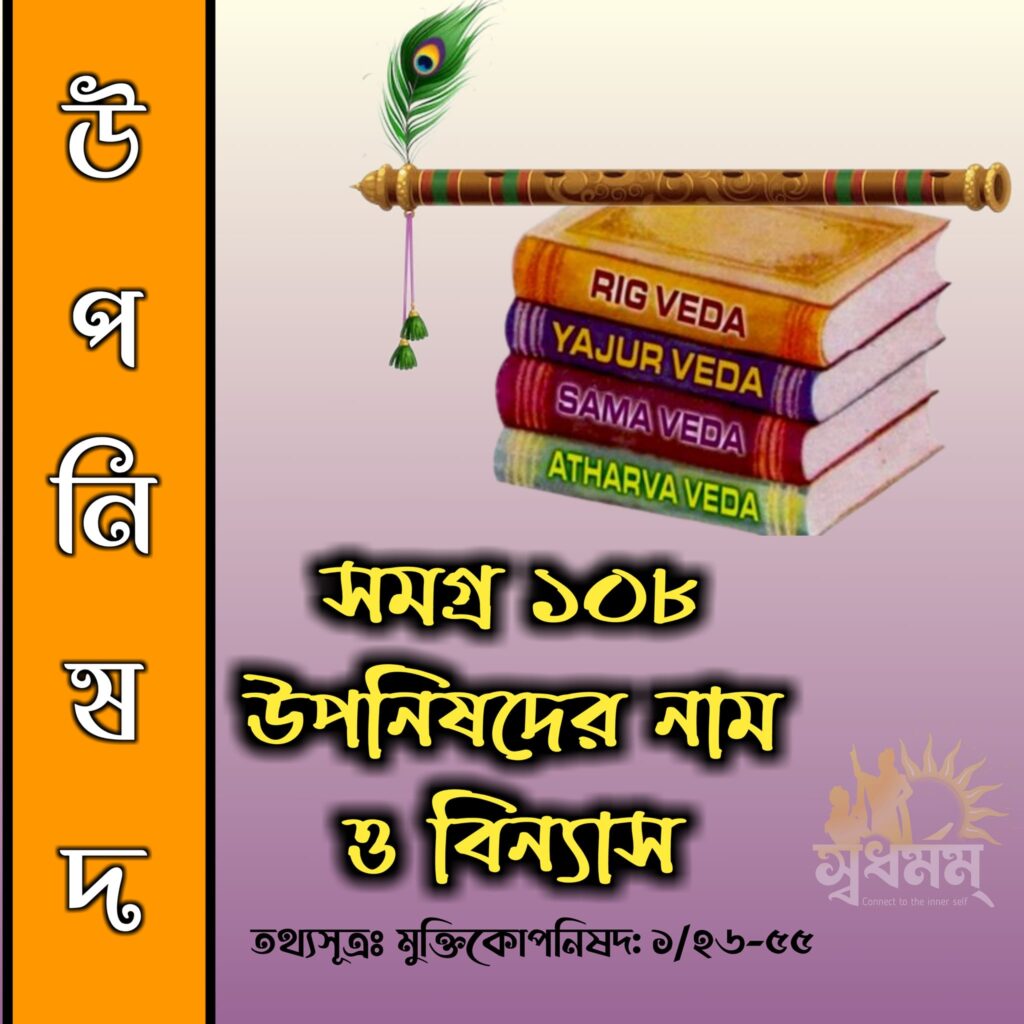
উপনিষদের সংখ্যা বিন্যাস ও মান্যতা নিয়ে অল্পবিদ্যা ভয়ংকরীরা প্রতিনিয়তই প্রপাগাণ্ডা ছড়াতে ব্যস্ত। তারা তাদের নিজস্ব মতাদর্শ প্রচারের স্বার্থে যেসমস্ত উপনিষদাদির তথ্য অনুকূল সেটাকে স্বীকার করে এবং অন্যগুলোকে অপ্রামাণিক ঘোষণা করতে উঠেপড়ে লেগে যায়। এই ধরনের ধৃষ্টতা তারা কেবল উপনিষদের বেলায় দেখায় তা নয়, বৈদিক শাস্ত্র সমূহের মধ্যে যেসমস্ত তথ্য তাদের নির্দিষ্ট আদর্শের সাথে অমিল মনে করে সেই সবগুলোকেই অস্বীকার করে। এমনসব নিন্দিত কার্যের মধ্যে একটি হচ্ছে অষ্টাদশ পুরাণসমুহকে তথা ধর্মশাস্ত্রকে অস্বীকার করা। তাই বেদ’ জ্ঞানের তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ মহর্ষি মনু পূর্ব হতেই এসব বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন। মনুসংহিতায় (২/১০,১১) উল্লেখ রয়েছে- “বেদকে শ্রুতি ও ধর্মশাস্ত্রকে স্মৃতি বলা হয়, ঐ শ্রুতি ও স্মৃতি বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা মীমাংসা করিবে না। যেহেতু, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম স্বয়ং প্রকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে।।১০।। যে ব্যক্তি প্রতিকূল তর্ক দ্বারা মূলস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রকে অবমাননা করে, সাধু লোকেরা সেই বেদনিন্দক নাস্তিককে দ্বিজের কর্তব্য কর্ম্ম অধ্যয়নাদি সকল অনুষ্ঠান হইতে বহিস্কৃত করিবেন।। ১১।।” এখানে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, যারা সমস্ত ১০৮ উপনিষদ সমূহকে, ১৮ পুরাণকে অস্বীকার করে তারা বেদনিন্দক আর বেদনিন্দক ব্যক্তি মাত্রই নাস্তিক। তাই বিদ্বান ব্যক্তি মাত্রের উচিত এইরকম নাস্তিকদের বিভ্রান্তিকর তথ্য দ্বারা প্রতারিত না হয়ে সত্যানুসন্ধান করা। অতএব, উপনিষদ সমূহের সংখ্যা, নাম ও বিন্যাস নিয়ে শুক্লযজুর্বেদীয় মুক্তিকোপনিষদেই (১/২৬-৫৫) সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। “মুক্তিক উপনিষদ” অনুযায়ী আমরা ১০৮টি উপনিষদের সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেখতে পাই। এই ১০৮ উপনিষদের মধ্যে মুক্তিকোপনিষদ বলেন যে- ঋগ্বেদীয় উপনিষদ : ১০ (দশ) টি শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় : ১৯ (উনিশ) টি কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় : ৩২ (বত্রিশ) টি সামবেদীয় :১৬ (ষোল) টি অথর্ব্ববেদীয় : ৩১ (একত্রিশ) টি ঋগবেদ অন্তর্গত ১০টি উপনিষদ: ১) ঐতরেয়, ২) কৌষীতকী, ৩) নাদবিন্দু, ৪) আত্মপ্রবোধ, ৫) নির্ব্বাণ, ৬) মুদগলা, ৭) অক্ষমালিকা, ৮) ত্রিপুরা, ৯) সৌভাগ্য ও ১০) বহ্বৃচ শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত ১৯টি উপনিষদ : ১) ঈশ, ২) বৃহদারণ্যক, ৩) জাবাল, ৪) হংস, ৫) পরমহংস, ৬) সুবাল, ৭) মন্ত্রিকা, ৮) নিরালম্ব, ৯) ত্রিশিখী, ১০) ব্রাহ্মণমণ্ডল, ১১) ব্রাহ্মণদ্বয়তারক, ১২) পৈঙ্গল, ১৩) ভিক্ষু, ১৪) তুরীয়, ১৫) অতীতাধ্যাত্ম, ১৬) তারসার, ১৭) যাজ্ঞবল্ক্য, ১৮) শাট্যায়নী ও ১৯) মুক্তিকা কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ এর অন্তর্গত ৩২টি উপনিষদ : ১) কঠবল্লী, ২) তৈত্তিরীয়, ৩) ব্রহ্ম, ৪)কৈবল্য, ৫) শ্বেতাশ্বতর, ৬) গর্ভ, ৭) নারায়ণ, ৮) অমৃতবিন্দু, ৯) অমৃতনাদ, ১০) কালাগ্নিরুদ্র, ১১) ক্ষুরিকা, ১২) সর্ব্বসার, ১৩) শুকরহস্য, ১৪) তেজোবিন্দু, ১৫) ধ্যানবিন্দু, ১৬) ব্রহ্মবিদ্যা, ১৭) যোগতত্ত্ব, ১৮) দক্ষিণামূর্তি, ১৯) স্কন্দ, ২০) শারীরক, ২১) যোগশিখা, ২২) একাক্ষর, ২৩) অক্ষি, ২৪) অবধূত, ২৫) কঠরুদ্র, ২৬) হৃদয়, ২৭) যোগকুগুলিনী, ২৮) পঞ্চব্রহ্ম, ২৯) প্রাণাগ্নিহোত্র, ৩০) বরাহ, ৩১) কলিসন্তরণ ও ৩২) সরস্বতীরহস্য সামবেদ এর অন্তর্গত ১৬টি উপনিষদ : ০১) কেন, ০২) ছান্দোগ্য, ০৩) আরুণি, ০৪) মৈত্রায়ণী, ০৫) মৈত্রেয়ী, ০৬) বজ্রসূচিক, ০৭) যোগচুড়ামণি, ০৮) বাসুদেব, ০৯) মহৎ, ১০) সংন্যাস, ১১) অব্যক্ত, ১২) কুণ্ডিকা, ১৩) সাবিত্রী, ১৪) রুদ্রাক্ষ, ১৫) জাবালদর্শন ও ১৬) জাবালী অথর্ব্ববেদ এর অন্তর্গত ৩১টি উপনিষদ : ০১) প্রশ্ন, ০২) মুণ্ডক, ০৩) মাণ্ডুক্য, ০৪) অথর্ব্বশিরঃ, ০৫) অথর্ব্বশিখা, ০৬) বৃহজ্জাবাল, ০৭) নৃসিংহ তাপনী, ০৮) নারদ পরিব্রাজক, ০৯) সীতা, ১০) সরভ, ১১) মহানারারণ, ১২) রামরহস্য, ১৩) রামতাপনী, ১৪) শাণ্ডিল্য, ১৫) পরমহংস পরিব্রাজক, ১৬) অন্নপূর্ণা, ১৭) সূর্য্যাত্ম, ১৮) পাশুপত, ১৯) পরব্রহ্ম, ২০) ত্রিপুরাতপন, ২১) দেবী, ২২) ভাবনা, ২৩) ভস্ম, ২৪) জাবাল, ২৫) গণপতি, ২৬) মহাবাক্য, ২৭) গোপালতাপন, ২৮) কৃষ্ণ, ২৯) হয়গ্রীব, ৩০) দত্তাত্রেয় ও ৩১) গারুড় আরও দুটি কথা এখানে না বললেই নয় যে, কালান্তরের মানুষের চর্চার অভাবে এসব শাস্ত্র আজ বিলুপ্তির পথে। আবার এখনও যেগুলো পাওয়া যায় তার অনেক মন্ত্র/শ্লোক আজ হারিয়ে গিয়েছে। যেমন- কলিসন্তরণ উপনিষদ, বজ্রসূচিকোপনিষদে বর্তমানে কয়েকটি মন্ত্রসংখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু তার মানেই এই নয় যে এগুলো মানবসৃষ্ট বা অগ্রহণযোগ্য। আমাদের শাস্ত্রবিমুখতার কারণেই চর্চার অভাবে দিন দিন এগুলো আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাই পাঠক মহলের কাছে অনুরোধ থাকবে যেন আমরা আমাদের বৈদিক শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করি এবং নিজ দায়িত্বে তা সংরক্ষণ করি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। – প্রবীর চৈতন্যচন্দ্র দাস


 Views Today : 144
Views Today : 144 Total views : 94652
Total views : 94652 Who's Online : 0
Who's Online : 0 Your IP Address : 216.73.216.27
Your IP Address : 216.73.216.27