বৈদিক শাস্ত্রে কোথায় ঈশ্বরের সাকারত্ব এবং মূর্তিপূজার উল্লেখ আছে?

[বি:দ্রঃ- কতিপয় দল ঈশ্বরের সাকারত্ব ও মূর্তি পুজা অস্বীকার করার জন্যে বিভিন্ন ভাবগম্ভী দেখাবে। যেমন এই ভাষ্য বিকৃত আমাদের ভাষ্যই স্বীকৃত। তাদের জানিয়ে রাখি এই আর্টিকেলটিতে সম্পূর্ণ ৬০+ উপরে শাস্ত্রীয় প্রমাণ সহ দেওয়া হয়েছে সেও একটি শাস্ত্র থেকে নয়, একাধিক শাস্ত্র থেকে (ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ, উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, পঞ্চরাত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, অন্যান্য অনুগামী শাস্ত্র)।] বেদে ঈশ্বরকে সাকার বলা হয়েছে। আর আমরা তো জানি, দেবতারা সাকার। সুতরাং, বেদ শাস্ত্রে যে ঈশ্বর এবং দেবতাদের শ্রীমূর্তি বা শ্রীবিগ্রহকে আরাধনা বা পূজা করার বিধান প্রদত্ত আছে, এটিই স্বাভাবিক। যদিও বেদ এবং অন্যন্যা সনাতনী শাস্ত্র অনুসারে পরমেশ্বর ভগবানের সুন্দর অপ্রাকৃত দেহ বিদ্যমান, কিন্তু আমরা সে অপ্রাকৃত দেহ প্রাকৃত চক্ষু দিয়ে দেখতে পাব না।তার জন্য চিন্ময় বা অপ্রাকৃত চক্ষু প্রয়োজন।তাই বেদে পরমেশ্বর ভগবান এবং দেবতাদের শ্রীমূর্তি/ শ্রীবিগ্রহ নির্মান করে, উপযুক্ত মন্ত্রের মাধ্যমে অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে, সে মুর্তিতে ভগবান ও দেবতা অধিষ্ঠান হয়েছেন,এরুপ চিন্তা করে তাদের পূজা ও বন্দনা করার নির্দেশ প্রদত্ত হয়েছে। ১। ঋগ্বেদ থেকে প্রমাণ~ इ॒दं विष्णु॒र्वि च॑क्रमे त्रे॒धा नि द॑धे प॒दम्। समू॑ळ्हमस्य पांसु॒रे ॥ ইদং বিষ্ণুর্বি চক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূলহমস্য পাংসুওে॥ – [ঋগ্বেদ ১/ ২২/ ১৭] অর্থাৎ, “বিষ্ণু এ জগৎ পরিক্রমা করেছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করেছিলেন, তাঁর ধুলিযুক্ত পদে জগৎ আবৃত হয়েছিল।” त्रीणि॑ प॒दा वि च॑क्रमे॒ विष्णु॑र्गो॒पा अदा॑भ्यः। अतो॒ धर्मा॑णि धा॒रय॑न् ॥ ত্রীণি পদা বি চক্রমে বিষ্ণু র্গোপা অদাভ্যাঃ। অতো ধর্মাণি ধারয়ন্॥ – [ঋগ্বেদ ১/ ২২/১৮] অর্থাৎ, “বিষ্ণু রক্ষক, তাঁকে কেহ আঘাত করতে পারে না, তিনি ধর্ম সমুদয় ধারণ করে তিন পদ পরিক্রমা করেছিলেন।” तद्विष्णो॑: पर॒मं प॒दं सदा॑ पश्यन्ति सू॒रय॑:। दि॒वी॑व॒ चक्षु॒रात॑तम् ॥ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ – [ঋগ্বেদ ১/২২/২০] অর্থাৎ, “আকাশে সর্বতো বিচারী যে চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেরূপ দৃষ্টি করেন।” तद्विप्रा॑सो विप॒न्यवो॑ जागृ॒वांस॒: समि॑न्धते। विष्णो॒र्यत्प॑र॒मं प॒दम् ॥ তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে। বিষ্ণো র্যৎ পরমং পদম॥ – [ঋগ্বেদ ১/২২/২১] অর্থাৎ, “স্তুতিবাদক ও সদাজাগরূক মেধাবী লোকেরা যে বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন।” दि॒वश्चि॑दस्य वरि॒मा वि प॑प्रथ॒ इन्द्रं॒ न म॒ह्ना पृ॑थि॒वी च॒न प्रति॑ । भी॒मस्तुवि॑ष्माञ्चर्ष॒णिभ्य॑ आत॒पः शिशी॑ते॒ वज्रं॒ तेज॑से॒ न वंस॑गः ॥ divaś cid asya varimā vi papratha indraṃ na mahnā pṛthivī cana prati | bhīmas tuviṣmāñ carṣaṇibhya ātapaḥ śiśīte vajraṃ tejase na vaṃsagaḥ || – [ঋগ্বেদ:- ১/৫৫/১] অর্থাৎ, হে অধ্বর্যুগণ! তোমরা স্তুতিপ্রিয় মহাবীর ইন্দ্রের নিমিত্ত এবং বিষ্ণুর জন্য পানীয় সোমরস যত্নপূর্বক প্রস্তুত কর। তাঁর উভয়ে দুর্ধর্ষ ও মহীয়ান। তাঁরা মেঘের উপর ভ্রমণ করেন, যেন সুশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করে ভ্রমণ করছেন। च॒तुर्भि॑: सा॒कं न॑व॒तिं च॒ नाम॑भिश्च॒क्रं न वृ॒त्तं व्यतीँ॑रवीविपत् । बृ॒हच्छ॑रीरो वि॒मिमा॑न॒ ऋक्व॑भि॒र्युवाकु॑मार॒: प्रत्ये॑त्याह॒वम् ॥ caturbhiḥ sākaṃ navatiṃ ca nāmabhiś cakraṃ na vṛttaṃ vyatīm̐r avīvipat | bṛhaccharīro vimimāna ṛkvabhir yuvākumāraḥ praty ety āhavam || – [ঋগ্বেদ:- ১/১৫৫/৬] অর্থাৎ, ঈশ্বরের বৃহৎ শরীর (बृहत्शरीरः । bṛhat-śarīraḥ |) আছে। यः पूर्व्याय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति । यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर्युज्यं चिदभ्यसत् ॥ যঃ পূর্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি। যঃ জাতমস্য মহতো মহি ব্রবৎ সেদূ শ্রবোভির্যূজ্যং চিদভ্যসৎ॥ yaḥ pūrvyāya vedhase navīyase sumajjānaye viṣṇave dadāśati | yo jātam asya mahato mahi bravat sed u śravobhir yujyaṃ cid abhy asat || – [ঋগ্বেদ :- ১/১৫৬/২] “যে মনুষ্য প্রাচীন, মেধাবী, নিত্য নতুন ও সূমজ্জানি বিষ্ণুকে হব্য প্রদান করেন; যিনি মহানুভব বিষ্ণুর পূজনীয় জন্ম (কথা) কীর্তন করেন, তিনিই যুজ্য (ভগবানের ধাম) প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ, তিনি জন্ম নেন (यः । जातम् । अस्य । yaḥ | jātam | asya |)। प॒रो मात्र॑या त॒न्वा॑ वृधान॒ न ते॑ महि॒त्वमन्व॑श्नुवन्ति । उ॒भे ते॑ विद्म॒ रज॑सी पृथि॒व्या विष्णो॑ देव॒ त्वं प॑र॒मस्य॑ वित्से ॥ পরো মাত্রয়া তন্বা বৃধান ন তে মহিত্বমন্বশ্নুবন্তি। উভে তে বিদ্ম রজসী পৃথিব্যা বিষ্ণো দেব ত্বং পরমস্য বিৎসে॥ – [ঋগ্বেদ ৭/৯৯/১] অর্থাৎ, “হে বিষ্ণু, তুমি মাত্রার অতীত শরীরে বর্ধমান হলে তোমার মহিমা কেউ অনুব্যাপ্ত করতে পারে না, পৃথিবী হতে আরম্ভ করে উভয় লোক আমরা জানি, কিন্তু তুমিই কেবল হে দেব, পরমলোক অবগত আছ।” नू मर्तो॑ दयते सनि॒ष्यन्यो विष्ण॑व उरुगा॒याय॒ दाश॑त् । प्र यः स॒त्राचा॒ मन॑सा॒ यजा॑त ए॒ताव॑न्तं॒ नर्य॑मा॒विवा॑सात् ॥ নূ মর্তো দয়তে সনিষ্যন্যো বিষ্ণব উরুগায়ায় দাশ। প্র যঃ সত্রাচা মনসা যজাত এতাবন্তং নর্যমাবিবাসাৎ।। nū marto dayate saniṣyan yo viṣṇava urugāyāya dāśat | pra yaḥ satrācā manasā yajāta etāvantaṃ naryam āvivāsāt || – [ঋগ্বেদ:-৭/১০০/১] অর্থাৎ, যিনি বহুলোকের কীর্তনীয় বিষ্ণুকে হব্য দান করেন, যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা পূজা করেন এবং মনুষ্যগণের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা করেন সে মর্ত্যধন ইচ্ছা করে শীঘ্র প্রাপ্ত হন। বিশ্লেষণ: যদি বিগ্রহ বা শ্রীমূর্তি পূজা বেদবিহিত না হত,তাহলে এ মন্ত্রে পূজা,পরিচর্যার প্রসঙ্গই আসতো না। अर्च॑त॒ प्रार्च॑त॒ प्रिय॑मेधासो॒ अर्च॑त । अर्च॑न्तु पुत्र॒का उ॒त पुरं॒ न धृ॒ष्ण्व॑र्चत ॥ অচর্ত প্রার্চত প্রিয়মেধসো অচর্ত। অচন্তু পুত্রকা উত পুরং ন ধৃঞ্চবচর্ত।। arcata prārcata priyamedhāso arcata| arcantu putrakā uta puraṃ na dhṛṣṇv arcata || – [ঋগ্বেদ:- ৮/৬৯/৮] অর্থাৎ, হে প্রিয়মেধগণ! তোমরা ইন্দ্রক অর্চনা কর। বিশেষরূপে অর্চনা কর, পুত্রগণ পুরবিদারীকে যেরূপ অর্চনা করে, সেরূপ ইন্দ্রের অর্চনা করুক। বিশ্লেষণ: বেদে ঈশ্বরকে ইন্দ্র বলা হয়েছে। বিগ্রহ আরাধনা বা শ্রীমুর্তি পূজা বেদবিহিত না হতো তবে উক্ত মন্ত্রে ইন্দ্রকে বিশেষ রূপে অর্চনা বা পূজা করার প্রসঙ্গ আসতো না। কারন নিরাকার ঈশ্বরকে কখনো পূজা করার কথা শাস্ত্রে বলা হয় না। সুতারাং মুর্তি পূজা বেদবিহিত। विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात् । सं बाहुभ्यां धमति सं पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन्देव एकः ॥ viśvataścakṣur uta viśvatomukho viśvatobāhur uta viśvataspāt | sam bāhubhyāṃ dhamati sam patatrair dyāvābhūmī janayan deva ekaḥ || – [ঋগ্বেদ:- ১০/৮১/৩] অর্থাৎ, সর্বত্র তার হাত, পা, মূখ, চোখ (वि॒श्वत॑श्चक्षुरु॒त वि॒श्वतो॑मुखो वि॒श्वतो॑बाहुरु॒त वि॒श्वत॑स्पात् ।)। स॒हस्र॑शीर्षा॒ पुरु॑षः सहस्रा॒क्षः स॒हस्र॑पात्। स भूमिं॑ वि॒श्वतो॑ वृ॒त्वात्य॑तिष्ठद्दशाङ्गु॒लम् ॥ সহস্রাশীর্ষা পুরুষাঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রাপাৎ। স ভূমিং বিশ্বতো বৃহাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্ ॥ – [ঋগ্বেদ১০/৯০/১] অর্থাৎ, “পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ।…” कासी॑त्प्र॒मा प्र॑ति॒मा किं नि॒दान॒माज्यं॒ किमा॑सीत्परि॒धिः क आ॑सीत् । छन्द॒: किमा॑सी॒त्प्रउ॑गं॒ किमु॒क्थं यद्दे॒वा दे॒वमय॑जन्त॒ विश्वे॑ ॥ কাসীৎপ্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎপরিধিঃ ক আসীৎ। ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুকথং যদ্দেবা দেবমযজন্ত বিশ্বে।। kāsīt pramā pratimā kiṃ nidānam ājyaṃ kim āsīt paridhiḥ ka āsīt | chandaḥ kim āsīt praügaṃ kim ukthaṃ yad devā devam ayajanta viśve || – [ ঋগ্বেদ ১০/১৩০/৩ ] অর্থাৎ, যে কালে সকল দেবতা দেবপূজা করলেন তখন তাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের পরিমাণ কি ছিল? দেব মূর্তি বা কি ছিল? সংকল্প কি ছিল? ঘৃত কি ছিল? পরিধি অর্থাৎ যজ্ঞস্থানের চতুর্দিকের বৃত্তি স্বরূপ সীমা বন্ধনই বা কি ছিল? ছন্দ প্রয়োগই বা কি ছিল? বিশ্লেষণ: উক্ত মন্ত্রে মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি বর্তমানের কথা অনুধাবন করে পূর্বের অবস্থা বুঝার জন্য প্রশ্ন করেছেন। এই মন্ত্রে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সময় দেব মূর্তি বিদ্যমান ছিল এবং তাহার পূজাও করা হতো।এ বেদ মন্ত্র থেকে বুঝা যায় দেবতাদের শ্রীমূর্তির পূজা বেদবিহিত। ক্ষীরেণ স্নাপিতা দুর্গা চন্দনেনানুলেপিতা।
আমরা কেন সাত্ত্বিক আহার গ্রহণ করব?
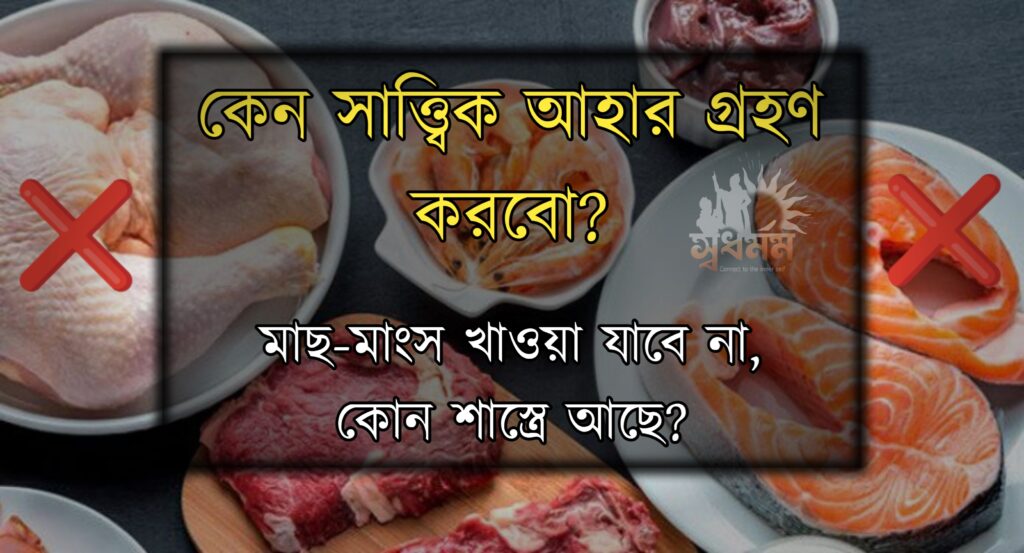
♦অসাবি দেবং গোঋজীকমন্ধো ন্যস্মিন্নিন্দ্রো জনুষেমুবোচ। বোধামসি ত্বা হয়র্শ্ব য়জ্ঞৈবোধা ন স্তোমমন্ধসো মদেষু॥ (সামবেদ ৩১৩) অথবা (সামবেদ ৯/৩/১) 🍎সরলার্থঃ আহার সেটিই উত্তম যা কিনা উৎপাদন করা হয়েছে। আহার ভূমিমাতা থেকে উৎপন্ন শস্যাদিরই করা উচিত, সাথে গোদুগ্ধ। এই আহারই সাত্ত্বিক ও দৈবী সম্পত্তির জন্মদাতা। এই সাত্ত্বিক ভোজনে নিশ্চিতভাবেই, স্বভাবতই ইন্দ্রিয়সমূহের শাসক হওয়া যায়, দাস নয়। অর্থাৎ সাত্ত্বিক ভোজন দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করা যায়। পক্ষান্তরে রাজসিক ও তামসিক আহার ইন্দ্রিয়ের দাসত্বের কারণ। প্রভু উপদেশ দিচ্ছেন শীঘ্রতাযুক্ত ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বযুক্ত মানব ! তোমাকে যজ্ঞসমূহ দ্বারা জ্ঞানযুক্ত করি। ভক্ত বলছেন, সাত্ত্বিক আহারের আনন্দে বিহ্বলিত আমাদের স্তুতি সমূহকেও জ্ঞাত হও। অর্থাৎ, সাত্ত্বিক আহারী মানব প্রভুকে বিস্মৃত হয় না। বরং সর্বদা স্মরণ করে। ★ব্রীহিমন্নং যবমত্তমথো মাষমথো তিলম । এষ বাং ভাগো নিহিতো রত্নেধেয়ায় দন্তৌ মা হিংসিষ্ট পিতরং মাতরং চ।। (অথর্ববেদ ৬।১৪০।২) — হে দন্ত! অন্ন খাও যব খাও মাষ কালাই এবং তিল খাও তোমার এই ভাগ উত্তম পদার্থ ধারনের জন্য স্থাপন করা হয়েছে হে দন্ত! পিতা ও মাতাকে হিংসিত করো না [মাংসাহার থেকে দূরে থাকো] এবং বেদ মন্ত্রে সেই পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে যে, আমাদের দন্ত যেন ব্যাঘের ন্যায় না হয়। কারন বাঘের দন্ত সর্বদা মাংসাহার করে থাকে। সে জন্য আমাদের দন্ত কে ব্যাঘের ন্যায় না করে কল্যাণকারী করো। ★যৌ ব্যাঘ্রাববরূঢৌ জিঘত্সতঃ পিতরং মাতরং চ। তৌ দন্ত ব্রহ্মণস্পতে শিবৌ কৃণু জাতবেদঃ।। (অথর্ববেদ ৬।১৪০।১) — যে দন্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় পিতা ও মাতাকে খাওয়ার জন্য চেষ্টা করে সেই দাঁত কে হে সর্বব্যাপক জ্ঞানের পরিপালক কল্যাণকারী করো। অর্থাৎ বেদ আমাদের সর্বদাই কল্যাণকারী হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন। যাতে করে আমাদের কাছ থেকে কেউ যেন কষ্ট না পায়। আমরা যেন নিরীহ প্রাণীদের হিংসা না করি। কারন, “অহিংসা পরম ধর্ম ” (মহাঃ আদিঃ অঃ ১১, শ্লোঃ ১৩) এবং “হিংসা অধর্মস্তথহিত” (মহাঃ শান্তিঃ ২৭২, শ্লোক ১৮) হিংসা অধর্ম এবং অহিতকর। “প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজায়ান্” (মহাঃ কর্ণ পর্ব, অঃ ২৬৯, শ্লোক ২৩) অর্থাৎ প্রাণীদের বধ না করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ★জীবিতুং যঃ স্বযং চেচ্ছেত্ কথং সোন্যং প্রঘাতয়েত। যদ যদাৎমসি চেচ্ছেত তত পরস্যাপি চিন্তয়েত।। (মহাঃ শান্তি পর্ব, অঃ ২৫৯, শ্লোক ২২) উপরিউক্ত মন্ত্রগুলি দ্বারা এটা স্পষ্ট যে, বেদ কোন নির্দোষ পশু কে হত্যার উপদেশ করে নি।বরং উপদেশ করেছে, পশুস্ত্রাঁয়েথাঙ (যজুর্বেদ ৭/৬/১১) অর্থাৎ পশুদের রক্ষা করো এবং তাদের বর্ধিত করো।কারন বেদ সর্বদাই কল্যাণময়। ♦মহাভারতের_অনুশাসন_পর্বের, ১০০তম অধ্যায়ের, ৩৭, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৪৮, ৪৯ নং শ্লোকে #পিতামহ_ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় #যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন- “যারা সৌন্দর্য, সাস্থ্য, বল, আয়ু, বুদ্ধি, স্মরণ শক্তি চান তারা মাংস আহার ত্যাগ করেন। মনু বলেছেন, যিনি মাংস আহার ও পশু হত্যা করেন না তিনি সর্বজীবের মিত্র ও বিশ্বাসের পাত্র। নারদ বলেছেন, যে পরের মাংস খেয়ে নিজের পেশী বৃদ্ধি করেন সে অশেষ কষ্ট ভোগ করে। মাংসাশী লোক যদি মাংসাহার ত্যাগ করে তবে সে যে ফল পায় বেদ অধ্যায়ন ও সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেও কেউ সেই ফল পায় না। মাংস ভোজনে আসক্তি জম্মালে তা ত্যাগ করা অতীব কঠিন। মাংস বর্জন ব্রত পালন করলে সকল প্রাণী অভয় লাভ করে। যদি মাংসভোজী না থাকে তবে কেউ পশুহনন করে না, মাংসখাদকের জন্যই পশুঘাতক হয়। যে পরমাংস দ্বারা নিজ মাংস বৃদ্ধি করতে চায় তার চেয়ে ক্ষুদ্র আর নৃশংস কেউ নেই!” মনুসংহিতায় মাছ-মাংস ভক্ষণে কি ভয়ংকর পাপ ও শাস্তি এবং আমিষাহার বর্জনে কি পুন্য লাভ হয় তার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে- মনুসংহিতায় মাছ ভক্ষণ নিষিদ্ধঃ ★যো যস্য মাংসমশ্লানি স তন্মাংসাদ উচ্যতে। মৎস্যাদঃ সর্বমাংসাদস্তম্মান্মত্স্যান্ বিবর্জয়েৎ।। 🔴[ মনুসংহিতা ৫/১৫ ]🔴 ~ যে যার মাংস খায় তাকে ‘তন্মাংসাদ’ অর্থাৎ তার মাংসভোজী বলে (যেমন, বিড়াল ইঁদুরের মাংস খায়, তাই বিড়াল ‘মূষিকাদ’, নকুল অর্থাৎ বেজী ‘সর্পাদ’); কিন্তু যে ‘মৎস্যাদ’ অর্থাৎ মাছ-ভোজী, তাকে সর্বমাংসভোজী বলা চলে। (এমন কি তাকে ‘গো-মাংসদ’ও বলা যায়)। অতএব মৎস্য-ভোজনে যেহেতু সমস্ত প্রকার মাংস ভক্ষণের সমান বিষম পাপ হয়, তাই সর্বতভাবে মৎস্যভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকবে ।। মনুসংহিতায় মাংস ভক্ষণে পাপ ও ভয়ংকর শাস্তি ★মাংসভোজীরা মৃত্যুর পর যাদৃশ্য দুঃখসহ দুঃখরাশি ভোগ করে।(মনু সংহিতা ৫/৩৪) ★যে ব্যক্তি হিংসাদিশূণ্য হরিণ এবং হরিণের ন্যায় হিংসাশূণ্য অন্যান্য পশুকে আপন সুখের জন্য হত্যা করে সে কি জীবিত অবস্থায়, কি পরলোকে উভয়েই সুখ পায় না।(মনুসংহিতা ৫/৪৫) ★যিনি প্রাণীদিগকে বন্ধন-ধাদি দ্বারা কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না ও যিনি সকলের হিতকামী, তিনি অত্যন্ত সুখভোগ করেন। (মনুসংহিতা৫/৪৬) ★যিনি কাহাকেও হিংসা করেন না, তিনি যা ধ্যান করেন, যে কিছু ধর্মের অনুষ্ঠান করেন,এবং যে বিষয়ে মনােনিবেশ করেন—সেই সমুদয়ই অনায়াসে লাভ করিয়া থাকেন। (মনুসংহিতা ৫/ ৪৭) ★প্রাণি হিংসা না করিলে মাংস উতপন্ন হয় ,প্রাণিবধও নরকের কারণ,অতএব মাংস ভক্ষন করবে না(মনুসংহিতা ৫/৪৮) ★শুক্রশোশিত দ্বারা মাংসের উতপত্তি।অতএব ইহা ঘৃণিত; বধ ও বন্ধন নিষ্ঠুর হৃদয়ের কর্ম;ইহা নিশ্চিত করিয়া সাধুরা বিহিত মাংস ভক্ষনেও হইতেও নিবৃত্ত হয়;অবৈধ মাংস ভক্ষনের কথা আর কিই বা বলিব?(মনুসংহিতা ৫/৪৯) ★যিনি পশুবধ করতে অনুমতি দেন, যিনি অস্ত্রাদির দ্বারা পশুর অঙ্গপ্রতঙ্গ খন্ড খন্ড করেন, যিনি পশু বধ করেন, যিনি সেই প্রাণীর মাংস ক্রয় করে, যিনি তা বিক্রয় করেন, যিনি মাংস পাক করেন, যিনি পরিবেশন করেন এবং যিনি মাংস ভক্ষণ করেন তারা সকলেই সেই পশুর ঘাতক রূপে অভিহিত হন ৷ (মনুসংহিতা ৫/৫১) ★যে ব্যক্তি শতবর্ষ ব্যাপিয়া বৎসর বৎসর অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন মাংস ভোজন না করেন,এই উভয়েরই পূর্ণফল সমান। (মনুসংহিতা ৫/৫৩) ★ইহলোকে আমি যার মাংস ভক্ষন করিতেছি,পরলোকে সে আমাকে ভক্ষন করবে।পন্ডিতেরা মাংস (মাং-আমায়,সঃ-ভক্ষন করিবে) শব্দের এইরূপ ব্যাখা করেছেন।(মনুসংহিতা ৫/৫৫) শ্রী বিষ্ণুপুরাণে জীবহত্যা ও মাংসাহারের শাস্তির বর্ণনা: ১) ভ্রুণহত্যাকারী, গো-বধকারী শ্বাসরুদ্ধকর রোধ নরকে যায়। ♦[বিষ্ণুপুরাণ ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ৭]🏵 ২) পশুপাখি পালন করে তার মাংস ভক্ষণ করে জীবনধারণকারী, মাংস বিক্রেতা পূয়বহ নরকে মলভক্ষণ করে। ♦[বিষ্ণুপুরাণ ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ২০-২১]🏵 ৩) ধীবর বা জেলেরা রুধিরান্ধ নরকে যায়। ♦[বিষ্ণুপুরাণ ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ২২]🏵 ৪) মেষ (ভেড়া )পালন করে ভক্ষণকারী, পশুপাখি শিকারীরা বহ্নিজাল নরকে অগ্নিদগ্ধ হয়। ♦[বিষ্ণুপুরাণ ২য় খন্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, শ্লোক ২৬]🏵 ৫)”যদি যজ্ঞে বলিদান করলে পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহলে যজমান তাঁর পিতাকে কেন মেরে ফেলেন না?” ♦[বিষ্ণুপুরাণ, ৩/১৮/২৮]🔴 ৬)স্বর্গার্থং যদি বো বাঞ্ছা নির্বাণার্থমথাসুরা। তদলং পশুঘাতাদিদুষ্টধর্মৈৰ্নিবোধত৷৷ ♦( বিষ্ণুপুরাণ ৩।১৮।১৭)🔴 অনুবাদ: হে অসুরগণ ! যদি তোমাদের স্বর্গ বা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে পশুহিংসা ইত্যাদি দুষ্কর্ম ত্যাগ করে বোধ প্রাপ্ত করো৷৷ এবার আপনারাই বিবেচনা করুন যে কোন অবস্থাতেই বলি বা পশু হত্যা করা বা তাদের মাংসাহার করা উচিত কি না?
বৈষ্ণবের বর্ণ ও অশৌচ বিচার

“বৈষ্ণব” একটি স্বতন্ত্র বর্ণ: ১)ব্রহ্মক্ষত্রিয়বিটশূদ্রাশ্চতস্রো জাতয়ো যথা। স্বতন্ত্রজাতিরেকা চ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা।।” [ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখন্ড, ১১।৪৩ ] বঙ্গানুবাদঃ ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য ও শূদ্র নামে যেরূপ চারিটি জাতি আছে তদ্রূপ সমগ্র বিশ্বে বৈষ্ণব নামক একটি স্বতন্ত্র জাতি আছে। ২)ললাটাদ্বৈষ্ণবো জাতঃ ব্রাহ্মণো মুখদেশতঃ ৷ ক্ষত্রিয় বাহুমূলাচ্চ ঊরুদেশাচ্চ বৈশ্য বৈ ৷৷ জাতো বিষ্ণোঃ পদাচ্ছুদ্রঃ ভক্তিধর্ম্মবিবর্জিতঃ ৷ তস্মাদ্বৈ বৈষ্ণবঃ খ্যাতঃ চতুর্ব্বর্ণেষু সত্তমঃ ৷৷ ( বৃহদ্বিষ্ণুযামল) অনুবাদ: শ্রী ভগবান্ বিষ্ণুর ললাট হইতে বৈষ্ণব, মুখ হইতে ব্রাহ্মণ,বাহু হইতে ক্ষত্রিয়,ঊরুদেশ হইতে বৈশ্য ,পদদেশ হইতে ভক্তিধর্ম্মবিবর্জিত শূদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে ৷ ইহার মধ্যে যিনি বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত, তিনি চতুর্বর্ণ হইতেও সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম ৷ শ্রীহরির পবিত্র নামস্মরণ হেতু বৈষ্ণবগণ অশৌচ মুক্ত: শাস্ত্রীয় প্রমাণ- অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা যঃ স্মরেৎপুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।।১২ নামসংস্মরণাদেব তথা তৎপাদচিন্তনাৎ ॥ ১৩ [ পদ্মপুরাণ, পাতালখন্ড, অধ্যায় ৪৯, শ্লোক ১২-১৩] অনুবাদ: অপবিত্র বা পবিত্র যে কোন অবস্থাপন্ন হইয়া যে ব্যক্তি পুণ্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করে, সে কি বাহ্য, কি অভ্যন্তর, উভয়াথাই শুচি হইয়া থাকে। ফলে ভগবানের নাম স্মরণ এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মের চিন্তায় সকলে সর্ব্বদা পবিত্র হয়। নিত্য শ্রীহরির চরণামৃত পান/ধারণ হেতু বৈষ্ণবের কোন জন্মাশৌচ/মরণাশৌচ নেই: প্রমাণ: আশৌচং নৈব বিদ্যেত সূতকে মৃতকেছপি চ। যেষাং পাদোদকং মুর্দ্ধি প্রাশনং যে প্রকুর্ব্বতে। [ স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখন্ডে-মার্গশীর্ষমাহাত্ম্যম, শ্লোক ৪০] অনুবাদ: যাহারা বিষ্ণুপাদোদক পান বা মস্তকে ধারণ করে, কি জননাশৌচ, কি মরণাশৌচ, কোন অশৌচই তাহাদের হয় না।
মাছ-মাংস খেয়ে কি ভগবানের সেবা পূজা করা যায়?
অনেকেই এই প্রশ্নটা করে: মাছ-মাংস খেয়ে কি ভগবানের সেবা পূজা করা যায়? আমিষভোজী কিংবা জীবহিংসকদের বিগ্রহ অর্চন নিষিদ্ধ : শ্রী বরাহদেব বসুন্ধরা দেবীকে সেবা অপরাধ সম্পর্কে বলেছেন- ♦”মংস্য মাংস ভক্ষণ করিয়া আমার অর্চ্চনা করা কোন ক্রমেই কৰ্ত্তব্য নহে। তাহা করিলে আমি অষ্টাদশ অপরাধ গণ্য করিয়া থাকি ।” [ বরাহ মহাপুরাণ, অধ্যায় ১১৭, শ্লোক ২১ ] ♦জাল- পাদ, অর্থাৎ হংসাদি জলজ প্রাণি ভক্ষণ করিয়া আমার অর্চ্চনা করা ঊন- বিংশ অপরাধ । [ বরাহ মহাপুরাণ, অধ্যায় ১১৭, শ্লোক ২২ ] ♦”বরাহমাংস ভক্ষণ করা, ত্রয়োবিংশ অপরাধ । যদি কেহ সুরাপান করিয়া আমার অর্চ্চনা করে, আমি তাহা চতুর্ব্বিংশ অপরাধ বলিয়া গণনা করিয়া থাকি।” [ বরাহ মহাপুরাণ, অধ্যায় ১১৭, শ্লোক ২৬,২৭ ] তাই আমিষভোজী বা জীবহিংসকদের বিগ্রহ অর্চণ করতে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তারা চিত্রপট কিংবা ঘট স্থাপন করে পূজা করতে পারেন। এভাবে ব্যাবহারিক ভক্তি করতে করতে একসময় যখন তাদের ভক্তিতে নিষ্ঠা আসবে,তখন তারা তাদের জিভের লালসা বর্জন করে শুদ্ধ প্রসাদভোজীতে পরিণত হবেন। তখন ভগবানই তাদের সে যোগ্যতা প্রদান করবেন। শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল বিগ্রহ অর্চনের অধিকার রাখেন।
বালীকে হত্যা নাকি মুক্তি?

আমরা সবাই কম-বেশী “রামায়ণ” এর মূল কাহিনী সম্পর্কে অবগত আছি। মিত্র সুগ্রীবকে তাঁর হারানো রাজ্য এবং স্ত্রী পুনরুদ্ধারে সাহায্য করতে গিয়ে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আড়াল থেকে তীর নিক্ষেপ করে সুগ্রীব এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে হত্যা করেন। এখানে অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগতে পারে, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, যিনি মর্যাদা পুরুষোত্তম, সর্বকালের আদর্শ রাজা, উন্নত চরিত্রের অধিকারী, অসাধারণ শৌর্য ও বীর্যের অধিকারী, তিনি কেন এ কাজ করলেন? এ কাজ কি অন্যায় ছিল? এ কাজ কি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে কালিমা লেপন করে? নিচের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে আমরা দেখতে পাই, রাম এবং সুগ্রীব মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ হন। সুগ্রীব রামকে প্রতিশ্রুতি দেন সীতামাতাকে উদ্ধারের কাজে তিনি রামচন্দ্রকে সাহায্য করবেন। তিনি আরও বলেন অপহরণকালে সীতামাতাকে তিনি দেখেছেন। যে গহনাগুলো মাতা পুষ্পক রথ থেকে নিচে ফেলেছিলেন সুগ্রীব সেগুলো শ্রীরামকে দেখান। রামচন্দ্রকে সুগ্রীব আশ্বস্ত করেন কিন্তু একই সঙ্গে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ঋষ্যমূখ পর্বতের বাইরে বের হলেই বালী তাঁকে হত্যা করবে। সুগ্রীব বালীর নির্দয়তা এবং শক্তি সম্পর্কে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে অবহিত করেন। রামচন্দ্র বালীকে হত্যা করতে সুগ্রীবকে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। সুগ্রীবের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য রামচন্দ্র নিজের শক্তি,ক্ষমতা এবং ধনুর্বিদ্যার প্রমাণ দেন। সুগ্রীব এতে সাহস পান এবং বালীকে যুদ্ধে আহবান করেন। বালী রণক্ষেত্রে এসে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। এদিকে রামচন্দ্র ঝোপের আড়ালে তীর-ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইলেন। [ রামায়ণে সুগ্রীব এবং বালীর যুদ্ধে আমরা বালীর গলাতে একটি কণ্ঠহার (কাঞ্চনী মালা) দেখতে পাই। এই কণ্ঠহার বালী ইন্দ্র কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এখানে অনেকের একটি ভুল ধারণা আছে, এই অলঙ্কার তাঁকে যার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছেন তাঁর শক্তির অর্ধেক প্রদান করতো। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এই অলঙ্কার যুদ্ধের আগে ও পরে বালীর শক্তি সমান রাখতো (সূত্র- বাল্মীকি রামায়ণ)। ] প্রথমে শ্রীরামচন্দ্র বালী এবং সুগ্রীবকে পৃথক করে চিনতে পারেন নি। দুইজনকে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখতে একই রকম লাগছিল। বালীকে আঘাত করতে গিয়ে ভুলবশত সুগ্রীবকে যেন প্রহার না করেন এইজন্য রামচন্দ্র কোনও বাণ নিক্ষেপ করলেন না। সুগ্রীব প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হন এবং পালিয়ে আসেন। রামচন্দ্র সুগ্রীবকে দ্বিতীয়বার বালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অবতীর্ণ হতে বলেন এবং আশ্বস্ত করেন যে তিনি বালীকে এবার হত্যা করবেনই। রামচন্দ্র কর্তৃক নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে সুগ্রীব দ্বিতীয়বার বালীকে যুদ্ধে আহবান করেন। বালীর স্ত্রী, তারা, বালীকে এবার সুগ্রীবের সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন। কিন্তু অহঙ্কারে মত্ত বালী স্ত্রীর কোন কথাই শুনলেন না। যুদ্ধমধ্যে সুগ্রীব রামচন্দ্রের সাহায্যের জন্য চিৎকার করলেন। বালীকে লক্ষ্য করে রামচন্দ্র বাণ নিক্ষেপ করলেন। বাণ বালীর বুকে বিদ্ধ হল। রামচন্দ্র নিক্ষেপিত শক্তিশালী বাণ বুকে বিদ্ধ হওয়ার পরেও ইন্দ্রদেব প্রদত্ত কণ্ঠহারের প্রভাবে বালী সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন না। এখানে মর্যাদা পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের চরিত্রের ওপর প্রশ্ন উঠতেই পারে। কেনো তিনি ছলনার আশ্রয় নিলেন? কেনো তিনি লুকিয়ে থেকে বাণ নিক্ষেপ করলেন? বাণ নিক্ষেপের পরে রামচন্দ্র বালীর সম্মুখে উপস্থিত হলেন। বালী রামচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে গর্বিত বচনে বললেন, “কুলীনঃ সত্ত্বসম্পন্নস্তেজস্বী চরিতব্রতঃ। রামঃ করুণবেদী চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ ।। সানুক্রোশো মহোৎসাহঃ সময়জ্ঞো দৃঢ়ব্রতঃ। ইত্যেতৎ সর্বভূতানি কথয়ন্তি যশো ভুবি ।। দমঃ শমঃ ক্ষমা ধর্মো ধৃতিঃ সত্ত্বং পরাক্রমঃ। পার্থিবানাং গুণো রাজন্ দণ্ডশ্চাপ্যপকারিষু ।। তান্ গুণান্ সম্প্রধার্যাহমগ্র্যং চাভিজনং এব। তারয়া প্রতিষিদ্ধঃ সন্ সুগ্রীবেণ সমাগতঃ ।। ন মামনোন সংরব্ধং প্রমত্তং বেদ্ধুমর্হসি। ইতি তে বুদ্ধিরুৎপন্না বভূবাদর্শনে তব ।। স ত্বং বিনিহতাত্মানং ধর্মধ্বজমধার্মিকম্। জানে পাপসমাচারং তৃণৈঃ কৃপামবাবৃতম্ ।। সত্যং বেশধরং পাপং প্রচ্ছন্নমিব পাবকম্। নাহং ত্বামভিজানামি ধর্মচ্ছদ্মাভিসংবৃতম্ ।। (বাল্মীকি রামায়ণ ৪। ১৭। ১৭-২৩) অর্থাৎ, পৃথিবীর সকল লোকেই বলে যে রাম মহাকুলজাত বীর্যবান তেজস্বী, ব্রতচারী, করুণাশীল, প্রজাহিতে রত, অনুকম্পাপরায়ন, উৎসাহশীল, কালাকালজ্ঞ এবং অধ্যবসায়ী। দম, শম, ক্ষমা, ধর্ম, বীর্য, পরাক্রম, দণ্ডবিধান – এইসব রাজোচিত গুণ ও শ্রেষ্ঠ আভিজাত্য তোমার আছে এই ধারণায় আমি তারার নিষেধ না শুনে সুগ্রীবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলাম। তোমাকে দেখার পূর্বে ভেবেছিলাম, আমি অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত আছি, এই অসতর্ক অবস্থায় রাম আমাকে মারবেন না। এখন জানলাম, তুমি দুরাত্মা, ধর্মধ্বজী অধার্মিক, তৃণাবৃত কূপ ও প্রচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় সাধুবেশী পাপাচারী। তোমার ধর্মের কপট আবরণ আমি বুঝতে পারি নি। হত্বা বাণেন কাকুংস্থ মামিহানপরাধিনম্। কিং বক্ষ্যসি সত্যং মধ্যে কর্ম কৃত্বা জুগুপ্সিতম্ ।। (বাল্মিকী রামায়ণ ৪। ১৭। ৩৫) – কাকুংস্থ, বিনা অপরাধে আমাকে শরাঘাতে বধ করেছো, এই গর্হিত কর্ম করে সাধুসমাজে তুমি কি বলবে? তারপর বালী আরও বললেন, আমার চর্ম, লোম, অস্থি কিছুই তোমার ন্যায় ধার্মিকের কাজে লাগবে না। আমি পঞ্চনখ হলেও আমার মাংস অভক্ষ্য। তুমি আমাকে বৃথাই বধ করেছো। সর্বজ্ঞা তারার হিতবাক্য না শুনে আমি আজ কালের কবলে পড়েছি। সুগ্রীবের হিতকামনায় আমায় মেরেছো, কিন্তু যদি সাহায্যের জন্য আমার কাছে আস্তে,আমি একদিনেই রাবণকে হত্যা করে সীতামাতাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু এভাবে লুকিয়ে থেকে পেছন থেকে শরাঘাত করে অধর্মত আমায় বধ করা কি তোমার উচিত হয়েছে? তুমি একটু ভেবে উত্তর দাও। বালীর মুখ থেকে এ হেন কঠোর বাক্য শ্রবণ করে রামচন্দ্র বালীকে বললেন, ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রকৃত জ্ঞান ব্যতিরেকে অজ্ঞানতাবশত তুমি কেন আমায় দোষারোপ করছো? এই শৈলকাননসমন্বিত দেশ ইক্ষ্বাকুর অধিকৃত, ধর্মাত্মা ভরত এর শাসনকর্তা। আমি এবং অন্য রাজারা ধর্মের প্রসারার্থে তাঁর আদেশে পৃথিবীর সর্বত্র বিচরণ করছি। আমরা প্রত্যেকে ধর্ম ও ন্যায় রক্ষার্থে নিয়োজিত এবং যে বা যারা ধর্মপথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে তাদের শাস্তি প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। তুমি কামপরায়ণ, রাজধর্ম পালন কর না, তোমার বিগর্হিত কর্মে ধর্ম পীড়িত হয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য, মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ভগবানরূপে প্রতিষ্ঠিত না করে তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরতের একজন সেবকরূপে নিজেকে উপস্থাপন করলেন। তিনি বললেন, তদেতৎ কারণং পশ্য যদর্থং ত্বং ময়া হতঃ। ভ্রাতুর্বর্তসি ভার্যায়াং ত্যক্ত্বা ধর্মং সনাতনম্ ।। অস্য ত্বং ধরমাণস্য সুগ্রীবস্য মহাত্মনঃ। রুমায়াং বর্তসে কামাৎ স্নুষায়াং পাপকর্মকৃৎ ।। তদ্ ব্যতীতস্য তে ধর্মাৎ কামবৃত্তস্য বানর। ভ্রাতৃভার্যাভিমর্শেহস্মিন্ দণ্ডোঽয়ং প্রতিপাদিতঃ ।। (বাল্মিকী রামায়ণ ৪। ১৮। ১৮-২০) – কেন তোমাকে বধ করছি তার কারণ শোনো। তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করেছো। তুমি পাপাচারী, মহাত্মা সুগ্রীব জীবিত আছেন। তাঁর পত্নী রুমা তোমার পুত্রবধূস্থানীয়া, কামবশে তুমি তাঁকে অধিকার করেছো। বানর, তুমি ধর্মহীন, কামাসক্ত, ভ্রাতৃবধূকে ধর্ষণ করেছো। এইজন্য এই দণ্ডবিধান তোমার পক্ষে বিহিত। রামচন্দ্র আরও বললেন, সুগ্রীব আমার সখা। তাঁর পত্নী ও রাজ্য উদ্ধারের নিমিত্ত আমি প্রতিজ্ঞা করেছি। কী করে আমার বচন আমি ভঙ্গ করতে পারি? [ যদিও বালী এক দিনের মধ্যে সীতামাতাকে উদ্ধার করতে পারতেন এবং রাবণকে বধ করতে পারতেন, ভগবান সেই পথ চয়ন করেন নি কারণ তা ছিল ধর্মবিরুদ্ধ। ধর্মপথ অনুসরণ করে তিনি দীর্ঘসময় অপেক্ষা করে উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষায় ছিলেন। ] ভগবান বললেন, “ তোমাকে আমি ক্রোধবশত বধ করি নি, বধ করে আমার মনস্তাপও হয় নি। তোমায় বধ করার অন্য একটি কারণ শ্রবণ করো। লোকে ফাঁদ, জাল বা পাশ বিছিয়ে অথবা অন্য কোনও উপায়ে মৃগ ধরে থাকে। মৃগ নিশ্চিন্ত বা ত্রস্ত, সতর্ক বা অসতর্ক যেমনই থাকুক
গৌড়ীয় দর্শনে বেদ~পর্ব:১
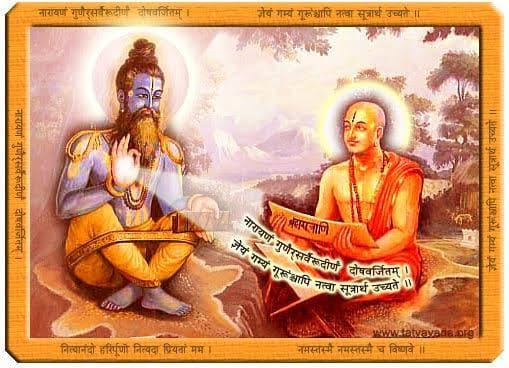
আমাদের এই পেজের উদ্দেশ্য বহুবিধ। তন্মধ্যে অন্যতম, অপসিদ্ধান্তের প্রচারকে সদর্থক ভঙ্গিতে খন্ডন করার পাশাপাশি সৎসিদ্ধান্তের প্রচার। তাই দুষ্টাত্মাদের জবাব ইতিমধ্যেই দেওয়া শুরু হয়েছে এবং আচার্যকৃপা সাপেক্ষে ক্রমশ চলতেও থাকবে। এর পাশাপাশি প্রকৃত রূপানুগ ভক্তিসিদ্ধান্তের যথাযথ প্রচারের চেষ্টা করব আমরা। আমরা ঠিক করেছি কয়েকটি পর্বে “গৌড়ীয় দর্শনে বেদ” এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হবে। আপনারা, অদোষদর্শী বৈষ্ণবগণ, তাই ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমা করবেন। ******************************************** ।।গৌড়ীয় দর্শনে বেদ।। (পর্ব ১) =================================== “তা বাং বাস্তূন্যুশ্মসি গমধ্যে যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ। অত্রাহ তদুরুগায়স্য বিষ্ণো পরমং পদমবভাতি ভূরি।।” (ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১৫৪ সূক্ত, মন্ত্র ৬) – “তোমাদের উভয়ের (রাধাকৃষ্ণ যুগলের) গৃহসমূহে স্থান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করি যেসব গৃহে সুন্দর সুন্দর গাভী সর্বপ্রকার সুখ প্রদান করে, সেই ধামে প্রচুর কীর্তিশালী সর্বকামনা বর্ষণশীল শ্রীকৃষ্ণের নিজধাম (নন্দগৃহ) বহুভাবে সর্বদা নিত্য প্রকাশিত।” ( শ্রীমদ্ভাগবতমের ১০|৮৭|১৮ শ্লোকের “বৃহদ্বৈষ্ণব তোষণী” টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃত ব্যাখ্যার বঙ্গানুবাদ) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: বেদের গৌড়ীয় দর্শন বা শ্রীমন্মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদতত্ত্বের বিষয়ে আলোকপাত করার পূর্বে বেদ কি বা বেদের সংজ্ঞা কি সেই বিষয়ে কিছু প্রাথমিক এবং আবশ্যিক জ্ঞানের প্রয়োজন মানি। সেই হেতু প্রথম পর্বে বেদের সংজ্ঞা এবং বিভাগ সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করব। বেদের সংজ্ঞা এবং ইতিবৃত্ত : “বেদ” শব্দটির উদ্ভব হয়েছে “বিদ্” ধাতু থেকে। সাধারণত “বিদ্” ধাতুর অর্থ “জানা বা অনুভব করা”। “বেদয়তি ধর্ম্মং ব্রহ্ম চ বেদঃ” -অর্থাৎ যে শাস্ত্র হতে ধৰ্ম্ম ও ব্রহ্মতত্ত্বকে জানতে পারি, তাকেই “বেদ” বলে। শ্রীল জীব গোস্বামীর বর্ণনায় পাই : “যশ্চানাদিত্বাৎ স্বয়মেব সিদ্ধঃ, স এব নিখিলৈতিহ্যমূলরূপো মহাবাক্য সমুদায়ঃ শব্দহত্র গৃহ্যতে, স চ শাস্ত্রমেব, তচ্চ বেদ এব – স বেদসিদ্ধঃ, য এব সর্ব্বকারণস্য ভগর্বতোনাদিসিদ্ধং পুনঃ সৃষ্ঠ্যাদৌ তস্মাদেবাবিভুর্তমপৌরষেয়ং বাক্যম, তদেব ভ্রমাদি-রহিতং সম্ভাবীতং, তচ্চ সর্ব্বজনকস্য তস্য চ সদোপদেশায়াবশ্যকং মন্তব্যং, তদেব চাব্যভিচারিপ্রমাণম। “ অর্থাৎ- যা অনাদি ও স্বয়ংসিদ্ধ, নিখিল ঐতিহ্য, প্রমাণ মূলরূপ সেই মহা বাক্য সমুদায়ই এখানে “শব্দ”রূপে গৃহীত হয়েছে। এই শব্দই শাস্ত্র নামে প্রচারিত এবং একেই “বেদ” বলে। “বেদ” হল অনাদিসিদ্ধ এবং জগৎ সৃষ্টির সময় পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণ হইতে বারংবার আবির্ভূত অপৌরুষেয় বাক্যসমুদায়। ভগবান শ্রী কৃষ্ণের পুরুষাবতার শ্রীমন্নারায়ণের শ্বাস থেকে বেদ প্রকাশিত হয় তাই এটি অপৌরুষেয়। যেহেতু বেদ প্রত্যক্ষভাবে শ্রীভগবান হতে প্রকাশিত এবং সেই সময়ের অত্যন্ত মেধাবী সাধুগণ এই জ্ঞান বছরের পর বছর তাঁদের হৃদয়ে যথাযথভাবে ধরে রাখতে পারতেন, সেহেতু এই অপৌরুষেয় বেদকে লিপিবদ্ধ করার কোন প্রয়োজন ছিলনা। কিন্তু দ্বাপরের শেষভাগে মনুষ্যের মেধাশক্তি হ্রাস পেতে থাকে; ফলে এই দিব্য জ্ঞানগঙ্গা যা সৃষ্টির শুরু থেকে তখনও পর্যন্ত সাধুজনের হৃদয়ের মাধ্যমে প্রবাহিত হত- সেই প্রবাহমানতায় ছেদ পড়ে। এছাড়াও আগতপ্রায় অধর্ম এবং স্বল্প মেধার যুগ কলি তখন শক্তি সংগ্রহ করে তার করাল গ্রাসে সসাগরা মেদিনী আগ্রাসনে মত্ত। এইসমস্ত বিষয় বিবেচনা করে ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস অপৌরুষেয় শাস্ত্রাবতার বেদকে “ঋক, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব” এই চারটি ভাগে বিভক্ত করেন এবং ভবিষ্যত স্বল্প মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য তা লিপিবদ্ধ করলেন। পরমব্রহ্মের শব্দময় শাস্ত্রাবতারই হলো বেদ। সাধারণত বেদের শ্লোক ছন্দময়। এইরকম ছন্দময় শ্লোককে বেদে “মন্ত্র” বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং মন্ত্রের সমষ্টিকে “সূক্ত” বলা হয়। বেদের বিভাগ : এই অপৌরুষেয় শব্দবতার বেদ চারভাগে বিভক্ত। ১) সংহিতা : সূক্তের সমষ্টি বেদে “সংহিতা” নামে পরিচিত। ২) ব্রাহ্মণ : এই অংশে বিভিন্ন যজ্ঞের মন্ত্র এবং নিয়মাদি উল্লিখিত। ৩) আরণ্যক : চতুরাশ্রমের অন্যতম বানপ্রস্থাশ্রমে ব্রহ্ম চিন্তার বিষয়াদি এখানে বর্ণিত। ৪) উপনিষদ : এটি বেদের শেষ অংশ এবং “বেদান্ত” নামে পরিচিত। বেদের শেষ বা অন্তিম বা অন্ত অংশ এবং সম্পূর্ণ বেদের চরম ও পরম সিদ্ধান্ত এই অংশেই উপলব্ধ হয় তাই উপনিষদকে “বেদান্ত” বলা হয়েছে। “উপনিষদ” শব্দের অর্থ হলো : “ব্রাহ্মণ উপ সমীপে নিষিদতি অনয়া ইত্যুপনিষদ” -অর্থাৎ যে শাস্ত্রের সাহায্যে সাধক মুক্ত হয়ে ভগবানের সমীপে উপস্থিত হোতে সমর্থ হন সেটিই উপনিষদ। “বেদান্ত সূত্র” : ভগবান ব্যাসদেব উপনিষদ বা বেদান্তের জটিল তাৎপর্য গুলি সূত্রাকারে সুসংবদ্ধভাবে গুম্ফিত করেন। এটিই “বেদান্ত সূত্র” বা “ব্রহ্ম সূত্র” নামে পরিচিত। অর্থাৎ শ্রীল ব্যাসদেব শ্রুতি শাস্ত্রের চরম তাৎপর্য সূত্রাকারে উপস্থাপন করলেন বলে এটি “বেদান্ত সূত্র”। আবার বেদের সমস্ত মীমাংসা এই সূত্রের মধ্যে পাওয়া যায় বলে এটিকে “উত্তরমীমাংসা” বা “মীমাংসাশাস্ত্র” বলেও অভিহিত করা হয়। বেদান্ত সূত্রের রচনার পর ভগবান ব্যাসদেব অনুধাবন করেন যে, এই “বেদান্ত সূত্র” তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করার পক্ষে যথেষ্ট প্রামানিক শাস্ত্র হলেও সূত্রার্থ নির্ণয় বিষম দুরূহ, এছাড়াও পরবর্তীকালে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজ নিজ মতে ব্রহ্মসূত্রের মনগড়া ব্যাখ্যা করতে পারে। শ্রীল ব্যাসদেব এই সমস্যার সমাধানার্থে নিজ গুরুদেব শ্রীল নারদ মুনির শরণাপন্ন হন এবং সমাধিস্থ অবস্থায় তত্ত্ব দর্শনপূর্বক বেদান্ত/ব্রহ্ম সূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য “শ্রীমদ্ভাগবতম্” রচনা করেন। চিত্রে : “বদরিকাশ্রমে ভগবান ব্যাস শ্রীমধ্বকে বেদান্তশিক্ষা দিচ্ছেন” (চলবে…….)
গৌড়ীয় দর্শনে বেদ~পর্ব:২
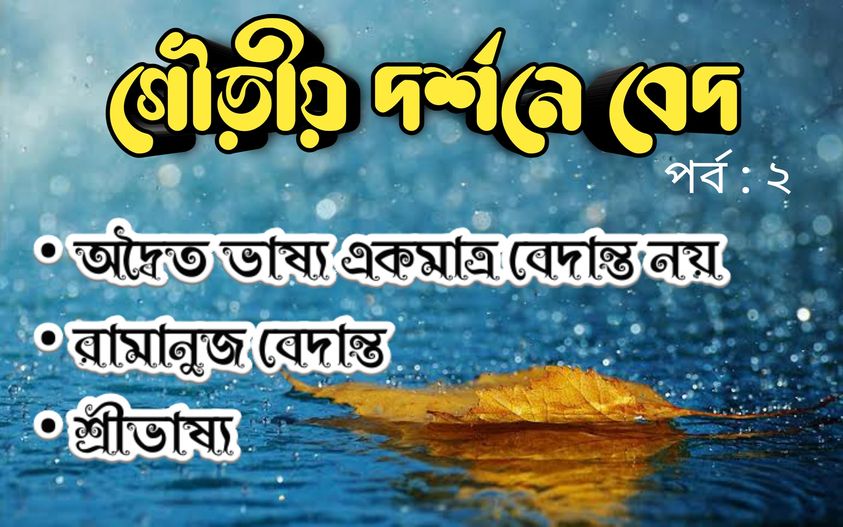
প্রভু কহে, বেদান্তসূত্র – ঈশ্বর বচন। ব্যাসরূপে কৈল তাহা শ্রীনারায়ণ।। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব। ঈশ্বরের বাক্যে নাহি দোষ এই সব।। (চৈ: চ: আদি) ************************** পূর্ববর্তী পর্বে আমরা বেদ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। সেখানে বেদান্ত সূত্র সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা হয়েছিল, আজকের পর্বে আমরা বেদান্ত সূত্রের প্রসঙ্গ ধরেই চার সুবৃহৎ বৈষ্ণব মহাসম্প্রদায়ের বেদান্ত ভাষ্য এবং অদ্বৈত মায়াবাদী ভাষ্য সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা করব। বেদান্ত সূত্রে অর্থবাদ আরোপিত হতে পারে ভেবে শ্রীল কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস নিজ গুরুদেবের নির্দেশে সমাধিস্থ অবস্থায় ব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম এবং যথাযথ ভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তদনুগত গোস্বামীগণও শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তের যথার্থ ভাষ্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত, বর্তমানে বেদান্ত সূত্র বা বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য বলতে অনেকেই উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে শ্রীল শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদী “শারীরক ভাষ্যকেই” বোঝেন। তাঁরা এটা জানেন না যে আচার্য শঙ্করের বহু আগেই রুদ্র সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীল বিষ্ণুস্বামী বেদান্ত ভাষ্য রচনা করেন। শঙ্করোত্তর সময়ে যথাক্রমে শ্রী, মাধ্ব এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্যগণ পৃথক পৃথক দ্বৈতবাদী দর্শন দ্বারা ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন এবং শঙ্করের অদ্বৈতবাদ পুনঃ পুনঃ খন্ডন করেছেন। • পদ্মপুরাণে উল্লিখিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদী “বেদান্ত দর্শন”: • বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (শ্রী সম্প্রদায়): শ্রী সম্প্রদায় আচার্য শেষাবতার শ্রীল রামানুজাচার্য বেদান্ত সূত্রের যে ভাষ্য রচনা করেন সেটি “শ্রীভাষ্য” নামে খ্যাত। তাঁর দর্শন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। এই মতানুসারে পরম ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্বীকার করা হয়েছে- পরব্রহ্ম এক। “চিদচিদবিশিষ্টাদ্বৈতং তত্ত্বম্” অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ ব্রহ্মের একত্বই বিশিষ্ট অদ্বৈত তত্ত্বের প্রতিপাদ্য। তাঁর মতে এই অদ্বয় ব্রহ্ম বিশেষ বিশেষণযুক্ত বা বিশিষ্ট। চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর এই তিনটি তত্ত্ব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ দর্শনে উল্ল্যেখ করা হয়েছে। “চিৎ” শব্দে জীবাত্মাকে বোঝানো হয়েছে, অচিৎ শব্দে “জড়” এবং “ঈশ্বর” শব্দে চিৎ ও অচিৎ তত্ত্বের পরম নিয়ন্ত্রক পরম পুরুষোত্তম শ্রীমন্নারায়ণ। চিৎ ও অচিৎ সগুণ ব্রহ্মের বিশেষণ এবং ঈশ্বর হলেন বিশেষ বা বিশিষ্ট। চিৎ-অচিৎ বিশেষণযুক্ত একাত্ম অদ্বৈত ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে বিশ্লেষণ করার জন্য এই দর্শনকে বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ বলা হয়। পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা বা ঈশ্বর পূর্ণতম, সর্বব্যাপী এবং অখন্ড চেতন কিন্তু জীবাত্মা পরমাত্মার নিত্য অংশ হলেও সেটি খন্ড চেতন। আত্মা এবং পরমাত্মা তত্ত্ব তত্ত্বগতভাবে সমান হলেও আত্মা অণুসদৃশ তাই পরমাত্মার সাথে সেটি কখনোই একত্ব নয়। এই জায়গাতেই শ্রীল রামানুজাচার্যের এই মতবাদের সাথে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অচিন্ত্য ভেদ অভেদ তত্ত্বের মিল পাওয়া যায়। (চলবে…) পর্ব : ১ এর লিঙ্ক https://www.facebook.com/105504134466044/posts/109429214073536/
গৌড়ীয় দর্শনে বেদ~পর্ব-৩
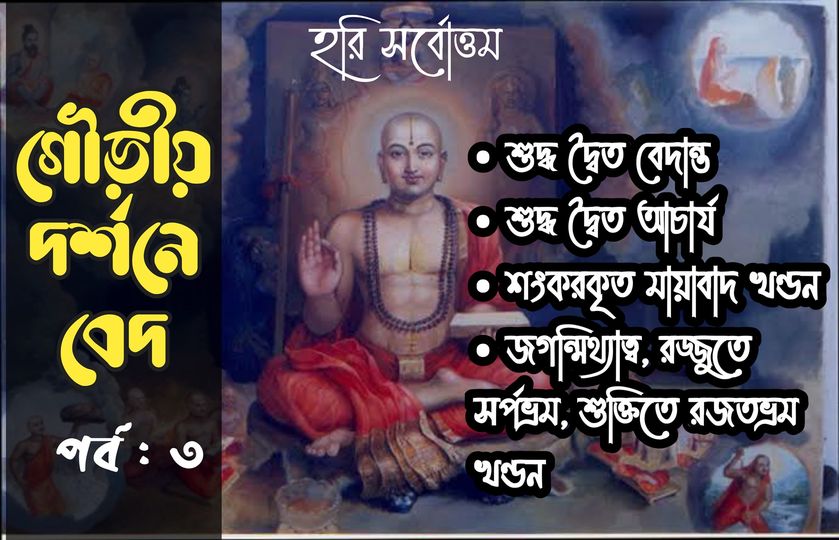
গত পর্বে সংক্ষেপে রামানুজ বেদান্ত আলোচনার পর এই পর্বে মধ্বাচার্যের বেদান্ত মত সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে। শ্রীরামানুজের পূর্বেই বৌধায়ন, দ্রমিড়, টঙ্কাচার্য প্রমুখ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী আচার্য এই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ প্রচার করেছিলেন। সুতরাং এই দর্শন শ্রীল রামানুজাচার্যের পূর্বেও প্রচলিত ছিল। আচার্য রামানুজ ভক্তিকে দার্শনিক ভাবে ব্যাখ্যা করেন। এরপর আসেন শ্রীল মধ্বাচার্য। যিনি আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ নামে ও পরিচিতি পান। • শুদ্ধদ্বৈত বাদ (ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায়): শ্রীব্রহ্মা হতে এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি এবং শ্রীল মধ্বাচার্য তাঁর শুদ্ধ দ্বৈত দর্শনের দ্বারা এই সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য বর্ধন করেছেন। তাই এই সম্প্রদায়কে ব্রহ্ম-মাধ্ব সম্প্রদায় বলা হয়। আচার্য মধ্বের দর্শন হলো শুদ্ধ-দ্বৈতবাদ অর্থাৎ ঈশ্বরে জীবে, জড়ে নিত্য ভেদ বর্তমান। এই সিদ্ধান্ত মতে • পরব্রহ্ম ভগবান শ্রী বিষ্ণুই সর্বোত্তম। • জগৎ সত্য, • ঈশ্বর, জীব এবং জড়ে পঞ্চভেদ নিত্য বর্তমান (ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ, জীবে ও জড়ে ভেদ, জীবে ও জীবে ভেদ, ঈশ্বরে ও জড়ে ভেদ এবং জড়ে ও জড়ে ভেদ বর্তমান ), • জীবসমূহ শ্রীহরির অনুচর, যোগ্যতানুসারে জীবগণের মধ্যে নিত্য তারতম্য বর্তমান। • শুদ্ধা ভক্তিই জীবের স্বরূপানুগত ধর্মের অভিব্যক্তির সাধন অর্থাৎ জীব মাত্রেই বিষ্ণুদাস। এই যুক্তির সাথে গৌড়ীয়নাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উক্তি (জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস) মিল পাওয়া যায়। • আচার্য মধ্ব শাংকরভাষ্য খণ্ডন করেন: শঙ্করের অদ্বৈতবাদ খন্ডন করে শ্রী মধ্ব বলেন: ১) বিষ্ণু/কৃষ্ণই পরম বস্তু, ২) বিষ্ণু/কৃষ্ণ – অখিল বেদবেদ্য, ৩) জগৎ সত্য, ৪) জীব ও জড় “বিষ্ণু বা কৃষ্ণ” হতে ভিন্ন, ৫) জীব মাত্রই ভগবান বিষ্ণুর দাস, ৬) বদ্ধ ও মুক্তভেদে জীবের মধ্যে তারতম্য আছে, ৭) বিষ্ণুপাদপদ্ম লাভই জীবের লক্ষ্য, ৮) জীবের মুক্তির কারণ -বিষ্ণুর শুদ্ধ ভক্তি এবং ৯) প্রত্যক্ষ, অনুমান ও বেদই প্রমাণত্রয়। শ্রী মধ্বের এই নয়টি প্রমেয়ই শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশ করেছেন। • মহাভারত তাৎপর্য নির্ণয়ে ১/১১ শ্লোকের শ্রী মধ্ব বললেন – “নির্দ্দোষপূর্ণগুণবিগ্রহ-আত্মতন্ত্র নিশ্চেতনাত্মকশরীর-গুণৈশ্চ হীনাঃ। আনন্দমাত্রকরপাদমুখোদরাদি: সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদ বিবর্জ্জিতাত্মা।। অর্থাৎ, ভগবান বিষ্ণু সর্ব প্রকার দোষরোহিত, তিনি পরিপূর্ণ চিদগুণাত্মক দেহবান (সচ্চিদানন্দ), সম্পূর্ণ স্বাধীন, তাঁর দেহ বা গুণাবলী সম্পূর্ণ চিন্ময়, তাঁর অবচেতনার লেশমাত্র নেই, তিনি হস্ত-পদ-মুখ-উদরাদি যুক্ত শ্রীবিগ্রহ, সেইসকল আনন্দমাত্রস্বরূপ। তিনি সর্বত্র স্বগতভেদ রোহিত বাস্তব বস্তু। • পবনাবতার শ্রী মধ্ব, শঙ্করের “জগৎ মিথ্যা” যুক্তিকে খন্ডন করে জগতের সত্যতা প্রমান করেন এবং বলেন : ভগবান শ্রীহরি কল্পের আদিতে অনাদি-নিত্যা জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণ (সত্ত, রজ, তম), মহৎ, অহংকার, পঞ্চভূত-ক্রমে ব্রহ্মান্ড, ব্রহ্মান্ড মধ্যে চতুর্দশ লোক, সমুদ্র, মেরুমন্দরাদি পর্বত, গঙ্গা যমুনাদি নদী, শিলা, বনস্পতি, ঔষধি, ধান্য, পুষ্প, ফল, পুষ্প, নবরত্ন, সুবর্ণ, লৌহাদি ধাতু প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সৃষ্টি করেন। এই সবই কার্যরূপে অনিত্য কিন্তু কারণরূপে নিত্য। বিষ্ণুর বুদ্ধিবলে সৃষ্ট জগৎ কখনই তাঁর অধ্যক্ষতা ছাড়া মায়ার উপাদানে তৈরী হতে পারে না। অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট জগৎ সত্য কিন্তু নশ্বর। • উপসংহারে বলা যায়, আচার্য মধ্ব কখনোই জগৎকে মিথ্যা বলেননি। ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্তকারণ কুমোর- তিনটিই সত্য। তেমনি জগৎ সৃষ্টির উপাদান গুলি শ্রীহরি হতেই উৎপন্ন, আবার শ্রীহরিই নিমিত্তকারণ। তাই সত্যবস্তু শ্রীহরি থেকে উৎপন্ন জগৎ কি প্রকারে মিথ্যা হতে পারে। শ্রীহরি এই জগৎসৃষ্টি করেও অবিকারী তত্ত্ব। গীতাতে এ কথা বলা হয়েছে : মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতা।।” (৯|৪) – ভূতসকল আমাতে অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নহি। শংকর জগৎকে রজ্জুতে সর্পভ্রম বা শুক্তিতে রজতভ্রম বলেছেন। মধ্বমতে রজ্জুতে তখনই সর্পভ্রম হবে, যখন প্রকৃত সর্পের বিষয়ে জ্ঞান থাকবে; শুক্তিতে তখনই রজতভ্রম হবে, যখন প্রকৃত রজতের স্মৃতি থাকবে। এইভাবে নিশ্চয়ই একটি শুদ্ধ চিন্ময় জগৎ আছে, যার ফলে জগতে তার ভ্রম হয়। অর্থাৎ, শ্রীভগবানের অবশ্যই চিদ্বৈচিত্র্য আছে। শ্রীল মধ্ব সম্পর্কে আলাদা দুটি পোস্ট পূর্বে করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে পঞ্চভেদ এবং মধ্বাচার্যের লক্ষ্মী ঠাকুরাণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলাদা ভাবে বিস্তৃত বর্ণনা করে পোস্ট দেওয়া হবে। গৌড়ীয় দর্শনে বেদ, প্রথম পর্ব লিঙ্ক https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=109429214073536&id=105504134466044 দ্বিতীয় পর্ব লিঙ্ক https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=121211272895330&id=105504134466044
গৌড়ীয় দর্শনে বেদ~পর্ব-৪
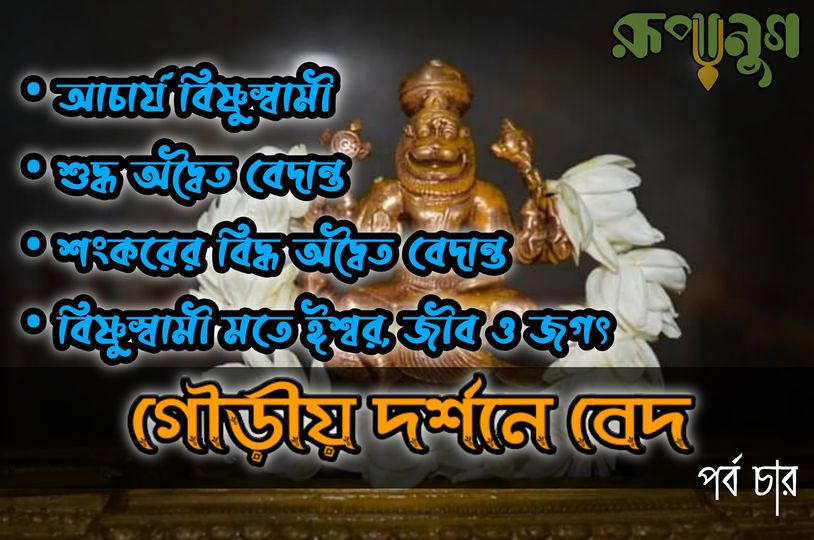
পূর্ববর্তী ৩ টি পর্বে বেদের সংজ্ঞা, বিভাগ, বেদান্ত, বেদান্ত সূত্র এবং শ্রীল রামানুজাচার্য ও শ্রীল মধ্বাচার্যের বেদান্ত দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। এই পর্বে আমরা শ্রীমদ বিষ্ণুস্বামীপাদের শুদ্ধাদ্বৈতবাদের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। ************************************************ “নমঃ শ্রী গান্ধর্বিকা গিরিধরাভ্যাম্ কন্দর্প কোটি রম্যায় স্ফুরদ ইন্দিবর ত্বিষে জগন্মোহনলীলায় নমো গোপেন্দ্র সূনবে।। “ ************* সদ্য প্রস্ফুটিত নীল পদ্মের মত যার রূপ, মদনের রূপের কোটি গুন সুন্দর , যিনি নানান লীলায় জগতবাসী কে মুগ্ধ করেন , সেই গোপকূলরাজ নন্দের পুত্র কে বন্দনা করি। (মুক্তা চরিত ১) (সূত্র -গৌড়ীয় স্ক্রিপচার) ************************************************ শুদ্ধাদ্বৈতবাদ (শ্রীবিষ্ণুস্বামী): বৈষ্ণব শিরোমণি দেবাদিদেব মহাদেব হতে উদ্ভূত রুদ্র সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের আচার্য শ্রীল বিষ্ণুস্বামীপাদ। তাঁর রচিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য “সর্ব্বজ্ঞসূক্তি” এবং এনার বেদান্ত দর্শন শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ নামে পরিচিত। কিছু মূর্খ ব্যক্তি নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য বৈষ্ণবীয় শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে শঙ্করের কেবলাদ্বৈতবাদ মনে করে ভ্রমের শিকার হন। রুদ্র সম্প্রদায়ে পরবর্তী কালে আরও দুই ব্যক্তি বিষ্ণুস্বামী নামে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু এক্ষণে আমরা শ্রীদেবেশ্বর পুত্র দেবতনু আদি বিষ্ণুস্বামীর বেদান্ত দর্শন বিষয়েই আলোচনা করবো। শ্রীল বিষ্ণুস্বামী অদ্বয় জ্ঞান বা শুদ্ধ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত দর্শন প্রচার করেন। শ্রীধর স্বামী, শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে অদ্বৈতবাদী সিদ্ধান্তের বিদ্ধমতবাদ প্রবর্তন করেন শঙ্করাচার্য। ফলে রুদ্র সম্প্রদায়ের আচার্যগণ তাঁদের অদ্বৈতবাদ কে শুদ্ধাদ্বৈত এবং শঙ্করের মায়াচ্ছন্ন বিদ্ধ অদ্বৈতবাদকে কেবলাদ্বৈতবাদ নামে আখ্যায়িত করেন। শ্রীল বিষ্ণুস্বামীপাদের মতে ঈশ্বরের, ভগবানের চিদ শরীরের এবং ভজনকারী ভক্তের শুদ্ধত্ব স্বীকৃত হয়েছে। জীব, মায়া এবং জগত ঈশ্বরের আশ্রয়েই পরিচালিত এবং ঈশ্বর হইতে অভেদ ও সত্য সেটিও স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে জীব, জগৎ ও মায়া পরম বস্তু বা পরম ঈশ্বরের অংশ বিশেষ, কখনোই তারা ঈশ্বর বা পরমব্রহ্ম নয়। অর্থাৎ পরম তত্ত্ব এবং তাঁর অংশ তত্ত্বগতভাবে বা উপাদানগত ভাবে অদ্বয় হলেও পরিমাণগত ভাবে ভিন্ন। জীব, জগৎ এবং মায়া ঈশ্বরের নিত্য অংশ বিশেষ। এখানেও ভগবান চৈতন্যের অচিন্ত্য ভেদ-অভেদ তত্ত্বের মিল পাওয়া গেলো। শঙ্করের জগৎ মিথ্যা এবং ব্রহ্ম মায়ার প্রভাবে জীব হন এই উক্তি গুলিও এখানে খণ্ডিত হলো। জগৎ: এই বিষয়ে শ্রীল আচার্য বললেন “জগৎ হলো পরম বস্তু বা পরমব্রহ্মের কার্য্য। সোনা যেরকম কণ্ঠহার, কুন্ডল ইত্যাদিতে পরিণত হলেও সোনাই থাকে সেইরকমভাবেই সর্বকারণকারণম্ ঈশ্বর যখন সত্য তখন তদ্দ্বারা নির্মিত কার্যরূপ জগৎ সত্য ও নিত্য। এখানে প্রশ্ন আসতে পারে কালের প্রভাবে জগতে প্রলয় আসে এবং জগৎ বিলুপ্ত হয় তবে জগতের নিত্যত্ব কিরূপে প্রমাণিত হয়? শ্রীল বিষ্ণুস্বামীপাদ এর উত্তরে বলছেন -“কোনো বস্তুর তৎকালীন অদর্শনের দ্বারা বস্তুর নিত্যত্ব বা অনিত্যত্ব বিচার করতে পারিনা। যেমন মেঘ সূর্য্য কে ঢেকে দিলেও সূর্য্য হারিয়ে যায়না, সুতরাং এই অদর্শন তাৎক্ষণিক। অতি ক্ষুদ্র অণু পরমাণু আমাদের দৃষ্টিগোচর নয় বলে তাহা বিদ্যমান নয় সেটি আমরা বলতে পারিনা বা গৃহাভ্যন্তরে স্থিত রাজমহিষীর অদর্শনে আমরা তার অবিদ্যমানতার সিদ্ধান্তে উপনীত হোতে পারিনা বা লবনাক্ত জলে লবণের অদর্শনে আমরা লবণের উপস্থিতি অস্বীকার করতে পারিনা সেরকমই জগৎ তাৎক্ষনিকভাবে অদৃশ্যমান হলেও তাহার নিত্যত্ব বর্তমান থাকে। আবার আমরা ব্যক্তিগত ভাবে এটাও বলতে পারি রক্তে লোহার অদর্শনে আমরা রক্তে হিমোগ্লোবিনের নিত্যত্ব অস্বীকার করতে পারিনা। অন্ধের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অবিদ্যমান মনে করা যা জগৎ মিথ্যা মনে করাও তাই। ঈশ্বর: এই বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে আচার্য বিষ্ণুস্বামীপাদ বললেন – “হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্ঠ: সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর:। স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীব: সংক্লেশনিকরাকর:।। তথা__স ঈশো যদ্বশে মায়া স জীব যস্তয়ার্দ্দিত:। স্বাবির্ভুত: পরানন্দ: স্বাবির্ভূত: সুদু:খভূ:।। “ অর্থাৎ, হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি আলিঙ্গিত সচ্চিদানন্দ বিগ্রহই ঈশ্বর। অবিদ্যা সংবৃতত্ব ও সংক্লেশ ইত্যাদির মূল স্বরূপতাই বদ্ধ জীবের লক্ষণ। বিভু ঈশ্বরের সহিত অংশস্বরূপ জীবের যে সেব্য ও সেবক বা প্রভু ও ভৃত্যের অবস্থানরূপ একত্বাবস্থা সেই শুদ্ধজ্ঞান থেকে বিচ্যুত এবং উপাধিবশত ঈশ্বর এবং জড়ের ভেদগত সত্তা দর্শনে নিজেকে অবিদ্যার দ্বারা আবৃত ও সংক্লেশের মূল স্বরূপ জ্ঞানই বদ্ধ জীবাভিমান। উল্লেখ্য, বর্তমানে কিছু মূঢ় ব্যক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঈশ্বর এবং তটস্থা জীবের যে প্রভু এবং ভৃত্যের সম্পর্ক সেই বিষয়ে অশাস্ত্রীয় বালক সুলভ মন্তব্য করে থাকেন কিন্তু বহুকাল পূর্বেই বৈষ্ণবাচার্য শ্রীল বিষ্ণুস্বামীর সিদ্ধান্তেও যে উক্ত প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে সেটি তারা মায়াপহৃত জ্ঞানের কারণে বুঝতে সক্ষম হন না। আচার্যদেব বিষ্ণুস্বামীর মতে ঈশ্বর মায়াধীশ, স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ, তিনি নিত্য মুক্ত (এক্ষেত্রে শঙ্করের ব্রহ্ম মায়াবদ্ধ তত্ত্ব খণ্ডিত হলো), ঈশ্বর কোনো উপাধির বশ্যতা প্রাপ্ত হননা, তিনি অপ্রাকৃত গুণ বিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান, সর্ব্বেশ্বর (উল্ল্যেখ্য শঙ্কর মতে ব্রহ্ম শক্তিহীন), সর্ব নিয়ন্তা, সর্ব্বোপাস্য, সর্ব্বকর্মফল প্রদাতা এবং সচ্চিদানন্দ পরমবস্তু। আচার্য বিষ্ণুস্বামী প্রবর্তিত মতবাদ যদিও অদ্বৈত কিন্তু এখানে তিনি ঈশ্বরের সচ্চিদানন্দ সাকার ঈশ্বরের কথাই বললেন, তিনি অদ্বৈত মতবাদ প্রচার করলেও ঈশ্বরের নিরাকারত্ব স্বীকার করেননি। তাঁর মতে জীব সেই পরম সচ্চিদানন্দ পরমবস্তুর অংশ বিশেষ কিন্তু কখনোই পরমবস্তুর সাথে এক নয় অর্থাৎ ঈশ্বর এবং জীবের ভেদ নিত্য। জীব: এই বিষয়ে আচার্য বিষ্ণুস্বামী বলেন জীব পরমবস্তুর অংশ বিশেষ এবং ব্রহ্ম সূত্রের থেকেই তিনি প্রমান দিলেন এইভাবে – “অংশ নানা ব্যপদেশাৎ” (ব্রহ্ম সূত্র -২/৩/৪২) ব্যাখ্যা : বেদে কোথাও জীবকে ব্রহ্ম, কোথাও অজ্ঞ, কোথাও চিদরূপ, কোথাও দাস আবার কোথাও অণু বলা হয়েছে। এই ভাবে জীবতত্ত্বকে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে সম্বোধনের ফলে প্রমান হচ্ছে যে জীব ব্রহ্মের অংশ স্বয়ং ব্রহ্ম নয়। এছাড়াও ব্রহ্ম সূত্রের আরও কিছু সূত্রে জীব ব্রহ্মের অংশ বিশেষ এই তত্ত্বই বর্ণিত হয়েছে যেমন “মন্ত্রবর্ণাৎ”-সূত্র ২/৩/৪৩, “অপি স্মর্য্যতে”-সূত্র ২/৩/৪৪, “প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পর:”-সূত্র ২/৩/৪৫ ইত্যাদি। যেভাবে অগ্নি হোতে নির্গত অগ্নি স্ফুলিঙ্গও অগ্নি নামেই পরিচিত কিন্তু অগ্নিসম নয় সেইরূপ জীব ও ব্রহ্ম অংশ ও অংশী হলেও দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান তাই জীব কখনও পরমব্রহ্ম নয়। আর এই ভেদ এবং অভেদ তত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত। বাকি সমস্ত আচার্যদের সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণতা পায় একমাত্র “অচিন্ত্য ভেদ-অভেদ” তত্ত্ব এসে। উল্লেখ যোগ্য বিষয় এই যে, কিছু ব্যক্তি বলে থাকেন, অদ্বৈতবাদের প্রবর্তক শ্রীল শঙ্করাচার্য। কিন্তু অজ্ঞানতাবশত তাঁরা জানেননা যে খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০ বছর আগে এবং আদি শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই রুদ্র সম্প্রদায় আচার্য শ্রীল বিষ্ণুস্বামীপাদ অদ্বৈত দর্শনের শুদ্ধ মতবাদ প্রবর্তন করেছিলেন। শঙ্করের বহু পূর্ব থেকেই ছয়টি বৈষ্ণব সম্প্রদায় বর্তমান ছিল। বহু পরে আচার্য শঙ্কর এসে অদ্বৈত দর্শনের বিদ্ধ মতবাদ প্রচার করেন। অর্থাৎ শুদ্ধ-অদ্বৈতবাদের বিকৃত রূপ হলো প্রচলিত কেবলাদ্বৈতবাদ। সঠিক জ্ঞানের অভাবে মূর্খেরাই অদ্বৈতবাদ বলতে কেবলাদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ বা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ মতবাদকেই বোঝেন। শ্রীল বিষ্ণুস্বামী এবং তাঁর শুদ্ধ-অদ্বৈত দর্শন সংক্রান্ত একটি পৃথক বিশদ প্রবন্ধ শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। “গৌড়ীয় দর্শনে বেদ” সিরিজের পর্ব ৫ -এ নিম্বার্ক সম্প্রদায় এবং তার বেদান্ত দর্শন নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রতিটি প্রবন্ধ বা পোস্ট মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং শেয়ার করে সৎ দর্শন প্রচারে আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করুন। পাশে থাকুন। গৌর প্রেমানন্দে হরি হরিবোল। @RUPANUGA
অযোধ্যায় শ্রীরাম বিগ্রহ নাকি ভাষ্কর্য?!?
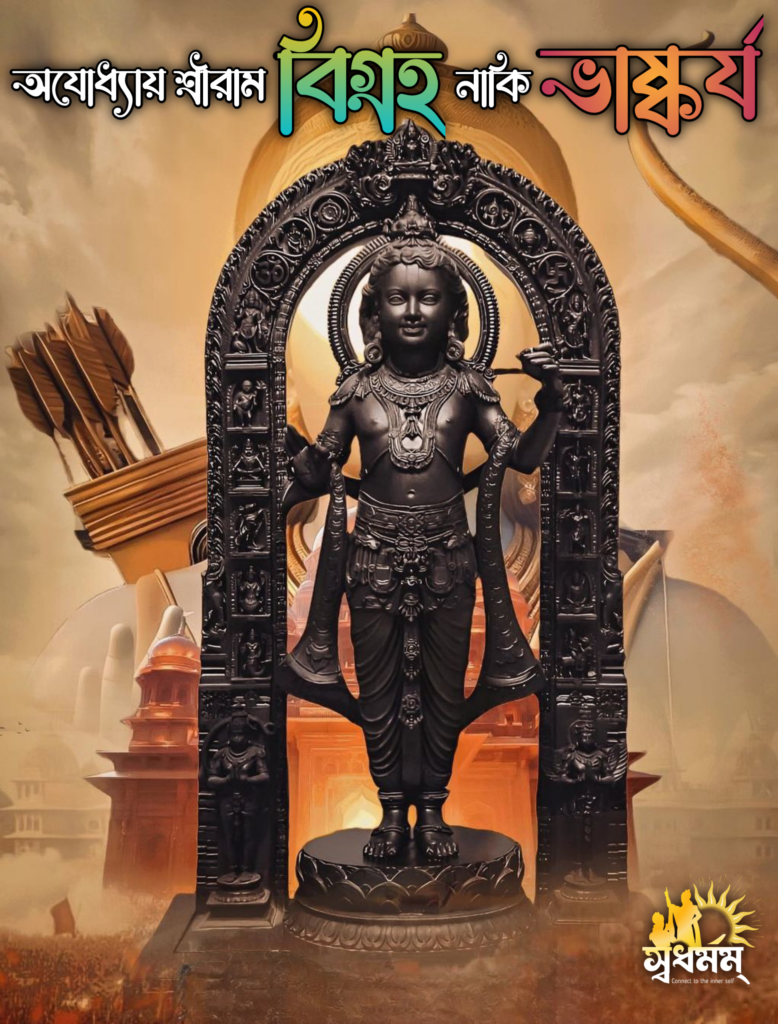
মর্যাদা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামের বিগ্রহকে ভাষ্কর্য বলার দুঃসাহস করছে একদল তথাকথিত বেদবাদী পণ্ডিত!!! যারা দীর্ঘদিন থেকেই বেদের নাম করে কিছু মনগড়া ভাষ্যে দেখিয়ে সহজ সরলমনা সনাতনীদের মাথায় নিরাকারবাদ, নাস্তিক্যবাদ ঢুকিয়ে তাদের ধর্মবিমুখ করার পায়তারা করছে। যদিও এরা প্রকাশ্যে শ্রীরামবিগ্রহের ছবি পোস্ট করে, দূর্গা পূজায় শুভেচ্ছামূলক পোস্ট দিয়ে, জন্মাষ্টমীতে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে জনসমর্থন কুঁড়ায় কিন্তু আড়ালে সুকৌশলে ঠিকই তাদের নাস্তিক্য দর্শন প্রচার করে। এরই ধারাবাহিকতায় অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামের বিগ্রহকে সাধারণ ভাষ্কর্যের সঙ্গে তুলনা করে তাচ্ছিল্যভরে নানা ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট করতেও দ্বিধাবোধ করেনি তারা। অথচ বেদাদি শাস্ত্রে শ্রীবিগ্রহ আরাধনার যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও এরা কিভাবে যে সাধারণ জনগণের চোখে ধুলা দেয় বোধগম্য নয়। “আমি দেবলোকের উদ্দেশ্যে প্রতিমা তৈরি কারী শিল্পীকে নিযুক্ত করছি।“ (যজুর্বেদ: ৩০/১২) তাঁর মূর্তি কিভাবে সম্পন্ন বা নির্মান হবে, তার নির্দেশনা- “পাষাণ, মৃত্তিকা, পাহাড়-পর্বত বালুক বনস্পতি, স্বর্ণ, রৌপ্য লৌহ, তামা সীসা দ্বারা আমার যজ্ঞ সম্পন্ন হউক ।“ (যজুর্বেদ: ১৮/১৩) সেই স্থানে তিঁনি অবস্থানও করেন- হে শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি অনন্তস্বরূপ, ভগবানের শরীর সদৃশ, ভগবত সম্বন্ধযুক্ত স্থানে উপবেশন করো ।’’ (যজুর্বেদ: ৫/৩০) रू॒पंरू॑पं॒ प्रति॑रूपो बभूव॒ तद॑स्य रू॒पं प्र॑ति॒चक्ष॑णाय। इन्द्रो॑ मा॒याभि॑: पुरु॒रूप॑ ईयते यु॒क्ता ह्य॑स्य॒ हर॑यः श॒ता दश॑॥ “রুপং রুপং প্রতিরুপো বভূব তদস্য রুপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরুপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ।।” অনুবাদঃ ঈশ্বর (ইন্দ্র), বিভিন্ন রুপ বা দেহ ধারন করেন। এবং সে রুপ ধারন করে তিনি পৃথকভাবে প্রকাশিত হন।তিনি তার মায়া দ্বারা বিবিধ রুপ ধারন করে যজমানগণের নিকট উপস্থিত হন।কারন তার রথ সহস্র অশ্ব সংযুক্ত(অনন্ত শক্তি), অথাৎ তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। – ঋগ্বেদ ৬/৪৭/১৮ नू मर्तो॑ दयते सनि॒ष्यन्यो विष्ण॑व उरुगा॒याय॒ दाश॑त्। प्र यः स॒त्राचा॒ मन॑सा॒ यजा॑त ए॒ताव॑न्तं॒ नर्य॑मा॒विवा॑सात्॥ nū marto dayate saniṣyan yo viṣṇava urugāyāya dāśat| pra yaḥ satrācā manasā yajāta etāvantaṃ naryam āvivāsāt|| “যিনি বহু লোকের কীর্তনীয় বিষ্ণুকে হব্য দান করেন,যিনি যুগপৎ উচ্চারিত স্তোত্রের দ্বারা তাকে পূজা করেন এবং মনুষ্যের হিতকর বিষ্ণুর পরিচর্যা করেন সে মর্ত্যধন ইচ্ছা করে শীঘ্রই প্রাপ্ত হন।” – (ঋকবেদঃ ৭/১০০/১) अर्च॑त॒ प्रार्च॑त॒ प्रिय॑मेधासो॒ अर्च॑त। अर्च॑न्तु पुत्र॒का उ॒त पुरं॒ न धृ॒ष्ण्व॑र्चत॥ arcata prārcata priyamedhāso arcata| arcantu putrakā uta puraṃ na dhṛṣṇv arcata|| “হে প্রিয়মেধগণ! তোমরা ইন্দ্রক অর্চনা কর। বিশেষরূপে অর্চনা কর, পুত্রগণ পুরবিদারীকে যেরূপ অর্চনা করে, সেরূপ ইন্দ্রের অর্চনা করুক।” – [ঋগবেদ:- ৮/৬৯/৮] যদি বিগ্রহ বা শ্রীমূর্তি পূজা বেদবিহিত না হত,তাহলে এ মন্ত্রে পূজা,পরিচর্যার প্রসঙ্গই আসতো না। যজুর্বেদের ১৩/৪১ নং মন্ত্রে বলা আছে, “সহসস্র প্রতিমাং বিশ্বরূপম।’’ অর্থাৎ, ঈশ্বর সহস্র রূপে বিশ্বজুড়ে আছেন । “তং যজ্ঞম্বর্হিষিপ্রৌক্ষংন্ন…..সাধ্যাঋষ্যশ্চ য়ে (যজুর্বেদ৩১/৯) এর নিরুক্ত শতপথ ১১/১/৩ দেখলে তার অর্থ এমন দাঁড়াবে যে- “সাধ্য দেবগণ এবং সনকাদি ঋষিগণ সৃষ্টির পূর্বে উৎপন্ন সেই যজ্ঞসাধনভূত বিরাট পুরুষের মানস যজ্ঞের সম্পন্নতার নিমিত্তে প্রোক্ষণ করেন এবং সেই বিরাট পুরুষের অবয়বেই যজ্ঞ সম্পাদন করেন।”


 Views Today : 123
Views Today : 123 Total views : 94631
Total views : 94631 Who's Online : 0
Who's Online : 0 Your IP Address : 216.73.216.27
Your IP Address : 216.73.216.27