শূদ্রকুলে জন্ম নেওয়া ব্যক্তি কি দীক্ষাগুরু হতে পারেন?~পর্ব-১
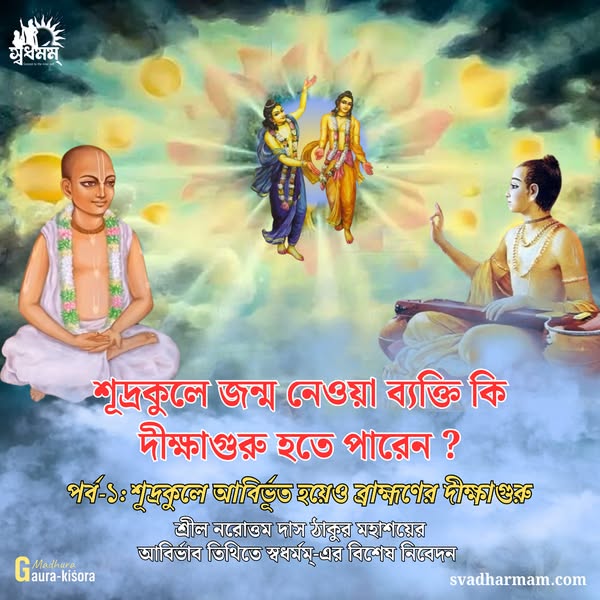
সাম্প্রতিক সময়ে শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি দীক্ষাগুরু হতে পারে না, এমন বিষয় নিয়ে প্রচুর চর্চা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু শাস্ত্রে এর ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত আছে, যেখানে বৈষ্ণবগণ শূদ্র কুলে আবির্ভূত হয়েও ব্রাহ্মণের দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন। পর্যায়ক্রমে আমরা তাদের বিষয়ে প্রকাশ করব। গৌড়ীয় পরম্পরায় শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় একজন বিখ্যাত আচার্য যিনি শূদ্র কায়স্থকুলে আবির্ভূত হলেও কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব অর্জন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন মহান দীক্ষাগুরুতে পরিণত হয়েছিলেন। নরোত্তম দাস ঠাকুর বহু স্মার্ত ব্রাহ্মণকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেছিলেন। ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ, প্রচার ও বিগ্রহসেবা: শ্রী নরোত্তম দাস বৃন্দাবনে মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা ও শ্রীল জীব গোস্বামীর নিকট শিক্ষা লাভ করে গৌড়ীয় শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি ‘ঠাকুর মহাশয়’ উপাধি লাভ করেন। এরপর গুরুবর্গের নির্দেশে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য পুনরায় পূর্ববঙ্গে ফিরে আসেন। ঠাকুর মহাশয় তাঁর আবির্ভাব স্থান খেতুরী অঞ্চলে ছয়টি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। এই উপলক্ষে তৎকালীন সময়ের সমস্ত বৈষ্ণব খেতু্রীগ্রামে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে গৌর পূর্ণিমায় এত বিশাল মহোৎসব হয়েছিল যে তা এখনও ইতিহাসে বিখ্যাত এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর প্রধান পার্ষদগণ তখন প্রকট না থাকলেও আকাশপথে আবির্ভূত হয়ে সেই উৎসবে ঠাকুর মহাশয়ের কীর্তনে নৃত্য করেছিলেন যা উপস্থিত বহু ভক্ত দর্শন করেছিলেন। যদিও ঠাকুর মহাশয় বাহ্যত শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর গুরুদেবের আদেশে এভাবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরাঙ্গ, শ্রীবল্লবীকান্ত, শ্রীরাধারমণ, শ্রীব্রজমোহন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধাকান্ত — এই ছয় বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন এবং এভাবে বৈষ্ণবদীক্ষায় দীক্ষিত ব্যক্তি যেকোনো কুলে জন্মগ্রহণ করেও বিগ্রহসেবার অধিকারী হয় এই শাস্ত্রীয় বাক্যের উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। শূদ্রগৃহে জন্ম নিয়ে ব্রাহ্মণ সন্তানদের দীক্ষা দেওয়ায় তিনি জাতি ব্রাহ্মণদের প্রবল বিরোধের সম্মুখীন হন। কিন্তু খেতুরী মহোৎসবে শ্রী নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু স্বয়ং বহু শাস্ত্র প্রমাণাদি সহযোগে বলেন কৃষ্ণ দীক্ষা গ্রহণ করলে দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হয় এবং নরোত্তম দাস ঠাকুর যদিও শূদ্র কুলোদ্ভব কিন্তু বীরচন্দ্র প্রভু তাকে ব্রাহ্মণ বলে ঘোষণা করেন ও তার বক্ষে জ্যোতির্ময় যজ্ঞোপবীত সকলকে দর্শন করান। শ্রীপ্রেমবিলাসে (১৯ বিলাসে) উল্লেখ আছে— এই নরোত্তম কায়স্থ কুলোদ্ভব হয়। শূদ্র বলি কেহ কেহ অবজ্ঞা করয়॥ কৃষ্ণভক্ত জন হয় ব্রাহ্মণ হৈতে বড়। যিঁহো শাস্ত্র জানে তিঁহো মানে করি দৃঢ়॥ কৃষ্ণ দীক্ষায় দ্বিজত্ব লাভ শাস্ত্রের বচন। ইথে অবিশ্বাস যায় নরক ভবন॥ কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণকে কৃপা: শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর নাম প্রচার এবং দীক্ষামন্ত্র দান করে গুরুরূপে সেবা করছিলেন, যা স্বভাবতই বহু লোকের মনঃপুত হয়নি। এখনকার দিনেও এরকম ব্যক্তি রয়েছে, অতএব সেই সময়ের আর কি কথা। একদিন এক কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ নরোত্তম দাস ঠাকুরের ভজনতলীতে আগমন করে হাত জোড় করে বিনীতভাবে বলতে লাগলেন, “ঠাকুর, আমি এক অহংকারী ব্রাহ্মণ, আমি আপনার সমালোচনা ও বিদ্রূপ করেছি এবং এই অপরাধের ফলে এইরকম যন্ত্রণাদায়ক রোগ লাভ হয়েছে আমি যতই ঔষধ গ্রহণ করি না কেন, এই রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। তাই আমি মনোকষ্টে পদ্মায় আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সেই রাতে আমার আরাধ্যা ভগবতী দেবী স্বপ্নে আমাকে রোগের কারণ অবগত করে আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করতে কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু আমি মহাপাপী, ক্ষমার অযোগ্য। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।” ব্রাহ্মণের এই আর্তনাদ দেখে ঠাকুরের হৃদয় বিগলিত হয়ে গেল। ঠাকুর মহাশয় তাকে ভূমি থেকে তুলে হরে কৃষ্ণ কীর্তন করতে করতে আলিঙ্গন করলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণও কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে কীর্তন করতে করতে হাত তুলে নৃত্য করতে লাগলেন। যখন ব্রাহ্মণের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলো, তিনি দেখলেন তার দেহ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। তখন সেই ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন এবং অহংকারশূন্য হয়ে কৃষ্ণভক্তি করতে লাগলেন। সেই অঞ্চলের লোকজন এই ঘটনা শুনতে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং সকলেই নরোত্তম দাস ঠাকুরের মহিমা উপলব্ধি করতে পারলেন। তাঁরা বলতে লাগলেন— কেহ কার প্রতি কহে, হও সাবধান। শ্রীনরোত্তমেরে না করিহ শূদ্রজ্ঞান॥ কেহ কহে মত্ত হৈয়া বিপ্র অহংকারে। নরোত্তম হেন রত্ন নারি চিনিবারে ॥ (নরোত্তম বিলাস, নবম বিলাস) হরিরাম, রামকৃষ্ণ ও শিবানন্দ উদ্ধার: শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের ফলে কালক্রমে এই অঞ্চলের বহু লোক নিতাই-গৌরের প্রেমভক্তি গ্রহণ করতে লাগল। ঠাকুর মহাশয় তাদের দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করলেন। বহু ব্রাহ্মণসন্তানও ঠাকুর মহাশয়ের নিকট দীক্ষা নিয়েছিলেন, যাদের মধ্যে হরিরাম আচার্য, রামকৃষ্ণ আচার্য, গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী বিখ্যাত। এছাড়াও জগন্নাথ আচার্য, শিবানন্দ আচার্য, রূপ নারায়ণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণও অগ্রগণ্য। হরিরাম ও রামকৃষ্ণ ঠাকুর আশ্রয়ে কৃষ্ণভক্তি ও শাস্ত্রশিক্ষা করতে থাকলে তাদের পিতা শিবানন্দ আচার্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তিনি তাদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, “ব্রাহ্মণ হয়ে কায়স্থের পায়ে ধরতে তোদের লজ্জা করল না? আর সে কোথাকার কোন বৈষ্ণব, যে কিনা ব্রাহ্মণকে শিষ্য করার দুঃসাহস করেছে?” তখন দুই ভাই পিতাকে বললেন, “পিতা, আপনি দয়া করে শান্ত হোন, আপনি পণ্ডিতগণসহ শাস্ত্রবিচার আয়োজন করুন, আমরা শাস্ত্রের বিচারে এর উত্তর দেবো। সেই বিচারে যদি আপনার মত শ্রেষ্ঠ হয়, তাহলে আমরা প্রায়শ্চিত্তও করব।” শিবানন্দ তখন আরো দুইজন পণ্ডিতকে আমন্ত্রণ করে শাস্ত্রবিচার আয়োজন করেন এবং পরাজিত হন। তখন তিনি মিথিলা থেকে এক বিখ্যাত পণ্ডিত মুরারি মহাশয়কে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু শ্রীগুরুদেবের আশির্বাদে হরিরাম ও রামকৃষ্ণ তাঁকেও ভাগবতের সিদ্ধান্ত দ্বারা পরাজিত করেন। মুরারি মহাশয় তখন লজ্জায় স্থান ত্যাগ করেন। সেদিন রাতে শিবানন্দ আচার্যের পূজিতা দুর্গাদেবী তাকে স্বপ্নে বললেন, “যারা শ্রীহরির প্রিয় ভক্ত, তাঁরাই আমার প্রিয়। তুই যদি রক্ষা পেতে চাস, তাহলে শ্রী নরোত্তমের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর।” পরদিন পরিবারের বাকি সকলকে নিয়ে শিবানন্দ আচার্য শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের চরণাশ্রয় গ্রহণ করলেন। গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও মণিপুরী বৈষ্ণব হরিরাম ও রামকৃষ্ণের প্রচারের ফলে গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয়ের চরণাশ্রয় করেন এবং অল্পসময়ে ভক্তিশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত হন। তিনি পরবর্তী সময়ে মণিপুরী সম্প্রদায়ে কৃষ্ণভক্তি প্রচার করেছিলেন, যার ফলে আজও সেখানে কৃষ্ণভক্তির প্রবাহ দেখা যায়। রূপ নারায়ণ ও রাজা নরসিংহ ক্রমে ক্রমে নরোত্তম দাস ঠাকুরের ব্রাহ্মণ শিষ্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। অনেক প্রধান ব্রাহ্মণ নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রেমভক্তির বন্যায় নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন। এতে স্মার্ত ব্রাহ্মণ সমাজ ঠাকুর মহাশয়ের প্রতি কুপিত হতে লাগলেন। কারণ ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য সংখ্যা এতোই বেড়েছে যে, তাকে আর একঘরে করে দিলেও কোনো লাভ হবে না। শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের মহিমা দেখে স্মার্ত ব্রাহ্মণ সমাজ ঈর্ষায় দগ্ধ হতে লাগল। তাই সকলেই রাজা নরসিংহের কাছে গিয়ে নালিশ করল, “মহারাজ, আপনি যদি ব্রাহ্মণ সমাজকে না বাঁচান, তবে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র নরোত্তম শুদ্র হয়ে ব্রাহ্মণদের শিষ্য করছে এবং জাদু-মন্ত্র দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করছে।” রাজা নরসিংহ বললেন, “আমি আপনাদের রক্ষা করব। আমায় কী করতে হবে বলুন?” ব্রাহ্মণগণ বললেন, “মহাদিগবিজয়ী পণ্ডিত শ্রীরূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে আমরা খেতুরিতে গিয়ে নরোত্তমকে পরাস্ত করব। এ কাজে আপনি আমাদের সাহায্য করুন।” রাজা নরসিংহ বললেন, “আমিও আপনাদের সাথে যাবো।” রাজা তার সভাসদ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ ও সভাপণ্ডিত রূপনারায়ণ সহ বিষয়টি আলোচনা করলেন এবং স্থির করলেন সবাইকে নিয়ে খেতুরি অভিমুখে যাত্রা করবেন। স্মার্ত ব্রাহ্মণগণ দিগ্বিজয়ী রূপনারায়ণকে সঙ্গে নিয়ে খেতুরি গ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। একজন লোক এসে তা শ্রীনরোত্তম ও শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ আদি সকল ভক্তকে জানালেন। এদিকে এ
যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ~২য় পর্ব

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কংস, শিশুপাল, শকুনি, দুর্যোধনাদি অসুরদের মতো পূর্বজন্মের ঈর্ষাপরায়ণ, বিষ্ণুবিদ্বেষী কতিপয় ব্যক্তি ইহজন্মেও অবচেতন মনের সেই প্রবৃত্তির জন্য তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণ) সাধারণ মনুষ্য বানাতে ব্যতিব্যস্ত। তারা নানা ফন্দি আঁটে তাঁর ভগবত্তাকে নস্যাৎ করার জন্য। এই নির্বোধদের এমনই এক দাবি, “শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর নন। তিনি যোগযুক্ত হয়ে অর্থাৎ যোগের দ্বারা পরমেশ্বরের সাথে যুক্ত হয়ে ভগবদ্গীতার জ্ঞান প্রদান করেছিলেন”। অথচ পুরো ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যে ঠিক কখন যোগযুক্ত হলেন আর কখন তার স্বাভাবিক স্বরূপ(মনুষ্য~অর্বাচীনদের ভাষ্যমতে)-এ ফিরে এলেন তার কোন ইয়ত্তা আমরা খুঁজে পাই না। এই নির্বোধরাও এই বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলতে পারে না। সমগ্র গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অসংখ্যবার নিজেকে পরমেশ্বর, জীবের অন্তরাত্মা, পরমব্রহ্ম দাবি করেছেন। আবার গুটিকয়েক জায়গায় তিনি পরোক্ষভাবে পরমাত্মা’র শরণ গ্রহণ করার কথাও বলেছেন(গীতাঃ ১৮/৬১-৬২)। এবং এই দুটি শ্লোকের ব্যাখ্যাও আমরা ১ম পর্বে করেছি। ১ম পর্বঃ https://svadharmam.com/krishna-is-the-supreme-personality-of-godhead/ ⚫ মূর্খদের দাবি অনুযায়ী যদি ধরেও নেই যে, “শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার সঙ্গে যোগের দ্বারা যুক্ত হয়ে গীতার জ্ঞান প্রদান করেছিলেন” তবে সেই দাবী অনুযায়ী ১৮/৬১-৬২ শ্লোক বিবেচনা করলে দেখা যায় উক্ত শ্লোক দুটি শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার সহিত যোগবিযুক্ত অবস্থায় বলেছেন। সেজন্য নিজেকে শুধুই শ্রীকৃষ্ণ ভেবেছেন ও অর্জুনকে পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন । কিন্তু পরক্ষণেই আবার ১৮/৬৬ শ্লোকে পরমাত্মার সহিত যোগযুক্ত হয়ে পরমাত্মায় একাত্ম হয়ে গিয়ে (মূর্খমতে) নিজের (পরমেশ্বরের) শরণ গ্রহণ করার কথা বলেছেন। ⚫ তবে কি শ্রীকৃষ্ণ মুহুর্তেই যোগযুক্ত ও বিযুক্ত(যোগমুক্ত) হয়ে যান??? এইসব হাস্যকর, রম্য দাবি শুনে মনে হয় যেন “শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মার সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়ার জন্য যে Internet Connection Providers/Device ব্যবহার করতেন তার সিগন্যাল খুবই দুর্বল ছিল!। তা নাহলে তিনি কখন যে যোগযুক্ত হচ্ছেন (Connected) আর কখন যোগমুক্ত (Disconnected) হচ্ছেন তা বুঝা খুব মুশকিল।” যদিও ভগবদ্গীতায় কয়েক জায়গায়(১১/৮-৯; ১৮/৭৮) ভগবানকে “যোগেশ্বর” বলা হয়েছে। তা এই পর্বে আলোচনা করা হবে যে, শ্রীকৃষ্ণকে কেন “যোগেশ্বর বলা হয়েছে?”। দ্রঃ আমরা শ্রীকৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান জ্ঞানে এবং ভগবদ্গীতা’র “ভগবান উবাচ” বলে যত শ্লোক আছে তা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই মুখনিঃসৃত বিবেচনা করেই মূর্খদের দাবি খণ্ডণ করবো। ———————————————————————————————————————————————— শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত যোগ শক্তির অধীশ্বরঃ যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অণিমা-মহিমাদি অষ্টসিদ্ধি ও সমস্ত শক্তির প্রবর্তক – ♦মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে; গীতা ১০/৮ ~ আমার থেকেই সমস্ত কিছু প্রবর্তিত হয়েছে তাই শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত যোগ শক্তির অধীশ্বর অর্থাৎ যোগেশ্বর। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের বহু জায়গায় শ্রীকৃষ্ণকে ‘যোগেশ্বর’(১০/১৪/২১, ১/৮/১৪, ১/৮/৪৩), ‘যোগাধীশ’(১০/১৯/১২), ‘যোগবীর্যং’(১০/১৯/১৪) সম্বোধন করা হয়েছে। ———————————————————————————————————————————————— শ্রীকৃষ্ণই সকল জীবের হৃদ্যন্তস্থ পরমাত্মাঃ যারা অণিমা, মহিমা আদি বিভিন্ন যোগশক্তি লাভের আশায় যম, নিয়ম প্রাণায়াম আদি অষ্টাঙ্গ যোগ অনুশীলন করেন তাঁদেরও অন্তিম লক্ষ্য বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন– ♦যোগীনামাপি সর্বেষাম মদ্গতেন অন্তরাত্মনা গীতা ৬/৪৭ ~যোগীদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে আমার(শ্রীকৃষ্ণের) ভজনা করেন। ♦সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো গীতা ১৫/১৫ আমি(শ্রীকৃষ্ণ) সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি তাই সেইসব যোগীদের তথা সকল জীবের হৃদয়ে অবস্থিত অন্তরাত্মা শ্রীকৃষ্ণই। ———————————————————————————————————————————————— শ্রীকৃষ্ণই যোগেশ্বরেশ্বরঃ অনেক সময় সিদ্ধ যোগী(কর্দম মুনি, শুকদেব গোস্বামী) বা পরমেশ্বর ভগবানের শক্ত্যাবেশ অবতার(নারদ, ব্যসদেব, পরশুরাম) অথবা ভগবানের শুদ্ধভক্ত(যাঁরা ইতিমধ্যেই ব্রহ্মভূত স্তর প্রাপ্ত হয়েছেন) তাঁদের ক্ষেত্রেও (ভক্তিযোগেন, সেবতে…..ব্রহ্মভূয়ায়, কল্পতে; গীতাঃ১৪/২৬) “যোগেশ্বর” সম্বোধন ব্যবহৃত হয়। কারণ তাঁরা বিশেষ কার্যসিদ্ধির জন্য পরমেশ্বরের দ্বারা কৃপাপ্রাপ্ত। তাই তাঁরাও পরমেশ্বরের অনন্ত যোগশক্তির ক্ষীয়োদংশ প্রতিফলিত করেন। যেমন শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত আছে যে, কর্দম মুনি নিজেকে নয়টি রূপে বিভক্ত করেছিলেন। আবার কখনও শিব, ব্রহ্মা আদি মহান দেবতাদেরকেও মহান যোগী, পরম যোগী, যোগেশ্বর বলা হয়। কেননা তাঁরাও নিরন্তর শ্রীহরির ধ্যানে মগ্ন থাকেন। কপর্দ্দী জটীলো মুণ্ডঃ শ্মশানগৃহসেবকঃ॥ উগ্রব্রতধরো রুদ্রো যোগী পরমদারুণঃ। দক্ষক্রতুহরশ্চৈব ভগনেত্রহরস্তথা॥ নারায়ণাত্মকো জ্ঞেয়ঃ পাণ্ডবেয় যুগে যুগে॥ মহাভারত, শান্তিপর্ব ৩২৭।১৮-২১ অনুবাদ: যিনি বিশাল জটাজুটযুক্ত, শ্মশানবাসী, কঠোরব্রতপরায়ণ, পরমযোগী রুদ্র যিনি দক্ষযজ্ঞ নাশ করেছিলেন, ভগের চোখ উৎপাটন করেছিলেন তিনি নারায়ণের অংশস্বরূপ। দিষ্ট্যা জনার্দন ভবানিহ নঃ প্রতীতো যোগেশ্বরৈরপি দুরাপগতিঃ সুরেশৈঃ। শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৪৮/২৭ অনুবাদঃ হে জনার্দন, আমাদের মহা সৌভাগ্যের দ্বারা এখন আপনি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছেন, কারণ যোগেশ্বরগণ এবং দেবেন্দ্রগণও অতি কষ্টের দ্বারা কেবল এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারেন। তাই পরমেশ্বর ভগবান এই সমস্ত যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর। যেমনটা বলা হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতমে— ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্যো ভবতা ভগবত্যজে। যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২৯/১৬ অনুবাদঃ জন্মরহিত যোগেশ্বরেশ্বর পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে তোমার বিস্মিত হওয়া উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত এই ভগবানই জগতকে মুক্তি প্রদান করেন। বীক্ষ্য তান্ বৈ তথাভূতান্ কৃষ্ণো যোগেশ্বরেশ্বরঃ। ঈক্ষয়ামৃতবর্ষিণ্যা স্বনাথান্ সমজীবয়ৎ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৫/৫০ অনুবাদঃ সেই যোগেশ্বরগণেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত ভক্তদের প্রতি অনুকম্পা অনুভব করেছিলেন। এভাবেই তিনি তাঁদের প্রতি তাঁর অমৃতবৎ কৃপাদৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁদের পুনর্জীবিত করেছিলেন। নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি। ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ । তথাপি হু্যত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তির্দৃঢ়া ন চাম্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০/২৩/৪৩-৪৪ অনুবাদঃ এই নারীগণের কখনও উপনয়নাদি সংস্কার হয়নি, তারা ব্রহ্মচারীরূপে গুরুর আশ্রমে বাস করেনি, তারা কোনও তপশ্চর্যার অনুষ্ঠান করেনি, তারা আত্মার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করেনি, শৌচাচার অথবা পুণ্য ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানেও যুক্ত নয়, তবুও উত্তমশ্লোক ও যোগেশ্বরেরও ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাদের দৃঢ় ভক্তি রয়েছে। পক্ষান্তরে, এই সমস্ত প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেও ভগবানের প্রতি আমাদের এরূপ ভক্তি নেই। যুধিষ্ঠির উবাচ কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীশ্বর। যোগেশ্বরাণাং দুর্দর্শো যন্নো দৃষ্টঃ কুমেধসাম্ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত: ১০/৫৮/১১ অনুবাদঃ রাজা যুধিষ্ঠির বললেন-হে অধীশ্বর, আমি জানি না, আমরা মূর্খেরা কোন্ পুণ্যকর্ম করেছি যার ফলে যোগেশ্বরগণেরও দুর্লভদর্শন আপনাকে আমরা দর্শন করতে পারছি। নৃগ রাজার প্রার্থনা সত্বং কথং মম বিভোেহক্ষিপথঃ পরাত্মা যোগেশ্বরৌঃ শ্রুতিদৃশামলহৃদ্বিভাব্যঃ । সাক্ষাদধোক্ষজ উরুব্যসনান্ধবুদ্ধেঃ স্যান্মেহনুদৃশ্য ইহ যস্য ভবাপবর্গঃ ৷৷ শ্রীমদ্ভাগবত: ১০/৬৪/২৬ অনুবাদঃ হে সর্বশক্তিমান, এখানে আমার সামনে আমার দু’নয়ন আপনাকে দর্শন করছে, এটা কিভাবে সম্ভব হল? আপনি পরমাত্মা, যাকে মহা-যোগেশ্বরগণ তাঁদের শুদ্ধ-অন্তরে কেবলমাত্র চিন্ময় বেদনয়নের মাধ্যমেই ধ্যান করেন। তা হলে, হে অধোক্ষজ, জাগতিক জীবনের দুঃসহ দুর্বিপাকে আমার বুদ্ধি অক্ষম হয়ে পড়লেও কিভাবে আপনি প্রত্যক্ষরূপে আমার দৃষ্টি গোচর হলেন? যিনি এই পৃথিবীতে তাঁর জড় জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করেছেন, কেবলমাত্র তিনিই তো আপনাকে দর্শনে সমর্থ হন। ———————————————————————————————————————————————– অনেকেই আবার মনে করেন “শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর গীতার জ্ঞান ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তিনি পুনরায় যোগযুক্ত হয়ে “অনুগীতা” প্রদান করেছিলেন।” এর খণ্ডন/উওর দেওয়া হয়েছে লিংকঃ https://svadharmam.com/does-krishna-forgot-the-transendental-knowledge/ ———————————————————————————————————————————————— শ্রীকৃষ্ণের চেয়ে উত্তম যোগী কেউ নেইঃ যেহেতু পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ এই জগতে ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে অবতরণ করেন তাই তিনি লোকশিক্ষার জন্য (যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ, গীতাঃ৩/২১) বহুবিধ যাগ-যজ্ঞ, তপস্যা, বিদ্যানুশীলন, গুরুগ্রহণ ও নানা সামাজিক অনুষ্ঠান করেন। এবং যেহেতু তাঁর আরেক নাম অসমোর্ধ তাই তিনি যে আচরণই করেন না কেন তা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, শ্রেষ্ঠ সন্তান, শ্রেষ্ঠ শিষ্য এবং শ্রেষ্ঠ যোগীও। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ বিশ্বাত্মন্ বিশ্বভাবন। প্রপন্নাং পাহি গোবিন্দ শিশুভিশ্চাবসীদতীম্ ৷৷ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৯।১১ অনুবাদঃ কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। হে পরম যোগী! হে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরমাত্মা ও রক্ষক। হে গোবিন্দ! দয়া করে আপনার শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন। সর্বং নরবরশ্রেষ্ঠৌ সর্ববিদ্যাপ্রবর্তকৌ। সকৃন্নিগদমাত্রেণ তৌ সঞ্জগৃহতুনূপ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৪৫।৩৫ অনুবাদঃ হে রাজন, সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ
রাসলীলা’র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য-(২য় পর্ব)

আপ্তকাম, হৃষিকেশ(ইন্দ্রিয়াধিপতি), জগৎপতি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট নর-লীলা ‘রাস’।যা ইন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ সাধারণ মানুষের কাম-ক্রীড়ার মতো মনে হলেও বস্তুত তা জড়াতীত। কেননা এই ‘রাস’ কীর্তনের শ্রোতা-বক্তা উভয়েই ছিলেন সুব্রত(নিষ্ঠা সহকারে ব্রহ্মচর্য ব্রতাদি পালনকারী)। উন্নতস্তরের মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য যে, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বিষয়ে অজ্ঞ মানুষদের মনেই কেবল এই সকল সন্দেহের উদয় হবে। তাই অনাদিকাল থেকেই মহান ঋষিবর্গ ও পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো উন্নত রাজারা ভাবীকালের জন্য প্রামাণ্য উত্তর প্রস্তুত রাখবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত প্রশ্ন প্রকাশ্যেই উত্থাপন করেছিলেন। এ পর্বে আমরা শুকদেব-পরীক্ষিত মহারাজের সেই কথোপকথন শ্রবণ করবো। যা আলোচিত হয়েছে শ্রীমদ্ভাগবত এর ১০/৩৩/২৬-৩৬ শ্লোকে। শ্রীপরীক্ষিদুবাচ সংস্থাপনায় ধর্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ । অবতীর্ণো হি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥ ২৬ ॥ স কথং ধর্মসেতুনাং বক্তা কর্তাভিরক্ষিতা। প্রতীপমাচরদ্ ব্রহ্মন্ পরদারাভিমর্শনম্ ॥ ২৭ ॥ অন্বয়: শ্রীপরীক্ষিৎ উবাচ – শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন; সংস্থাপনায় – স্থাপন করার জন্য; ধর্মস্য – ধর্মের, প্রশমায় – দমন করার জন্য; ইতরস্য – অধর্মের; চ – এবং, অবতীর্ণঃ – অবতরণ করেন (পৃথিবীতে); হি – বস্তুত; ভগবান্ – পরমেশ্বর ভগবান; অংশেন – তাঁর অংশপ্রকাশ (শ্রীবলরাম) সহ; জগৎ – সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের, ঈশ্বরঃ – প্রভু; সঃ – তিনি; কথম্ – কিভাবে; ধর্ম-সেতুনাম্ – ধর্ম-মর্যাদার; বক্তা – বক্তা, কর্তা – কর্তা; অভিরক্ষিতা – স্বাক্ষক, প্রতীপম্ – বিপরীত; আচরৎ – আচরণ করলেন; ব্রাহ্মন্ – হে ব্রাহ্মহ্মণ, শুকদেব গোস্বামী, পর – অন্যদের, দার – পত্নীদের, অভিমর্শনম্ – স্পর্শ করলেন। অনুবাদ: পরীক্ষিৎ মহারাজ বললেন-হে ব্রাহ্মণ, যিনি পরমেশ্বর ভগবান, জগদীশ্বর, ধর্ম সংস্থাপন ও অধর্মের বিনাশের জন্য যাঁর অংশপ্রকাশ সহ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন, প্রকৃতপক্ষে যিনি সমাজধর্মের মূল বক্তা, কর্তা ও সংরক্ষক, তিনি তা হলে কিভাবে পরস্ত্রীদের স্পর্শ করে প্রতিকূল আচরণ করলেন? ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য: শুকদেব গোস্বামী যখন বলছিলেন, তখন পরীক্ষিৎ মহারাজ লক্ষ্য করলেন যে, গঙ্গাতীরের সেই সমাবেশে উপবিষ্ট কিছু ব্যক্তি ভগবানের কার্যাবলী সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করছিলেন। এই সকল সন্দেহগ্রস্ত ব্যক্তিরা ছিল কর্মী, জ্ঞানী ও অন্যান্যরা, যারা ভগবানের ভক্ত নয়। তাদের সেই সন্দেহগুলি নিরসনের জন্য তাদের পক্ষ থেকে পরীক্ষিৎ মহারাজ এই প্রশ্নটি করেছিলেন। আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতম্। কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥ ২৮ ॥ অন্বয় আপ্তকামঃ-আত্ম-তৃপ্ত, যদুপতি- যদু বংশের অধিপতি, কৃতবান্- করলেন, বৈ-অবশ্যই। জুগুস্পিতম্-এই ধরনের নিন্দনীয়, কিম্-অভিপ্রায়ঃ-কি উদ্দেশ্যে, এতৎ-এই। নঃ-আমাদের, সংশয়ম্- সন্দেহ; ছিদ্ধি- ছেদন করুন, সুব্রত- হে নিষ্ঠাবান ব্রতপালনকারী। অনুবাদ হে নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারী, আত্মতৃপ্ত যদুপতি কি উদ্দেশ্যে এই ধরনের নিন্দিত আচরণ করেন, দয়া করে তা বর্ণনা করে আমাদের সন্দেহ অঞ্জন করুন। তাৎপর্য উন্নতস্তরের মানুষের কাছে সহজেই বোধগম্য যে, ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাস বিষয়ে অজ্ঞ মানুষদের মনেই কেবল এই সকল সন্দেহের উদয় হবে। তাই অনাদিকাল থেকেই মহান ঋষিবর্গ ও পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো উন্নত রাজারা ভাবীকালের জন্য প্রামাণ্য উত্তর প্রস্তুত রাখবার উদ্দেশ্যে এই সমস্ত প্রশ্ন প্রকাশ্যেই উত্থাপন করেছিলেন। শ্রীশুক উবাচ ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা ॥ ২৯ ॥ অন্বয় শ্রীশুকঃ উৰাচ-শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন, ধর্ম-ব্যতিক্রমঃ–ধর্মনীতির ব্যতিক্রম; দৃষ্টঃ-দেখা যায়, ঈশ্বরাণাম্- শক্তিশালী নিয়ন্তাগণের, চ-ও, সাহসম্-দুঃসাহস, তেজীয়সাম্-চিন্ময়ভাবে তেজস্বী, ন-না, দোষায়-দোষের; বহ্নেঃ -অগ্নির; সর্ব-সর্ব, ভুজঃ-ভক্ষণ; যথা-যেমন। অনুবাদ শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন-ঐশ্বরিক শক্তিমান নিয়ন্তাদের কার্যকলাপের মধ্যে আমরা আপাতদৃষ্টিতে সমাজনীতির দুঃসাহসিক ব্যতিক্রম লক্ষ্য করলেও, তাতে তাঁদের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ তাঁরা আগুনের মতোই সর্বভুক হলেও নির্দোষ হয়ে থাকেন। তাৎপর্য মহান তেজস্বী ব্যক্তিত্বগণ আপাতদৃষ্ট সমাজনীতি লঙ্ঘনের ফলে অধঃপতিত হন না। শ্রীধর স্বামী এই প্রসঙ্গে অন্যত্র ব্রহ্মা, ইন্দ্র, সোম, বিশ্বামিত্র ও অন্যান্যদের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। আগুন সবকিছুই ভক্ষণ করে, কিন্তু তার ফলে আগুনের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন হয় না। তেমনই, মহান ব্যক্তির আচরণের কোনও অনিয়ম হলেও তাঁর মর্যাদাহানি হয় না। যাই হোক, পরবর্তী শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন যে, আমরা যদি ব্রহ্মাণ্ড শাসনকারী শক্তিমান পুরুষদের অনুকরণ করার চেষ্টা করি, তবে তার ফল হবে ভয়াবহ। নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্ ॥ ৩০ ॥ অন্বয় ন-না, এতৎ- এই; সমাচরেৎ-অনুষ্ঠান করা উচিত; জাতু-কখনও; মনসা-মনে মনে; অপি-ও; হি-নিশ্চিতভাবে, অনীশ্বরঃ- যে ঈশ্বর নয়, বিনশ্যতি-বিনাশ প্রাপ্ত হয়; আচরন মৌঢ্যাৎ-মূঢ়তা প্রযুক্ত আচরণ করে; যথা-যেমন; অরুদ্রঃ-যে রুদ্রদেব নয়; অব্ধিজম্- সমুদ্র হতে উৎপন্ন; বিষম্-বিষ। অনুবাদ যে ঈশ্বর নয়, তার কখনই মনে মনেও ঈশ্বরের আচরণের অনুকরণ করা উচিত নয়। যদি মুঢ়তাবশত কোনও সাধারণ মানুষ এই ধরনের আচরণের অনুকরণ করে, তা হলে সে নিজেকেই কেবল ধ্বংস করবে, যেমন রুদ্রদেব না হয়েই রুদ্রের মতো সমুদ্রপরিমাণ বিষ পান করার চেষ্টার ফলে মানুষ নিজেকেই বংস করে। তাৎপর্য রুদ্র অর্থাৎ ভগবান শিব একবার সমুদ্রপরিমাণ বিষ পান করেছিলেন, আর তার ফলে এক আকর্ষণীয় নীল চিহ্ন তাঁর কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু আমরা যদি তেমন বিষের এক ফোঁটাও পান করি, আমরা সঙ্গে সঙ্গে মারা যাব। তাই আমাদের যেমন শিবের লীলা অনুকরণ করা উচিত নয়, তেমনি গোপীগণের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাদিও অনুকরণ করা উচিত নয়। আমাদের পরিষ্কারভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যে, ধর্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ ভগবান কৃষ্ণ আমাদের কাছে প্রতিপাদন করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে যে, নিশ্চিতভাবে তিনিই ভগবান, আমরা নই। সেটি অবশ্যই স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হওয়া উচিত। ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির সঙ্গে উপভোগ করেন আর এইভাবে আমাদের পারমার্থিক স্তরে আকর্ষণ করেন। আমাদের কৃষ্ণকে অনুকরণ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণ তা হলে অপরিসীম দুঃখ পেতে হবে। ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তৎ সমাচরেৎ ॥ ৩১ ॥ অন্বয় ঈশ্বরাণাম্-পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি প্রদত্ত সেবক, বচঃ-কথা; সত্যম্- সত্য, তথা এব-ও, আচরিতম্- তারা যা করে, কচিৎ-কখনও, তেষাম্-তাদের। যৎ- যাঃ স্ব বচঃ –তাদের নিজ কথার সঙ্গে, যুক্তম- সামঞ্জস্যপূর্ণ, বুদ্ধিমান- যিনি বুদ্ধিমান; তৎ-সেই, সমাচরেৎ-পালন করা উচিত। অনুবাদ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিপ্রদত্ত সেবকদের কথা সকল সময়েই সত্য আর সেই কথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ তাঁদের আচরণ অনুকরণযোগ্য। অতএব তাঁদের নির্দেশ পালন করা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের উচিত। তাৎপর্য ঈশ্বর শব্দটাকে সচরাচর সংস্কৃত অভিযানে “প্রভু, পরিচালক, রাজ্য” এবং “সমর্থ, সম্পাদনে ক্ষমতাসম্পন্ন” রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ সাধারণত ঈশ্বর শব্দটিকে “নিয়ন্তা” রূপে অনুবাদ করতেন যা চমৎকারভাবে “পরিচালক বা রাজা” এবং “সমর্থ ব্য সম্পাদনে ক্ষমতাসম্পন্ন” মুখ্যত এই দুই প্রাথমিক ধারণারই সমন্বয় সাধন করে। কোনও পরিচালক অযোগ্য হতে পারেন কিন্তু একজন নিয়ন্ত্রক হন তিনিই, যিনি প্রভু বা পরিচালকরূপে প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটিকে সংঘটিত করান। সর্বকারণের পরম কারণ ভগবান কৃষ্ণ নিশ্চিতভাবেই তাই পরমনিয়ন্তা বা পরমেশ্বর। ঈশ্বর বা শক্তিমান পুরুষেরা যে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষেরা, বিশেষত পশ্চিমী দেশগুলিতে সচেতন নন। ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আধুনিক নির্বিশেণবাদী ধারণা অনুযায়ী বর্ণনা করা হয় যে, প্রাণহীন মহাজগতে পৃথিবী অনর্থক ভাসছে। এইভাবে আমরা জীবনের এক অনিশ্চিত চরম লক্ষ্য নিয়েই নিজেদের সংরক্ষণ করছি আর বংশরক্ষার প্রক্রিয়ায় জন্ম দিচ্ছি এবং পরের পর নিজস্ব ‘চরম লক্ষ্য’ সংরক্ষণ ও জন্মদানের প্রক্রিয়ায় যুক্ত থেকে একটি অর্থহীন ঘটনাশৃঙ্খল বা ধারা তৈরি হয়ে চলেছে। অজ্ঞ জড়বাদীদের উদ্ভাবিত এই ধরনের নিখালা এবং অর্থহীন জগতের তুলনায় যে প্রকৃত মহা-জগৎ রয়েছে, তা জীবন প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এবং সবিশেষ ব্যক্তি জীবন এবং প্রকৃতপক্ষে ভগবানের অস্তিত্বে পরিপূর্ণ, যে ভগবান এই সকল অস্তিত্ব ধারণ করে আছেন ও পালন করছেন। পরমেশ্বর
কুব্জার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ক কেমন ছিল?

অনেকেই কুব্জার সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্পর্ককে সন্দেহভাজন দৃষ্টিতে দেখেন। কিন্তু আসলে শাস্ত্রের মর্মার্থ না জেনেই আমরা এমনটা ধারণা করি কেবল। তাই এর উত্তর প্রদান করেছেন আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মহাশয়। শ্রীমদ্ভাগবতঃ ১০/৪২/০১ শ্রীশুক উবাচ অথ ব্রজন্ রাজপথেন মাধবঃ স্ত্রিয়ং গৃহীতাঙ্গবিলেপভাজনাম্। বিলোক্য কুব্জাং যুবতীং বরাননাং পপ্রচ্ছ যান্তীং প্রহসন্ রসপ্রদঃ ॥ অন্বয়ঃ শ্রীশুকঃ উৰাচ-শুকদেব গোস্বামী বললেন, অথ-অতঃপর, ব্রজল্-হাঁটতে হাঁটতে, রাজপথেন রাজপথে, মাধবঃ-কৃষ্ণ, প্রিয়ম্ এক রমণী, গৃহীত-ধারণ করে; অঙ্গ-দেহের, বিলেপ-বিলেপন, ভাজনাম্-পাত্র; বিলোক্য দর্শন করে; কুঞ্জাম্-কুজা। মুৰতীম্-যুবতী। বর-আননাম্-সুমুখশ্রীযুক্ত, পপ্রচ্ছ-তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, যাস্তীম্ যাচ্ছিল; প্রহসন্-হাসতে হাসতে, রস-প্রেমানন্দ, প্রদঃ প্রদাতা। অনুবাদঃ শুকদেব গোস্বামী বললেন রাজপথে হাঁটতে হাঁটতে তিনি দেখলেন যে, সুপ্রীমুখ এক কুব্জা যুবতী রমণী সুগন্ধি অঙ্গবিলেপন দ্রব্যের পাত্র বহন করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রেমানন্দ প্রদাতা সহাস্যে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তাৎপর্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, যুবতী কুজা কন্যাটি প্রকৃতপক্ষে ভগবানের পত্নী সত্যভামার অংশপ্রকাশ। সত্যভামা ভগবানের ভু-শক্তি নামক অন্তরঙ্গ্য শক্তি এবং তাঁর এই প্রকাশ পৃথ্বী নামে পরিচিত, যা অসংখ্য খল শাসকের মহাভারে অবনত হয়ে পৃথিবীরূপে বিরাজ করছে। শ্রীকৃষ্ণ এইসকল দুষ্ট রাজাদের দমন করার জন্যই অবতরণ করেছেন আর তাই এই শ্লোকসমূহে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর ত্রিবক্রা কুজাকে সমুন্নত করার যে লীলা, সেটি তাঁর ভূভার সংশোধনেরই প্রতিকস্বরূপ। একই সঙ্গে ত্রিবক্রাকে ভগবান তাঁর সঙ্গে প্রণয় সম্পর্কও প্রদান করেছিলেন। প্রদত্ত ব্যাখ্যার সংযোজনরূপে রস-প্রদ শব্দের দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে যে, যুবতী কুজার সঙ্গে তাঁর আচরণের মাধ্যমে ভগবান তাঁর গোপবালক সখাদের মুগ্ধ করেছিলেন।
ভগবান কেন ভক্তের ডাকে সাড়া দেন না?
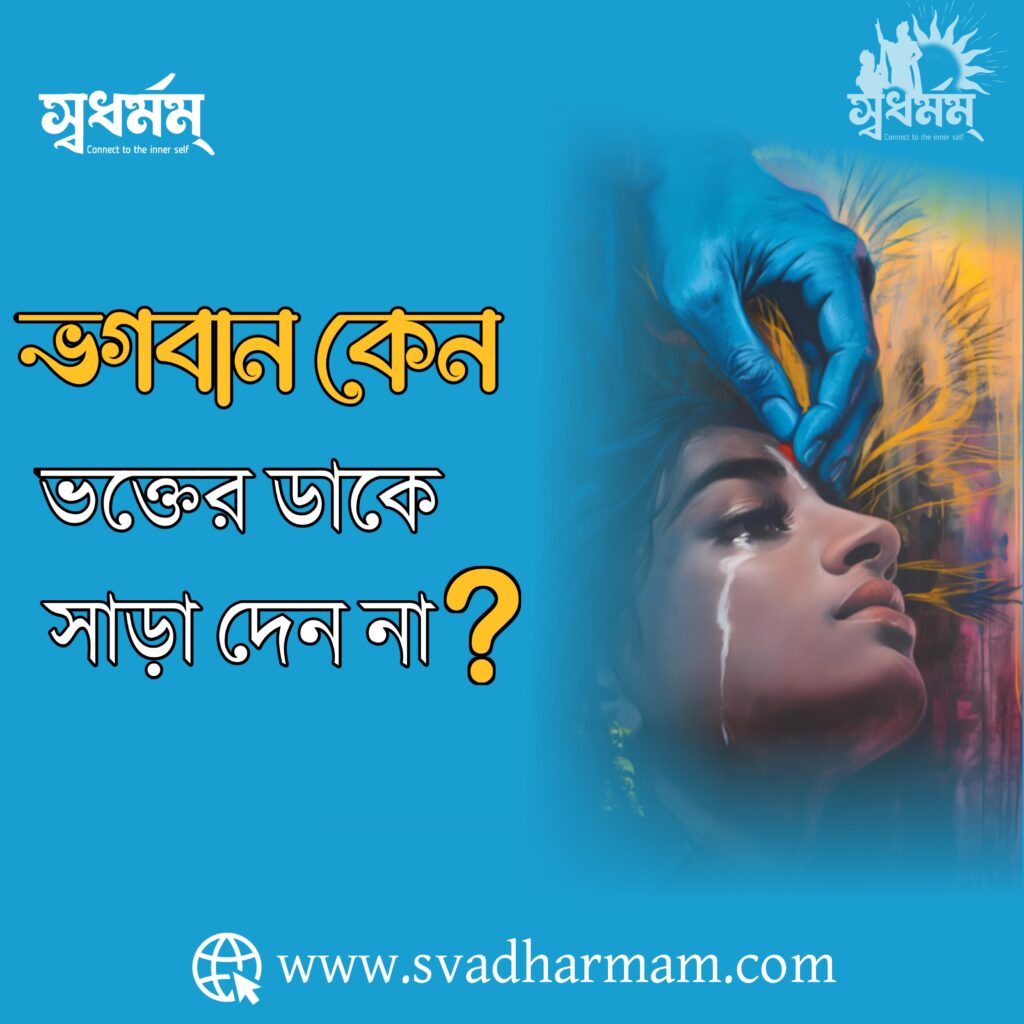
ভক্ত জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখে জর্জরিত হয়ে কখনও বা বলেন “ভগবান কেন আমার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন না?“। — এই প্রশ্নের উত্তর ভগবান স্বয়ং প্রদান করছেন শ্রীমদ্ভাগবতমে। প্রেক্ষাপটঃ রাসলীলা’র সময় ভগবান ব্রজগোপীকাদের ‘অহং’ ভাবের জন্য তাঁদের পরিত্যাগ করেছিলেন। তখন গোপীরা কৃষ্ণ-বিরহে বিলাপ করছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা অনুস্মরণ করছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁদের কাছে ফিরে আসলেন তখন গোপীকা’রা শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই প্রশ্ন করেছিলেন যে, তাঁদের আকুল আবেদন সত্ত্বেও ভগবান কেন সাড়া দেন নি। তখন ভগবান স্বয়ং এর উত্তর প্রদান করেছেন নিম্নোক্ত শ্লোকে। নাহং তু সখ্যো ভজতোহপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে। যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ ৷৷ শ্রীমদ্ভাগবতঃ ১০/৩২/২০ অন্বয়ঃ -করি না; অহম্-আমি; তু-অপরপক্ষে; সখ্যঃ-হে সখীগণ; ভজতঃ-পূজা করে; অপি-এমন কি; জন-জীবের সঙ্গে; ভজামি- ভাব বিনিময়; আমীষাম্- তাদের; অনুবৃত্তি- প্রবৃত্তি (শুদ্ধ প্রেমের জন্য); বৃত্তয়ে- চালিত করার জন্য; যথা-ঠিক যেমন; অধনঃ- এক ধনহীন মানুষ; লব্ধ- প্রাপ্ত হয়ে; ধনে- ধন; বিনষ্টে- এবং তা বিনষ্ট হলে; তৎ- তার; চিন্তয়া- উদ্বিগ্ন চিন্তাতেই; অন্যৎ- অন্য কোন কিছু; নিভৃতঃ- ব্যাপৃত; ন বেদ-জানে না। অনুবাদঃ জীব যখন আমাকে ভালবাসে, এমন কি তারা যখন আমার পূজাও করে, আমি তৎক্ষণাৎ সাড়া দিই না, তার কারণ হে গোপীগণ, আমি তাদের প্রেমময় ভক্তিকে তীব্রতর করতে চাই। লব্ধ ধন নষ্ট হওয়া নির্ধন ব্যক্তি যেমন সেই ধনের চিন্তাতেই উদ্বিগ্ন থাকে, অন্য কোন কিছুরই চিন্তা করতে পারে না, তখন তারা তেমনি হয়ে ওঠে। তাৎপর্য ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন ‘যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম’- “যারা যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্থন করে, আমি তাদের সেভাবেই পুরস্কৃত করি।” তবুও কেউ যদি ভক্তি সহকারে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, ভক্তের প্রেম তীব্রতর করার জন্য ভগবান তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ সাড়া না দিতেও পারেন। কার্যত, ভগবান কিন্তু যথাযথভাবেই সাড়া দিচ্ছেন। কারণ একজন ঐকান্তিক ভক্ত সকল সময়েই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, “দয়া করে তোমাকে শুদ্ধভাবে ভালবাসার জন্য আমাকে সাহায্য কর।” সুতরাং ভগবানের তথাকথিত অবহেলা আসলে ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করা। দৃশ্যত নিজেকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতি আমাদের ভালবাসা আরও তীব্র করে তোলেন আর তার ফলস্বরূপ বস্তুত আমরা যা চাই সেটি আমরা লাভ করি- পরমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের জন্য প্রগাঢ় প্রেম। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের দৃশ্যত অবহেলা, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সুচিন্তিত সাড়া দেওয়া আর আমাদের গভীর ও শুদ্ধ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা লাভ। আচার্যবর্গের মতানুসারে, শ্রীকৃষ্ণ যখন এই শ্লোকটি বলতে শুরু করলেন, তখন গোপীরা তাঁদের মুখের হাসি চেপে একে অপরের দিকে আড়চোখে দেখছিলেন। এরপরও শ্রীকৃষ্ণ যখন বলে চললেন, গোপীগণ হৃদয়ঙ্গম করতে শুরু করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রেমময়ী সেবার পরম পূর্ণতার স্তরে আনয়ন করছেন।
রাসলীলা’র অন্তর্নিহিত তাৎপর্য কি? – ১ম পর্ব

আত্মারাম পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা নিয়ে বদ্ধজীবের মনে সংশয়ের অন্ত নেই। তার মধ্যে একটি সংশয় বড়ই আশ্চর্যের যে, ব্রজগোপিকাদের নিয়ে শারদ রাতে নৃত্যরত রসিকেন্দ্রচূড়ামণি, রাসেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ যাদের আরাধ্য ভগবান, রাসলীলা যাদের পাঠ্যবিষয়, তারা কীভাবে বৈরাগ্য শিক্ষা লাভ করে? বস্তুত দেখা যায় যে, এই রাসলীলা যাদের পরম আদরণীয় বিষয়, তারা তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে বৈরাগ্যবিদ্যা চর্চা করেন এবং ব্রহ্মচর্যব্রত, সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। তাই, রাসলীলা শ্রবণ-কীর্তন করে কিভাবে বৈষ্ণবগণ তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনে ‘অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ বর্জন’ আদি কঠোর ব্রত গ্রহণ করেন, সেই রহস্য উন্মোচন করা হবে এই ১ম পর্বে। এই পর্বে উওর প্রদান করেছেন শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিষ্যবৃন্দ শ্রীমদ্ভাগবত ১০/৩০/৩৪ এর ভাষ্যে: রেমে তয়া স্বাত্মরত আত্মারামোহপ্যখণ্ডিতঃ । কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাম্ ॥ অন্বয়ঃ রেমে – তিনি বিহার করেছিলেন; তয়া – তাঁর সঙ্গে; চ – এবং; আত্ম-রতঃ – স্ব-ক্রীড়; আত্ম-আরামঃ – আত্মসন্তুষ্ট; অপি – যদিও; অখণ্ডিতঃ – স্বয়ংসম্পূর্ণ; কামিনাম্ – সাধারণ কামুক মানুষের; দর্শয়ন্ – প্রদর্শনের জন্য; দৈন্যম্ – দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা; স্ত্রীণাম্ – সাধারণ নারীদের; চ এব – ও; দুরাত্মতাম্ – দুরাত্মতা। অনুবাদ: [শুকদেব গোস্বামী বলতে থাকেন] ভগবান কৃষ্ণ স্ব-ক্রীড়, আত্মারাম ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ কামুক মানুষের দুর্দশা ও নারীদের দুরাত্মতা প্রদর্শনের জন্য সেই গোপীর সঙ্গে বিহার করেছিলেন। তাৎপর্য: জড়জাগতিক মানুষেরা কখনও শ্রীকৃষ্ণের লীলার যে বিরুদ্ধ সমালোচনা করে থাকে, এই শ্লোকে সরাসরি তা খণ্ডন করা হয়েছে। দার্শনিক অ্যারিস্টটল সাধারণ কার্যকলাপ সবই ভগবানের অযোগ্য বলে দাবী করেছিলেন এবং কিছু মানুষ এই ধারণা পোষণ করার ফলে ঘোষণা করে যে, ভগবান কৃষ্ণের কার্যকলাপ যেহেতু সাধারণ মানুষের মতো, তাই তিনি স্বয়ং কখনও পরমব্রহ্ম হতে পারেন না। কিন্তু এই শ্লোকে শুকদেব গোস্বামী দৃঢ়ভাবে বলছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পারমার্থিক আত্ম-সন্তুষ্টির মুক্ত স্তরে ক্রিয়া করেন। এই সত্যটি আত্ম-রত, আত্মারাম, এবং অখণ্ডিত শব্দ গুলির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। বন-জ্যোৎস্নায় আবেগপ্রবণ প্রণয় উপভোগকারী এক সুন্দর বালক এবং এক সুন্দরী বালিকা স্বার্থপর কামনা-বাসনারহিত শুদ্ধ কর্মে যুক্ত হতে পারে, সাধারণ মানুষের কাছে তা অচিন্তনীয়। যদিও ভগবান কৃষ্ণ সাধারণ মানুষদের কাছে অচিন্তনীয়, কিন্তু যারা তাঁকে ভালোবাসে, তারা সহজেই তাঁর লীলার পরম শুদ্ধতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কেউ হয়ত বলতে পারে যে, “সৌন্দর্য তো দর্শকের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার!”, আর তাই কৃষ্ণভক্তগণ ভগবানের কার্যকলাপকে শুদ্ধ বলে কল্পনা করছেন। এই যুক্তি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ সত্যকে অবজ্ঞা করছে। যেমন প্রথম হল, কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত হবার জন্য কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে একজন ভক্তকে কঠোরভাবে চারটি বিধি নিষেধ পালন করতে হয় – অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ করা চলবে না, কোন রকম জুয়াখেলা চলবে না, কোন নেশা করা চলবে না এবং মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি আমিষাহার করা চলবে না। কেউ যখন জাগতিক কামনা থেকে মুক্ত হয়ে জাগতিক আকাঙ্ক্ষার অতীত এক মুক্ত স্তরে উন্নীত হন, তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের পরম সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করেন। এটি কোন তাত্ত্বিক পন্থা নয়, কৃষ্ণভাবনামৃতের পথ সম্বন্ধে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা রেখে গেছেন যে শত-সহস্র মহান ঋষিগণ, তাঁরা এটি সম্পূর্ণ অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ত করেছিলেন। একথা ঠিকই যে, দ্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির উপর সৌন্দর্য নির্ভর করে। কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য জাগতিক দেহের কামুক চোখে নয়, আত্মার চোখে অনুভূত হয়। তাই, বৈদিক শাস্ত্রে বারে বারে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, জাগতিক আকাঙ্ক্ষা হতে মুক্তজনেরাই কেবল তাঁদের ভগবৎ-প্রেমের অঞ্জনে চর্চিত শুদ্ধ-আত্মার চোখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শন করতে পারেন। অবশেষে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই মানুষ জাগতিক ইন্দ্রিয়ের বিষয়গত সকল ইন্দ্রিয় বাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। পরিশেষে, চূড়ান্তভাবে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়লীলা তাঁর পরমতত্ত্বের যোগ্যতা অনুযায়ী যথাযথ। বেদান্তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পরম ব্রহ্ম সমস্ত কিছুর মূল উৎস। তাই, জড় জগতের কোন সুন্দর বস্তু পরমতত্ত্বে নেই, তা হতে পারে না। যেহেতু জড় জগৎ চিৎজগতের বিকৃত প্রতিফলন, তাই পরমতত্ত্বে শুদ্ধ, অপ্রাকৃতরূপে অধিষ্ঠিত প্রণয় বিষয়ও এই জগতে তার বিকৃত, জাগতিক রূপে প্রকাশিত হতে পারে। তাই, এই জগতের প্রতিভাত সৌন্দর্যকে চরমে পরিত্যাগ না করে, বরং তাকে তার শুদ্ধ অপ্রাকৃত রূপে গ্রহণ করা উচিত। অনাদি কাল হতে স্ত্রী ও পুরুষেরা প্রণয়কলা দ্বারা কাব্যিক আনন্দে উৎসাহিত হয়েছেন। দুর্ভাগ্যবশত, এই জগতে প্রণয় আমাদের হতাশা-ধ্বস্ত করে আমাদের হৃদয়ের পরিবর্তন কিম্বা মৃত্যু ঘটায়। এইভাবে প্রণয় বিষয়টিকে প্রথমত সুন্দর ও উপভোগ্যরূপে দেখা গেলেও, পরিশেষে তা জাগতিক প্রকৃতির প্রচণ্ড আক্রমণের ফলস্বরূপ নষ্ট হয়। তবুও প্রণয়ের ধারণাকে সামগ্রিকভাবে পরিত্যাগ করা অযৌক্তিক। বরং, স্বার্থপরতা বা জাগতিক কামে রঞ্জিত না করে প্রণয় আকর্ষণ যে ভাবে ঈশ্বরের মাঝে বিদ্যমান, সেই পরম, পূর্ণ, শুদ্ধ স্বরূপে আমাদের তা গ্রহণ করা উচিত। সেই পরম প্রণয় আকর্ষণ, পরম সত্যের পরম সৌন্দর্য ও আনন্দকে আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের পাতায় পাতায় পাঠ করছি। ।। হরে কৃষ্ণ ।। [ বি:দ্র: স্বধর্মম্ – এর অনুমোদন ব্যতীত এই গবেষণামূলক লেখার কোনো অংশ পুনরুৎপাদন, ব্যবহার, কপি পেস্ট নিষিদ্ধ। স্বধর্মম্ – এর সৌজন্যে শেয়ার করার জন্য উন্মুক্ত ]
সোমরস কি? সোমরস আর মদিরা বা সুরা কি এক?

সোমরস কি? সোমরস আর মদিরা বা সুরা কি এক? এ সম্পর্কে রসেন্দ্রচূড়ামণিতে বলা হয়েছে- পঞ্চাঙ্গযুত্পঞ্চদশচ্ছদাঢ্যা সর্পাকৃতিঃ শোণিতপর্বদেশা। সা সোমবল্লী রসবন্ধকর্ম করোতি একাদিবসোপনীতা। করোতি সোমবৃক্ষোহপি রসবন্ধবধাদিকম্। পূর্ণিমাদিবসানীতস্তযোবল্লী গুণাধিকা।। কৃষ্ণে পক্ষে প্রগলতি দলং প্রত্যহং চৈকমেকং। শুক্লেহপ্যেকং প্রভবতি পুনর্লন্বমানা লতাঃ স্যুঃ। তস্যাঃ কন্দঃ কলয়তিতরাং পূর্ণিমায়াং গৃহীতো। বদ্ধা সূতং কনকসহিতং দেহলোহং বিধত্তে।।ইয়ং সোমকলা লক্ষবেধী বদ্ধসূতেন্দ্রো নাম বল্লী পরমদুর্লভা। অনয়া প্রজায়তে।। [ রসেন্দ্রচূড়ামণি ৬।৬-৯] বঙ্গানুবাদ: সর্পের আকৃতির ন্যায় যার পনেরোটি পাতা, পাতা বেরোবার স্থানটি যার লালবর্ণ, পূর্ণিমার দিন সংগ্রহ করা এরই পঞ্চাঙ্গ (মূল, শাখা, পাতা, ফুল ও ফল) দ্বারা যুক্ত সোমবল্লী পারদকে বদ্ধ করে। পূর্ণিমার দিনে সংগ্রহ করা পঞ্চাঙ্গ (মূল, বল্কল, পাতা, ফুল ও ফল) যুক্ত সোমবৃক্ষও পারদকে সংযুক্ত করা, পারদকে ভস্মে পরিণত করা ইত্যাদি কাজ করে দেয়। কিন্তু সোমবল্লী এবং সোমবৃক্ষ-এই দুটির মধ্যে সোমবল্লী অধিক গুণসম্পন্ন। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিদিন এই সোমবল্লীর একটি করে পাতা খসে যায় এবং শুক্লপক্ষে প্রতিদিন একটি করে নতুন পাতা গজায়। এইভাবে এই লতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পূর্ণিমার দিন যদি এই লতার কন্দ বার হয়, তবে সেটি খুব ভালো হয়। ধুতরার সঙ্গে এই কন্দে আবদ্ধ পারদ শরীরকে লোহার মতো মজবুত করে এবং এর দ্বারা আবদ্ধ পারদ লক্ষবেধী হয় অর্থাৎ একগুণ বদ্ধ পারদ লক্ষগুণ লোহাকে সোনায় পরিণত করে। সোম নামক এই লতা অত্যন্ত দুর্লভ। সোমলতা নামক এই ওষধি গাছের রস থেকে তৈরি হয় সোমলতার রস বা সোমরস। সোমলতার কথা পাওয়া যায় আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র (৫।১২)-তে যেখানে বলা হচ্ছে, সোমযাগে সোমলতা ছেঁচা হত। সোমলতা ও মদিরা এক নয়।শতপথ ব্রাহ্মণ (৫।১।২)-এ সরাসরিই মদ্যপান করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাই সোমরস কোন মদিরা বা নেশাদ্রব্য নয়। ।। হরে কৃষ্ণ ।। [ বি:দ্র: স্বধর্মম্-এর অনুমোদন ব্যাতীত এই লেখার কোনো অংশ পুনরুৎপাদন, ব্যবহার, কপি পেস্ট নিষিদ্ধ। স্বধর্মম্-এর সৌজন্যে শেয়ার করার জন্য উন্মুক্ত ] নিবেদক- ° স্বধর্মম্: প্রশ্ন করুন | উত্তর পাবেন °
বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি পরমেশ্বর ভগবানের “নির্গুণ ও সগুণ” উভয় সত্তাকেই স্বীকার করেন?
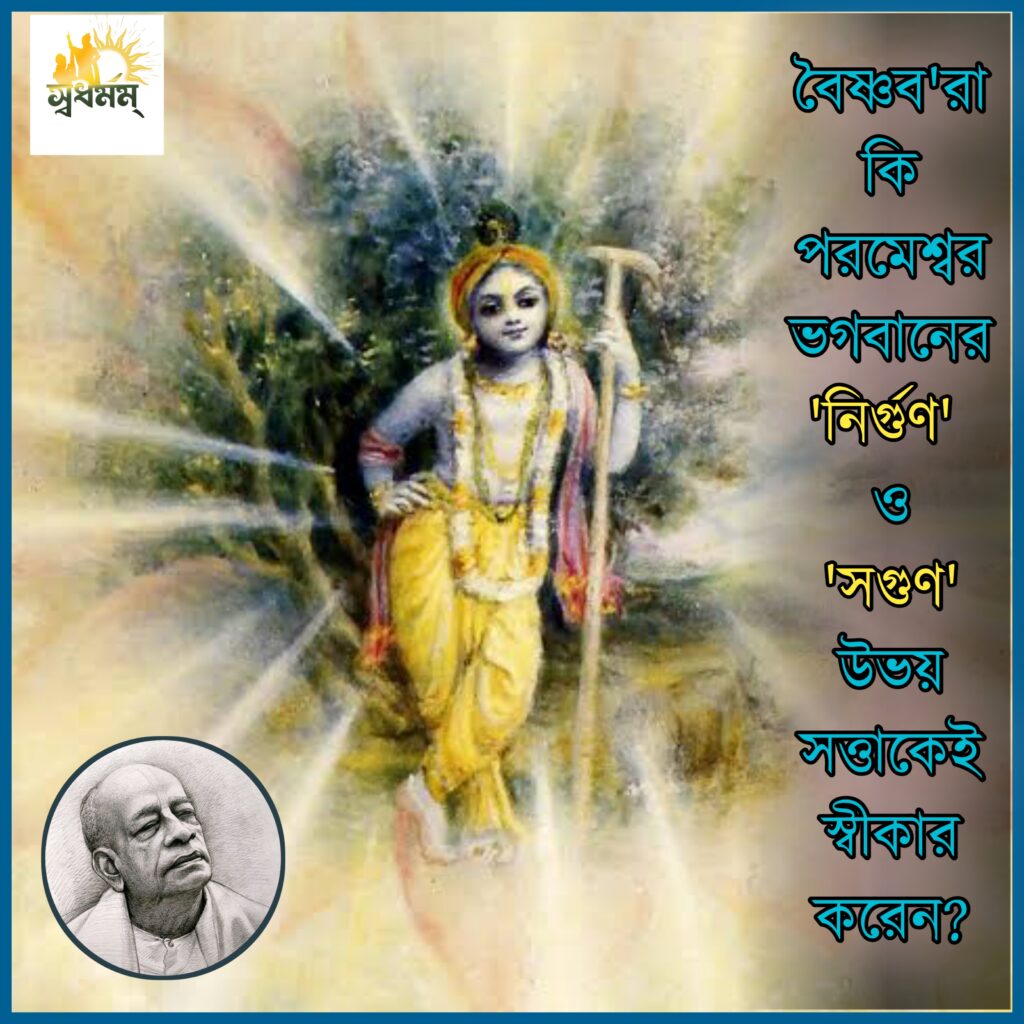
প্রশ্নঃ বৈষ্ণব সম্প্রদায় কি পরমেশ্বর ভগবানের নির্গুণ ও সগুণ উভয় সত্তাকেই স্বীকার করেন? উত্তরঃ হ্যাঁ। তারা এই উভয় দর্শনকেই স্বীকার করেন। প্রশ্নঃ তবে তা কিভাবে, ব্যাখ্যা করুন। উত্তরঃ এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর ‘শ্রীঈশোপনিষদের’ ৫ম মন্ত্রের ভক্তিবেদান্ত ভাষ্যে। আপনাদের সুবিধার্থে উক্ত ভাষ্য এখানে তুলে ধরা হলো। শ্রীঈশোপনিষদঃ মন্ত্র-৫ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্ দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥ তৎ-সেই পরমেশ্বর ভগবান; এজতি-সচল; তৎ-তিনি; ন-না; এজতি-সচল; তৎ-তিনি; দূরে-দূরে; তৎ-তিনি; উ-ও; অন্তিকে-অতি নিকটে; তৎ-তিনি; অন্তঃ-অন্তরে; অস্য-এর; সর্বস্য-সব কিছুর; তৎ-তিনি; উ-ও; সর্বস্য-সব কিছুর; অস্য– এর; বাহ্যতঃ-বাইরেও। অনুবাদঃপরমেশ্বর ভগবান সচল এবং অচল। তিনি বহু দূরে রয়েছেন, আবার সন্নিকটেও অবস্থান করছেন। তিনি সকল বস্তুর অন্তরে এবং বাইরে অবস্থান করেন। তাৎপর্যঃ এই শ্লোকে ভগবান অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা যে অপ্রাকৃত কার্যকলাপ প্রদর্শন করেন তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরস্পর-বিরোধী কথা উল্লেখ করে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রমাণ করা হয়েছে। তিনি সঞ্চরণশীল এবং সঞ্চরণশীল নন। এই প্রকার পরস্পর-বিরোধী বৈশিষ্ট্য ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে ইঙ্গিত করে। আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমরা এই ধরনের পরস্পর-বিরোধী উক্তির সমন্বয় সাধন করতে পারি না। আমাদের সীমিত জ্ঞান দ্বারা আমরা কেবল ভগবান সম্বন্ধে কিছু কল্পনা করতে পারি। মায়াবাদ সম্প্রদায়ের নির্বিশেষবাদী দার্শনিকেরা ভগবানের নির্বিশেষ কার্যকলাপ মাত্র গ্রহণ করেন এবং তাঁর সবিশেষ রূপকে বাতিল করে দেন। কিন্তু ভাগবত সম্প্রদায় ভগবানের সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয় রূপকেই স্বীকার করেন। ভাগবতগণ তাঁর অচিন্ত্য শক্তিসমুহকেও স্বীকার করেন, কেন না এই শক্তিসমূহ ব্যতিরেকে ‘পরমেশ্বর’ কথাটির কোন অর্থই হয় না। যেহেতু আমরা ভগবানকে স্বচক্ষে দর্শন করতে পারি না, আমাদের মনে করা উচিত নয় যে, তাই ভগবানের কোনও সবিশেষ সত্তা নেই। এই যুক্তি খণ্ডন করে শ্রীঈশোপনিষদ আমাদের সতর্ক করেছেন যে, ভগবান যেমন আমাদের থেকে অতি দূরে তেমনি তিনি অতি নিকটেও অবস্থান করেন। ভগবানের ধাম জড় আকাশ থেকে বহু দূরে এবং এমন কি এই জড় আকাশ পরিমাপ করার কোন উপায় আমাদের জানা নেই। জড় আকাশ যদি বহু বহু দূর বিস্তৃত হয়, তা হলে জড় আকাশের অতীত চিদাকাশকে জানার কোন প্রশ্নই ওঠে না। চিদাকাশ যে জড় ব্রহ্মাণ্ডের বহু দূরে অবস্থিত, তা ভগবদ্গীতায়ও (১৫/৬) প্রতিপন্ন হয়েছে। কিন্তু ভগবান এত দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও, মুহূর্তমধ্যে তিনি বায়ু অথবা মন অপেক্ষা দ্রুত গতিতে আমাদের কাছে আবির্ভূত হতে পারেন। তিনি এত দ্রুত চলতে পারেন যে, কেউ তাঁকে অতিক্রম করতে পারে না। এই বিষয়টি পূর্বোক্ত মন্ত্রে বর্ণনা করা হয়েছে। তবুও ভগবান যখন আমাদের কাছে আবির্ভূত হন তখন আমরা তাঁকে অবজ্ঞা করি। ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান এই বিচার- বুদ্ধিহীন অবস্থার নিন্দা করে বলেছেন যে, মূর্খরাই কেবল তাঁকে মরণশীল ব্যক্তি বলে অনুমান করে উপহাস করে। (গীতা ৯/১১) তিনি মরণশীল ব্যক্তি নন, তেমনই তিনি আমাদের সামনে জড়া প্রকৃতিজাত দেহ নিয়ে আবির্ভূত হন না। তথাকথিত অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা মনে করেন, ভগবান যখন জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জড়দেহ ধারণ করেন। তাঁর অচিন্ত্য শক্তির কথা না জেনেই, মূর্খরা ভগবানকে সাধারণ মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত বলে বিবেচনা করে। অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন বলে ভগবান যে কোন উপায়েই আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারেন, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তিকে স্বেচ্ছায় রূপান্তরিত করতে পারেন। অবিশ্বাসীরা তর্ক করে যে, ভগবান-স্বয়ং কোন মতেই মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারেন না এবং যদি তিনি সক্ষম হন, তবে তিনি জড়া প্রকৃতিজাত রূপ নিয়ে অবতরণ করেন। ভগবানের অচিন্ত্য শক্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করলেই এই যুক্তির অসারতা প্রতিপন্ন হয়। এমন কি ভগবান যদি জড়া প্রকৃতির আকার নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থিতও হন, তবুও তাঁর পক্ষে সেই জড় শক্তিকে চিন্ময় শক্তিতে রূপান্তরিত করা খুব সহজ। যেহেতু জড়া ও পরা শক্তি উভয়েরই উৎস এক, তাই উৎসের ইচ্ছা অনুসারেই শক্তিগুলির যথাযথ ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, ভগবান মাটি, পাথর কিংবা কাঠের অর্চা-বিগ্রহের মধ্যে আবির্ভূত হতে পারেন। এই সমস্ত শ্রীবিগ্রহ কাঠ, পাথর বা অন্য কোন পদার্থ থেকে প্রকাশিত হলেও তা দেবমূর্তি নয়, যা অপৌত্তলিকরা দাবি করেন। আমাদের বর্তমান অসম্পূর্ণ প্রাকৃত অবস্থায় ত্রুটিযুক্ত দর্শন-শক্তির কারণে আমরা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারি না। কিন্তু ভগবৎ-দর্শনে ইচ্ছুক জড় দৃষ্টিসম্পন্ন ভক্তবৃন্দের কাছে তিনি কৃপা করে তথাকথিত জড় বিগ্রহ-রূপে তাঁদের সেবা গ্রহণের জন্য আবির্ভূত হন। কারও মনে করা উচিত নয় যে, যারা পৌত্তলিক তাঁরা ভগবদ্ভক্তির নিম্নতম পর্যায়ে বিরাজ করছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ভগবৎ উপাসনাই করছেন এবং তিনি তাঁদের কাছে সহজগম্যভাবে আবির্ভূত হতে সম্মত হয়েছেন। অর্চা-বিগ্রহ উপাসকের মনগড়া নয়, তা তাঁর সকল আনুষঙ্গিক সহ নিত্য বর্তমান। একমাত্র শুদ্ধ অন্তঃকরণ- বিশিষ্ট ভক্তই এই সত্য অনুধাবন করতে পারেন, নাস্তিকের দ্বারা তা সম্ভব নয়। ভগবদ্গীতায় (৪/১১) শ্রীভগবান বলেছেন যে, ভক্তের শরণাগতির মাত্রা অনুসারেই তিনি তাঁর ভক্তের সঙ্গে সম্পর্কিত হন। তাঁর শরণাগত ভক্ত ভিন্ন অন্য কারও কাছে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন না। সুতরাং শরণাগত ভক্তের কাছে তিনি অত্যন্ত সুলভ, কিন্তু যারা শরণাগত নয়, তাদের কাছ থেকে তিনি বহু বহু দূরে অবস্থান করেন এবং তাদের কাছে তিনি একান্তই দুর্লভ। এই প্রসঙ্গে শাস্ত্রে বর্ণিত সগুণ এবং নির্গুণ শব্দ দুটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সগুণ শব্দের অর্থ এই নয় যে, ভগবান যখন এই জগতে আবির্ভূত হন, তখন তিনি জড়া প্রকৃতির নিয়মের অধীন হন, যদিও তিনি উপলভ্য এবং প্রাকৃত রূপেই আবির্ভূত হন। সকল শক্তির উৎস হওয়ায়, তাঁর কাছে জড়া শক্তি ও চিন্ময় শক্তির মধ্যে কোন ভেদ নেই। সকল শক্তির নিয়ন্তা বলে, আমাদের মতো তিনি কখনও সেই শক্তিগুলির দ্বারা প্রভাবিত হন না। জড় শক্তি তাঁর নির্দেশেই কাজ করে; তাই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জড় শক্তিকে চালনা করতে পারেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং কখনও এই জড় শক্তির গুণদ্বারা প্রভাবিত হন না। আবার পরিশেষে তিনি কখনও নিরাকার হয়ে যান না। প্রকৃতপক্ষে তিনি নিত্য শ্রীবিগ্রহ-সম্পন্ন আদিপুরুষ। তাঁর নির্বিশেষ রূপ বা ব্রহ্মজ্যোতি হচ্ছে তাঁর দেহনিঃসৃত জ্যোতি, ঠিক যেমন-সূর্যরশ্মি হচ্ছে সূর্যদেবতার দেহনিঃসৃত জ্যোতি। প্রহ্লাদ মহারাজ শৈশবে যখন তাঁর ঘোর নাস্তিক পিতা হিরণ্যকশিপুর সম্মুখে ছিলেন, তখন তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, “তোমার ভগবান কোথায়?” প্রহ্লাদ মহারাজ যখন উত্তর দিলেন, ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তখন তাঁর পিতা ক্রুদ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর ঈশ্বর এই রাজপ্রাসাদের কোন একটি স্তম্ভের মধ্যে আছে কি না। এবং শিশু প্রহ্লাদ বললেন, “হ্যাঁ আছেন।” তৎক্ষণাৎ সেই নাস্তিক অসুর তাঁর সম্মুখে স্তম্ভটি ভেঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ করলে তার ভিতর থেকে তৎক্ষণাৎ অর্ধ নর, অর্ধ সিংহ অবতার নৃসিংহ মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে হিরণ্যকশিপুকে বধ করেন। এভাবেই ভগবান সমস্ত কিছুর মধ্যে রয়েছেন এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেন। তাঁর ঐকান্তিক ভক্তকে কৃপা প্রদর্শন করার জন্য তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তিনি যে কোন স্থানে আবির্ভূত হতে পারেন। ভগবান নৃসিংহ ফটিক স্তম্ভের মধ্যে থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর ভক্ত প্রহ্লাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করবার জন্যে, নাস্তিক হিরণ্যকশিপুর আদেশে নয়। একজন নাস্তিক ভগবানকে আবির্ভূত হওয়ার জন্য আদেশ করতে পারে না, কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তকে কৃপা প্রদর্শনের জন্য সব সময়, সর্বত্র আবির্ভূত হন। তেমনই, ভগবদ্গীতায় (৪/৮) বলা হয়েছে যে, বিশ্বাসীদের রক্ষা এবং অবিশ্বাসীদের বিনাশ করবার জন্য ভগবান আবির্ভূত হন। অবশ্যই নাস্তিকদের
বিবাহে কোষ্ঠিবিচার কতটুকু যৌক্তিক?

⭕বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ ⭕বিবাহে কোষ্ঠিবিচার কতটুকু যৌক্তিক❓ বৈদিক প্রথায় পিতা-মাতা বিবাহের পূর্বে পাত্র এবং পাত্রীর কোষ্ঠি বিচার করেন। জ্যোতির্গণনায় পাত্র এবং পাত্রী যদি সর্বোতভাবে সুসঙ্গত হয়, তা হলে সেই সংযোগকে বলা হয় যোটক এবং তখন তাদের বিবাহ হয়। এমন কি পঞ্চাশ/একশো বছর আগেও হিন্দুসমাজে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। পাত্র যতই ধনী হোক না কেন অথবা কন্যা যতই সুন্দরী হোক না কেন, জ্যোতির্গণনায় মিল না হলে বিবাহ হত না। তিনটি শ্রেণীতে মানুষের জন্ম হয় — দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং রাক্ষসগণ। ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন ভাগে দেবতা এবং রাক্ষসেরা রয়েছে। মানব সমাজেও কোন কোন মানুষ দেবতাদের মতো এবং কোন কোন মানুষ আবার রাক্ষসের মতো। জ্যোতির্গণনাতেও তেমন দেবগণের সঙ্গে রাক্ষসগণের মিল না হওয়ায় তাদের মধ্যে বিবাহ হয় না। তেমনই প্রতিলোম(উচ্চ গুণসম্পন্ন/বর্ণের কন্যার সহিত নিম্ন গুণসম্পন্ন/বর্ণের পাত্রের বিবাহ) এবং অনুলোমের(উচ্চ গুণসম্পন্ন/বর্ণের পাত্রের সহিত নিম্ন গুণসম্পন্ন/বর্ণের কন্যার বিবাহ) বিচার রয়েছে। মূল কথা হচ্ছে, পাত্র এবং পাত্রী যদি সমান স্তরের হয় তা হলে বিবাহ সুখের হয়, কিন্তু বৈষম্য হলে তা চরমে দুঃখদায়ক হয়। যেহেতু আজকাল আর সেইভাবে বিচার বিবেচনা করা হয় না, তাই এত বিবাহ-বিচ্ছেদ হচ্ছে। বস্তুতপক্ষে, আজকাল বিবাহ-বিচ্ছেদ একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও পূর্বে পতি-পত্নীর সম্পর্ক ছিল সারা জীবনের সম্পর্ক, এবং এই সম্পর্ক এতই প্রীতির ছিল যে, পতির মৃত্যু হলে পত্নী স্বেচ্ছায় সহমৃতা হতেন অথবা আজীবন পতির অনুগত থেকে বৈধব্যদশা বরণ করতেন। আজকাল আর তা সম্ভব হচ্ছে না, কারণ মানব-সমাজ পশু-সমাজের স্তরে অধঃপতিত হয়েছে। এখন কেবল পরস্পরের প্রতি অভিরুচির ফলে বিবাহ হচ্ছে। দাম্পত্যেহভিরুচির্হেতুঃ (শ্রীমদ্ভাগবত ১২/২/৩)। অভিরুচির অর্থ হচ্ছে ‘সম্মতি’। পুরুষ এবং স্ত্রী যদি কেবল বিবাহ করতে সম্মত হয়, তা হলেই বিবাহ হতে পারে। কিন্তু বৈদিক প্রথা যদি নিষ্ঠা সহকারে পালন না করা হয়, তা হলে প্রায়ই সেই বিবাহের সমাপ্তি হয় বিবাহ-বিচ্ছেদে। ©️শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, ভা: ৯/১৮/২৩
বেদে কি পরমেশ্বর দারুব্রহ্ম জগন্নাথদেবের কথা বর্ণিত আছে?!

ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন শাখা ০৭.৫৬.০৪-০৫, সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদ৩.১৭.৬-৭, কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় নারায়ন উপনিষদ ৪, অথর্ববেদীয় গোপালতাপনী উপনিষদ ১/২১,১/২৪, কৃষ্ণ উপনিষদ এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কলির্সন্তরন উপনিষদ ২ ইত্যাদি বেদ বা শ্রুতি শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবান গোলকপতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণিত আছে। অথর্ববেদীয় গোপালতাপনী উপনিষদে বলা হয়েছে, “একো বশী সর্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্যঃ” অর্থাৎ, সেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পরম পুরুষোত্তম ভগবান,তিনিই আরাধ্য। – গোপালতাপনী উপনিষদ ১/২১(অথর্ববেদ) বেদসহ সমগ্র সনাতনী শাস্ত্রের শিক্ষা অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরমেশ্বর ভগবান। সমগ্র বেদ শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা আলোচিত হয়েছে।এ বিষয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় (১৫/১৫) বলেন, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो “বেদৈশ্চ সবৈররহমেব বেদ্যো” অর্থাৎ, আমি সমগ্র বেদে জ্ঞাতব্য। শ্রীকৃষ্ণকে বেদে বিষ্ণু, কৃষ্ণ,গোপাল ( চিন্ময় জগতের গোলক বৃন্দাবনে তিনি গোচারন করেন, তাই শ্রীকৃষ্ণের এক নাম গোপাল), দেবকীপুত্র ইত্যাদি নামে সম্বোধন করা হয়েছে। ঋগ্বেদীয় পুরুষসুক্ত,বিষ্ণু সুক্ত, এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় নারায়ন সুক্তে সমগ্র জগৎব্যাপী বিষ্ণুর বিরাটরূপ বা বিশ্বরূপের বর্ণনা করা হয়েছে,যে বিশ্বরূপটি গীতার বর্ণনা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে দর্শন দান করেন (গীতা ১১/৫-৪৪)। এবং একই গীতা শাস্ত্রে অর্জুনের ইচ্ছা অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে চতুর্ভূজ বিষ্ণুরুপ প্রদর্শন করেন (গীতা ১১/৪৬,৫০)।তাই মহাভারতে বহুবার শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীবিষ্ণু নামে সম্বোধন করা হয়েছে, (“অনুগ্রহার্থং লোকানাং বিষ্ণুলোক নমস্কৃতঃ।বসুদেবাত্তু দেবক্যাং প্রাদুর্ভূতো মহাযশাঃ।।” – “ত্রিজগতের পূজনীয় মহাযশস্বী স্বয়ং বিষ্ণু লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য বসুদেব-দেবকীতে আবির্ভূত হইয়া ছিলেন৷” – মহাভারত আদিপর্ব, ৫৮/১৩৮)। সে শ্রীকৃষ্ণ বা বিষ্ণু হলেন স্বয়ং দারুব্রহ্ম জগন্নাথ।দারুব্রহ্ম জগন্নাথ রুপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ উৎকল বা উড়িষ্যায় সমুদ্রের তীরবর্তী শ্রীক্ষেত্র পুরুষোত্তম ধাম জগন্নাথ পুরীতে নিত্য বিরাজমান।স্কন্দ পুরাণ শাস্ত্রের বিষ্ণু খন্ড,পুরুষোত্তমক্ষেত্র মাহাত্ম্য,১-২১ তম অধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী, বিষ্ণুভক্ত ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় স্বয়ং বিষ্ণু দারুরুপে উড়িষ্যার দক্ষিণ সাগরের তটে অবস্থান করেন। পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন সেবকগন কতৃর্ক সেই দারুকে মহাবেদীতে স্থাপন করেন।ইন্দ্রদ্যুম্নের প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তিনি দারু থেকে জগন্নাথ( শ্রীকৃষ্ণ), বলদেব (বলরাম), সুভদ্রা এবং সুদর্শনরুপে প্রকাশিত হয়েছিলেন। বেদ শাস্ত্রে সমুদ্রের তীরবর্তী দারুব্রহ্ম জগন্নাথের কথা বর্ণিত আছে। यद्दारु॒ प्लव॑ते॒ सिन्धो॑: पा॒रे अ॑पूरु॒षम्। तदा र॑भस्व दुर्हणो॒ तेन॑ गच्छ परस्त॒रम्॥ “যদ্ দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপূরুষম্। তদা রভস্ব দুর্হণো তেন গচ্ছ পরস্তরম্।। অনুবাদঃ ঐ দূরদেশে, সমুদ্রের পারে কোন প্রযত্ন ছাড়াই প্রকাশিত অপৌরুষেয় দারু ভাসছে– হে চিরঞ্জীবী স্তুতিকর্তা– তাঁর উপাসনা কর। সেই দারুময় বিগ্রহের উপাসনায় তুমি শ্রেষ্ঠতর দিব্যলোক প্রাপ্ত করবে। – ঋগ্বেদ সংহিতাঃ ১০/১৫৫/৩ ।।জয় জগন্নাথ।। ।।হরে কৃষ্ণ।। ।।প্রনাম।। – সদগুন মাধব দাস


 Views Today : 213
Views Today : 213 Total views : 118880
Total views : 118880 Who's Online : 0
Who's Online : 0 Your IP Address : 216.73.216.136
Your IP Address : 216.73.216.136